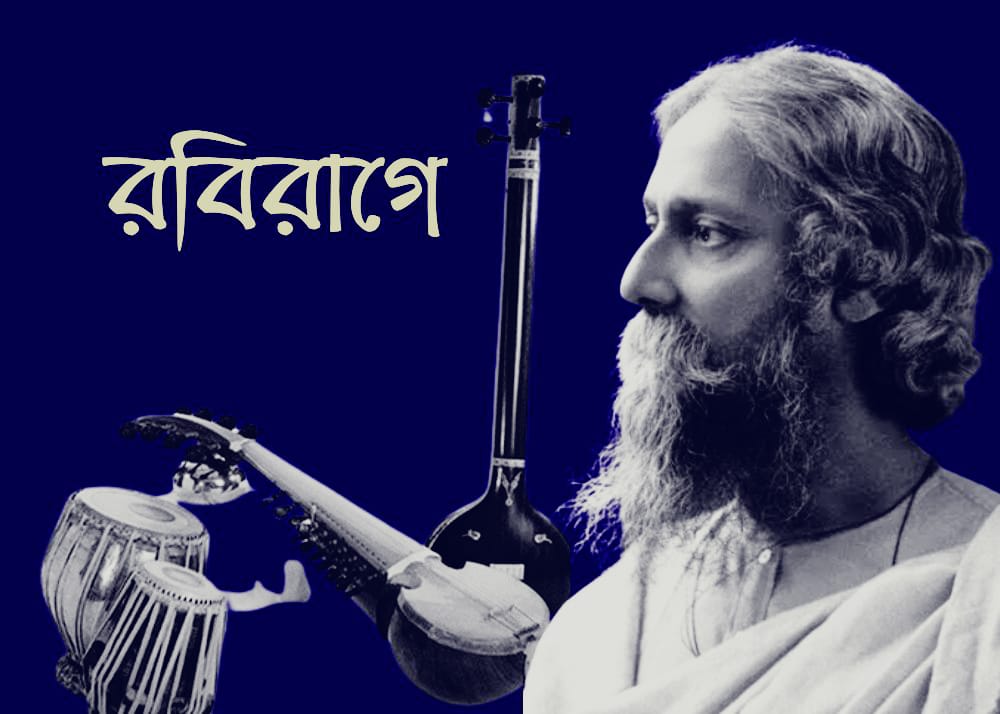গত পর্বে ছায়ানট (Chayanat) রাগের উল্লেখ করেছি; এই পর্বের বিষয়ও ছায়ানট রাগে রবীন্দ্র-গান (Rabindrasangeet)। ছায়ানটের প্রসঙ্গে আমার বন্ধু দেয়াসিনীর উল্লেখ গুরুত্বপূর্ণ। ছায়ানট রাগের প্রায় সব গানের সঙ্গেই আমার ওঁর মাধ্যমেই পরিচয়। দিদিমার কাছেও শিখেছি বেশ কিছু গান, কিন্তু, আলোচনা মূলত হয়েছে দেয়াসিনীর সঙ্গেই।
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছায়ানট রাগের সম্পর্ক নিয়ে খুব কিছু জানা যায় না। আমি যতটুকু পড়াশোনা করেছি, জেনেছি, কোনও এক আসরে শ্রীকৃষ্ণ রতনজংকারের ছায়ানট তিনি শুনেছিলেন; ভালো লাগেনি, সে কথা ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে জানিয়েওছিলেন। এই বিষয়ক তাঁদের পত্রবিনিময় আপনারা পড়বেন ‘সুর ও সংগতি’ গ্রন্থে।
ছায়ানট আদতে কী, ছায়ানট কীরকম, ছায়া এবং নট কী কী, এমন কিছু প্রশ্ন থাকতে বাধ্য। রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু ছায়ানটের গান শুনলে ছায়ানটের প্রচলিত রূপের সঙ্গে সবসময়ে তার মিল পাওয়া যায় না ঠিকই, তাই উল্লেখিত রাগগুলি একে একে জানব আমরা, এবং রবীন্দ্রনাথের কিছু গানের মাধ্যমে বুঝতে চেষ্টা করব, রবীন্দ্র-ভাবনায় ‘ছায়ানট’-কে।
একথা সর্বজনবিদিত— বিলাবল অঙ্গের দুই রাগ, ছায়া এবং নটের সংমিশ্রণেই আসে ছায়ানট। শুদ্ধ নট রাগে মধ্যম বাদী; ঋষভও প্রবল। পূর্বাঙ্গে যে স্বরবন্ধ আমরা প্রায়ই দেখি, তা হল—
সা রে, রে গা, গা মা
সা, রে গা মা, গা মা
রে গা মা ধাপা মা
পা মা গা, মা রে, সা রে
কখনও কখনও ‘র্সা, পা মা, রেগারে মা’ও পাব। এরই সঙ্গে যুক্ত হবে ঋষভ-কেন্দ্রিক কিছু স্বরবন্ধ, যেমন,
রে গা মা গারে সা গারে
রে গা মা রেগারে সা রে
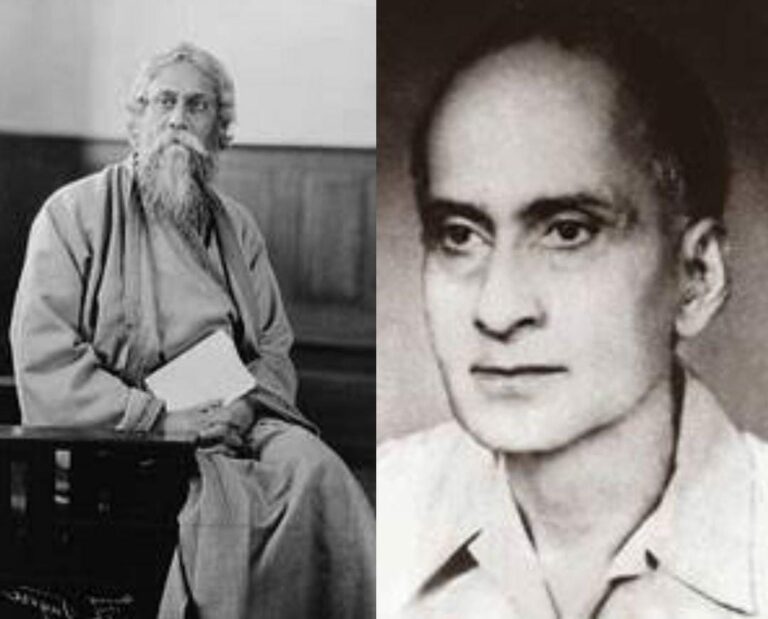
ছায়া রাগের সঙ্গে এই মধ্যম-কেন্দ্রিকতা এসে যুক্ত হয়ে হয়েছে ছায়ানট। ছায়া রাগে আমরা মধ্যমের প্রাবল্য পাব না; বরং, ঋষভের উপস্থিতিই এখানে বেশি। ছায়া রাগে প্রাপ্ত স্বরবন্ধগুলি যদি একবার দেখি, তবে পাব—
পা্ পা্ সা সা, নি সা রে সা
পা্ সা রে, রে সা
নি্ সা রে গা মা রে সা
সা রে, রে গা মাগা পা
পা > রে (পঞ্চম থেকে ঋষভ মীড়)
রে গা মা গা মা রে সা, রে
রে গা মা ধা ধা পা
পা ধা পা, র্সা র্সা
ধৈবতের ব্যবহার ছায়া এবং ছায়ানটের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে। ছায়া রাগে ধৈবত প্রবল, আন্দোলনমুক্ত। ছায়ানটে ধৈবত আন্দোলনযুক্ত; সে আন্দোলন একমুখী— কোমল নিষাদের দিকে। মাইহার ঘরানায় কোমল নিষাদের ব্যবহার নেই যদিও; আমরা এক্ষেত্রে গায়নে ছায়ানটের রূপকেই ধরে এগোব। ছায়া রাগে আমরা দেখলাম, মধ্যমে স্থায়িত্ব নেই; ছায়ানটে থাকবে, কারণ মধ্যমের স্থায়িত্ব নট-অঙ্গের অন্তর্গত।
ছায়ানটকে একটু চেনা যাক—
পা্ পা্ সা সা, নি্ সা রে সা (ছায়া রাগে পাই)
সা রে, রে গা, গা মা রে, সা (নট রাগে পাই)
রে গা মা নি ধা পা । নি > ধা, নি > ধা পা
পাহ্মা ধা পাহ্মা পাহ্মা পাহ্মা পা > রে
রে গা মা ধাপা মা (নট) গা মা রেসা গারে (ছায়া)
ছায়া রাগে উত্তরাঙ্গে দেখেছি, ‘পা ধা পা, র্সা র্সা’ স্বরবন্ধ ব্যবহৃত হয়; ছায়ানটে শুদ্ধ নিষাদের মাধ্যমে তার সপ্তকের ষড়জে যাওয়া হয় অধিকাংশ সময়।
দুটি বন্দিশের কথা উল্লেখ করব ছায়া এবং ছায়ানটের (Chayanat) প্রসঙ্গে; আগ্রার ফৈয়াজ খাঁ’র ছায়া রাগে ‘পবন চলত সন নন নন’ এবং আত্রাউলির ইনায়াত হুসেন খাঁ’র ছায়ানটে ‘ঝনন ঝনন ঝন নন নন’। দুটি বন্দিশই খরজের পঞ্চম থেকে শুরু, যা মনে করায়, দুটি বন্দিশই বুঝি ছায়া রাগে, তবে ইনায়াত হুসেনের বন্দিশটি ছায়ানটেই সকলে মনে করেন, মধ্যমের স্থায়িত্বের জন্যই হয়ত।
এবার উল্লেখ করা যায়, ‘শ্যামা’ নৃত্যনাট্যের একটি গান— ‘হৃদয়বসন্তবনে যে মাধুরি বিকাশিল’ (Rabindrasangeet)। গানটি নিঃসন্দেহে ছায়ানটে। গানটি যদি মনে রাখি, দেখব, প্রথম থেকেই যে স্বরবন্ধগুলি ব্যবহৃত হচ্ছে, তা ছায়ানটের দিকেই যায়। স্বরবন্ধগুলি—
রে ধা ধা নি ধা পা হ্মা পা
রে গা মা পা মা গা মা রে সা
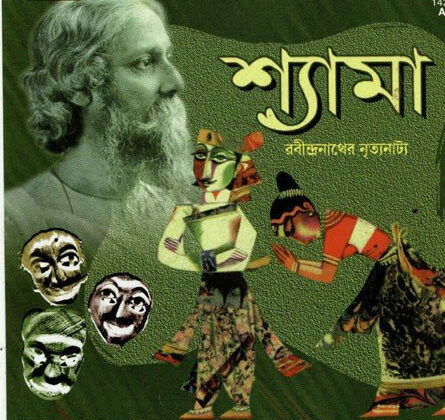
গত পর্বেও ছায়ানটের মধ্যে বিলাবল অঙ্গের এই স্বরবন্ধের কথা বলেছি— ‘রে গা মা পা গা মা রে সা’। যখন স্বরলিপিতে বা কারও গায়নে দেখি, ‘রে ধা ধা নি ধা পা হ্মা পা’, তখন ধৈবতে আন্দোলন চোখে পড়ে না ঠিকই, কিন্তু কোমল নিষাদের ছোঁয়া ধৈবতের প্রাচুর্যকে খানিক ধূসর করে দেয়। তখন আর এই গানকে শুধু ছায়া রাগে বলে ভাবতে ইচ্ছে করে না। প্রায় সবার উপস্থাপনাতেই দেখি, ছায়ানটের প্রচলিত রূপে পঞ্চম থেকে ঋষভে মীড় টেনে আসা; ছায়ানটের মূল বৈশিষ্ট্যের যে এটি একটি, তা আমিও দেখালাম একটু আগেই। আলোচ্য এই গানটিতেও দেখব, ‘যে’তে সেই একই মীড়— পঞ্চম থেকে ঋষভ; যা আবারও এই গানটি ছায়ানটে বলেই বিশ্বাস করায়। ‘সেই প্রেম এই মালিকায়’তে এবং প্রথম ‘রূপ নিল’তে দেখি মধ্যম-কেন্দ্রিকতা, যা নটে থাকলেও ছায়ানটের প্রচলিত রূপে ঠিক এভাবে থাকে কি না, বলা শক্ত। এর পর যখন স্থায়ী শেষ হয়, তখন আবার দেখব, ‘রূপ নিল’তে ‘ধা নি ধা পা’ স্বরবন্ধের প্রয়োগ। কোমল নিষাদের এই প্রয়োগ উপস্থিত এই কাঠামোতে ছায়ানটের নিশ্চিত বিস্তার প্রশস্ত করে। ‘সেই প্রেম এই মালিকায়’ প্রাপ্ত মধ্যম-কেন্দ্রিক স্বরবন্ধ ছায়ানটের অস্তিত্বের অন্তরায় কি না, তা নিয়ে আলোচনা করব একটু পরেই।
কিন্তু, এবার আসি দেয়াসিনীর কাছে প্রথম শোনা একটি গানে – ‘এই যে কালো মাটির বাসা’। গানের শুরুতে নট-অঙ্গে আমরা পাব,
রে মা রে মা পা
পা র্সা নি র্সা ধা পা
নট পরিস্ফুট হয়, ‘শ্যামল সুখের ধরা’য়, যেখানে ‘রে গা মা পা ধা পা মা’ পাই, এবং, ‘ধরা’ এসে মধ্যমে স্থির হয়। ছায়ানট স্পষ্টত বুঝতে পারি অন্তরার শেষে ‘দুঃখে আলো করা’য়, যেখানে আবার পাব—
ধা নি ধা পা
পা > রে
রে গা মা পা ধা পা মা
প্রশ্ন থেকে যায়, প্রথম পঙক্তিটি কি ছায়ানটে নয়?
‘আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই’ গানটিতেও প্রথম ছত্রে মনে হবে ছায়ানট সেভাবে পাব না। গান শুরু হয় পঞ্চমকে আধার করে, যদিও তারপর নট-অঙ্গে মধ্যমে ন্যাস রয়েছে। নটের বিলাবল অঙ্গের স্বরবন্ধ রয়েছে ‘বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে’তে— ‘রে গা মা ধা পা, মা গা মা রে সা’। ‘এ কৃপা কঠোরের’ শুরুতে আমরা যে স্বরবন্ধগুলি ব্যবহৃত হতে দেখি, তাও সরাসরিভাবে ছায়ানট নয় বলেই মনে হবে আমাদের—
- সা মা গা পা
- হ্মা পা ধা নি র্সা
ছায়ানট মূর্ত হয়ে উঠবে গানটির দ্বিতীয় ছত্রের শেষে, ‘জীবন ভরে’তে। দেখব, ‘র্সা নি ধা নি ধা পা, পা > রে, রে গা মা’; গানটিতে তখন ছায়ানটের উপস্থিতি নিয়ে আমাদের সন্দেহ থাকে না।
তবে, এখানে কি ছায়ানট আংশিক অনুপস্থিত?

না, উপরোক্ত দুটি গানই ছায়ানটেই। দুটি গান একটু খতিয়ে দেখলেই বুঝতে পারব সে কথা।
‘এই যে কালো মাটির বাসা’তে মধ্যমের মাধ্যমে উত্থান আমাদের বিপথে নিয়ে যাচ্ছে। এই স্বরবন্ধ মূলত কেদারের; কেদারও নট অঙ্গের রাগ। কেদারের সঙ্গে ছায়ানটের এই যোগ অসঙ্গত নয়; কীভাবে সম্পর্কিত, তা বলি। কিছুদিন আগে বন্ধু চিত্রায়ুধের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল ছায়ানটেরই একটি ভিন্ন প্রকার, কাওয়াল বাচ্চোঁ কা ছায়ানট নিয়ে। উল্লাস কাশলকারের ছাত্র, আদিত্য খান্ডওয়ে এই রাগ গেয়েছেন। রাগটিতে ছায়ানটের সঙ্গে এক এক জায়গায় কেদার এসে যুক্ত হয়; কিন্তু শুধুমাত্র উত্থানের সময়। সাধারণত ছায়ানটে যে যে স্বরবন্ধ আমরা দেখি, তাদের মধ্যে নট-কেন্দ্রিক স্বরবন্ধগুলি, ছায়া-অঙ্গে খরজের পঞ্চমভিত্তিক স্বরবন্ধগুলি, সবই এতে রয়েছে। কেদারের মূল সূত্রগুলি, অর্থাৎ
সা মা, সা রে সা
সা মাগা পা পা র্সা
যখন তার মধ্যে এসে পড়ে, তখন, হয়ত নট রাগের উপস্থিতির কারণেই মনে হয় না, আমরা বিযুক্ত কিছু শুনছি। এই রাগে তার-সপ্তকের ষড়জে পৌঁছনোর সময়ে ধৈবতের এবং নিষাদেরও ব্যবহার রবীন্দ্র-গানেও আমরা পাব।

‘আমি বহু বাসনায়’র ক্ষেত্রেও প্রশ্ন রয়েই যায়; পঞ্চমের আধারে স্বরবন্ধ কীভাবে নটের অন্তর্গত হয়? মনে রাখবেন, ‘সা রে পা পা ধা পা’ স্বরবন্ধটিও নট-অঙ্গেরই আরও একটি রাগ, কামোদের মূল সূত্র। শুধু ‘আমি বহু বাসনায়’ নয়, ‘স্বপনে দোঁহে ছিনু কী মোহে’ গানটিও শুরু হয়, এই একই স্বরবন্ধ দিয়ে। ‘স্বপনে দোঁহে ছিনু কী মোহে’র পথেই হয়ত রবীন্দ্র ভাবনায় ছায়ানটের একটি সামগ্রিক রূপের দিকে আমরা আরও একটু অগ্রসর হব। গানটি শুরু হয়, কামোদ রাগের ‘সা রে পা’ দিয়ে, কিন্তু ‘জাগার বেলা হল’তে আবারও বিলাবল অঙ্গে ‘গা মা ধা পা মা গা মা রে সা’। শুধু এতেই নয়, পরবর্তী পঙক্তিটি, অর্থাৎ, ‘যাবার আগে’তে যখন মধ্যমের আধারে কেদার অঙ্গে যে স্বরবন্ধ নিয়ে আসে, তাও নটের উপস্থিতির সাক্ষ্য দেয়। ‘বোলো বোলো’তে যখন প্রচলিত ছায়ানটের রূপ দেখি – ‘ধা নি ধা পা’, তখন বেশ বোঝা যায়, রবীন্দ্র-ভাবনায় ছায়ানটে সমানভাবে যুক্ত হয়েছে, ছায়া, নট, এবং অবশ্যই কেদার এবং কামোদ। অধিকাংশ সময়ই পূর্বাঙ্গে যখন রবীন্দ্রনাথ মধ্যমকে প্রকট রাখেন, হঠাৎই ‘অল্প লইয়া থাকি তাই’তে তার ব্যতিক্রম দেখে আমি দেয়াসিনীর সঙ্গে তর্ক জুড়েছিলাম, এই গানটি আসলে ছায়া রাগে; অনুরূপ নজরুলের গানটি ছায়ানটে। দেয়াসিনী আমাকে ‘অল্প’র কোমল নিষাদের যুক্তি দেখিয়ে শান্ত করেন।
সুতরাং, আমরা দেখি, রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাবনায় ছায়ানটে পূর্বাঙ্গে ছায়াকে প্রাধান্য দিচ্ছেন; মধ্য সপ্তকে নট-অঙ্গের মধ্যমের ন্যাস যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে নট-অঙ্গের আরও দুটি রাগ, কেদার এবং কামোদের ছায়া; উত্থানের সময় কেদারের আধারই বেশী; এবং ষড়জে ফিরে আসার সময় কোমল নিষাদের ব্যবহার সহ প্রচলিত ছায়ানটের স্বরবন্ধ। প্রচলিত ছায়ানটে তীব্র মধ্যম ব্যবহার নিয়ে বিভিন্ন ঘরানায় বিভিন্ন মতামত রয়েছে; রবীন্দ্রনাথ নির্দ্বিধায় তীব্র মধ্যম কণ-যুক্ত পঞ্চম ব্যবহার করেছেন।
দেয়াসিনীর মা, শ্রীমতী সঞ্চালি ঘোষকে একটি অনুষ্ঠানে প্রথম গাইতে শুনি, ‘যে ছায়ারে ধরব বলে’। ছায়ানটে রবীন্দ্রনাথের যত গান শুনেছি, বোধ হয় একমাত্র এই গানেই প্রচলিত ছায়ানটের রূপ স্পষ্ট; কেদার বা কামোদের ছোঁয়া এতে কম। বিশেষ করে
- রে নি ধা পা
- পা > রে
- রে গা মা ধাপা মা
এই স্বরবন্ধগুলি যখন দেখি, বাকি গানগুলির মতো তখন এখানে ছায়ানটকে খুঁজতে হয় না। গানের কথায় ‘ছায়ানট’ ব্যবহার করেছিলেন বলেই রাগরূপ রক্ষার্থে তাঁর দায়বদ্ধতা কাজ করেছিল, এমন ভাবা হয়ত ঠিক না। পঞ্চম থেকে ঋষভে মীড় স্পষ্টত আমরা ‘হৃদয়বসন্তবনে’ বা ‘যে ছায়ারে ধরব বলে’তেই পাই। অন্য গানগুলিতে কেউ যদি অনুরূপ মীড় টানতে চান, তাহলে স্বরলিপির দিক থেকে সঠিক না হলেও, সাঙ্গিতিক দিক থেকে তাতে কোনও দোষ নেই। গানের কথায় ‘ছায়ানট’ ব্যবহার করেছিলেন বলেই রাগরূপ রক্ষার্থে তাঁর দায়বদ্ধতা কাজ করেছিল, এমন ভাবা হয়ত ঠিক না।
ছায়ানটের মধ্যে এবং ছায়ানটের বাইরেও কেদারও রবীন্দ্র-গানের প্রসঙ্গে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরের পর্বে তাই নিয়ে আলোচনা করা যাবে।
সুভদ্রকল্যাণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের স্নাতকোত্তর। বর্তমানে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে ইংরেজি সাহিত্যে দ্বিতীয় স্নাতকোত্তর করছেন। স্তরের ছাত্র। বাংলা ও ইংরাজি উভয় ভাষাতেই তাঁর লেখা সংগীত ও সাহিত্য বিষয়ক বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ পেয়েছে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়। বহু বিশিষ্টজনের সাক্ষাৎকার সংগ্রহ করেছেন, সেগুলিও প্রকাশিত ও সমাদৃত। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর লেখা কবিতা প্রকাশ পেয়েছে। মূলত ইংরাজি ভাষায় কবিতা লেখেন সুভদ্রকল্যাণ। তাঁর আরেকটি পরিচয় রাগসঙ্গীতশিল্পী হিসেবে। সংগীতশিক্ষা করেছেন আচার্য শঙ্কর ঘোষ, পণ্ডিত বিক্রম ঘোষ, পণ্ডিত উদয় ভাওয়ালকর, ডঃ রাজিব চক্রবর্তী প্রমুখ গুরুর কাছে। পেয়েছেন একাধিক পুরস্কার ও সম্মাননা।