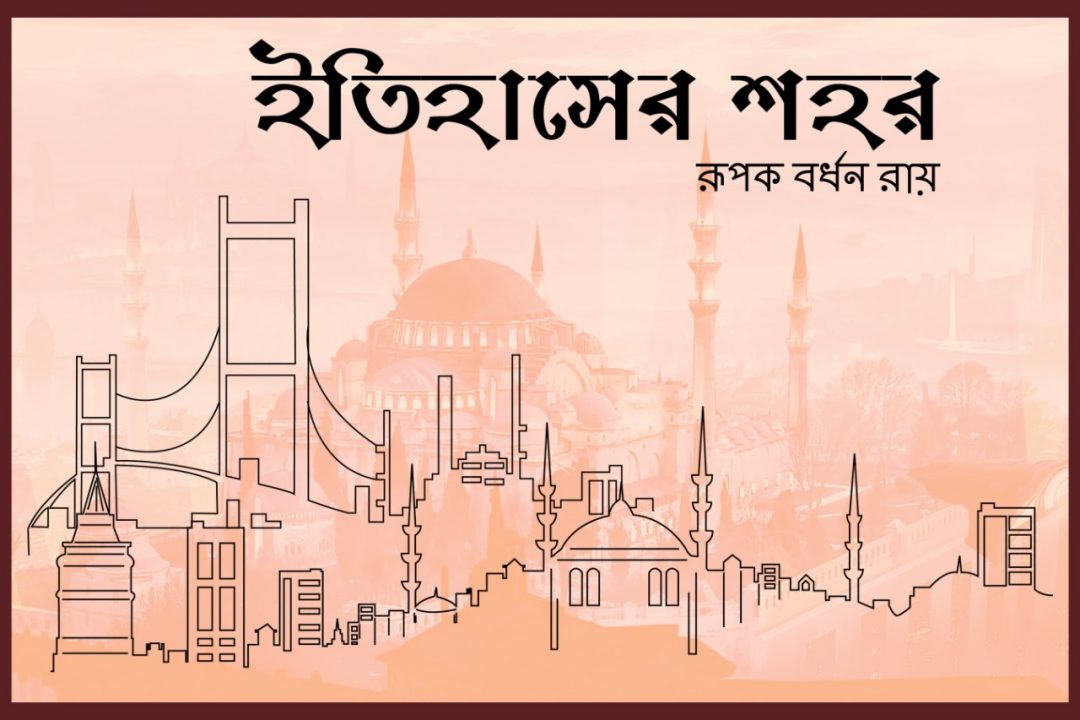২৩.০৬.২০১২, রাত ১২:৪৫, আমাস্রা, উত্তর পূর্ব তুরস্ক
হাইমে বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। খুবই স্বাভাবিক। একা হাতে সারাটা দিন গাড়ি চালিয়েছে ছেলেটা। তার উপর মৃদুমন্দ সমুদ্দুরের হাওয়ায় বসে রাতে বেশ খানিকটা বিয়ার সহযোগে একটা করে সি-ব্রিম মাছ খাওয়া হয়েছে। তাই মন মেজাজও ফুরফুরে! এই সুযোগেই বরং আজকের ডায়েরি এনট্রিগুলো সেরে রাখা যাক। কাল সারাদিনের যা প্ল্যান, বাড়ি ফিরে আর শরীর দেবে বলে মনে হয় না।
***
হাইমে কলম্বিয়ার মানুষ, বোগোটাতেই জন্ম। ফেব্রুয়ারি মাসে ইস্তানবুল আসবার পর-পরই নানা দেশের বন্ধুবান্ধব জুড়ে এক আন্তর্জাতিক গোলটেবিল তৈরি করেছি আমরা। হাইমে আর আমিই তার মধ্যমণি। তাছাড়াও আছে লিন-লিন, শান-শান, আমিন, মারিয়াম, দিলেক এমনই আরও অনেকে। ল্যাব অথবা ক্লাসের শেষে, হয় এর-তার বাড়িতে, নয় শহরের বিভিন্ন রেস্তোরাঁয়য় কিম্বা নেহাতই ইউনিভার্সিটির ক্যাফেতে সঙ্ঘবদ্ধ ডিনারের মাধ্যমে আমাদের রোজকারের আড্ডা জমে। তাছাড়া প্রায় প্রত্যেক সপ্তাহান্তে ইস্তানবুল শহর এবং তার আশপাশের ছোটখাটো জায়গাগুলো চরতে বেরনো তো রয়েইছে। ফিরি বেশ রাত করে। একআধবার তো আমি আর হাইমে, হয় ওর ঘরে, নয় আমার ঘরে আড্ডা মেরেই গোটা রাত কাটিয়ে দিয়েছি।
যাই হোক, যা বলছিলাম…
একটু সময় হাতে নিয়ে কোথাও বেড়াতে যাওয়ার ব্যাপারে মাসখানেক ধরেই আমাদের সান্ধ্য বৈঠকে তর্কাতর্কি চলছিল। সন্ন্যাসী অনেক, কাজেই গাজনও বিশেষ জমছিল না। এর হয় তো তার হয় না, এর ওই সমস্যা তো তার সেই সমস্যা। দূর! হপ্তাখানেক আগে একসঙ্গে লাঞ্চে বসে আমি, হাইমে আর লিন ঠিক করে ফেললাম, আমরা তিনজনেই বেরিয়ে পড়ব। একবার করে ফোন করা হল বাকিদের। নাঃ। বিশেষ উৎসাহ নেই কারও। আমি মনে মনে বিশেষ খুশিই হয়েছি। বেশি ভিড় আমার কোনওদিনই ভাল লাগে না।
এবার প্রশ্ন হল কোথায় যাওয়া যায়? ইস্তানবুল আসা ইস্তক মন চাইলেই মারমারা সাগরের দেখা পাই। ভালই লাগে, তবে বেড়াতে গিয়েও যদি সেই সমুদ্রই কেবল দেখতে হয়, ব্যাপারটা মনঃপূত হবে না। কাজেই আমার ইচ্ছে, পাহাড়, জঙ্গলওলা কোনও একটা ঐতিহাসিক শহরে যাওয়া যাক। লিন-দেবীর অবশ্য তুরষ্কের কোনও এক নামীদামি ‘সামার ডেস্টিনেশান’-এ জমিয়ে আরাম করার ইচ্ছে। আমি তাতে একেবারেই গররাজি। টানাপোড়েনটা ঝগড়ার দিকে মোড় নিতে হাইমেকেই দায়িত্ব নিতে হল।
“ব্ল্যাক সি-র (কৃষ্ণ সাগর) দিকটা যাই চল। একটা গাড়ি নিয়ে নেওয়া যাবে।”
আমি বললুম, “দূর সেই তো সমুদ্র!”
হাইমে: মোটেই না। যাওয়ার পথে আমরা সাফ্রানবোলুতে বেশ খানিকটা সময় কাটাব। সেখান থেকে ফিলিয়স হয়ে ব্ল্যাক সি উপকূলে আমাস্রা। উপকূলে পাহাড়ও পাওয়া যাবে। আমাস্রায় রাত কাটিয়ে ফেরার পথে আমরা ব্ল্যাক-সি সৈকত বরাবর পাহাড় ধরে ওঠানামা করব। ইস্তানবুলের কাছাকাছি পৌঁছে আবার শহরে ঢুকে পড়া যাবে। তোমার কথাও রইলো, লিনের কথাও রইল? কেমন?
আমায় আর পায় কে? হাইমের লিন-প্রীতি আমাদের কারওই অজানা নয়, তার মাঝেও যে ও এতটা ভেবেছে এই বেশি। আনন্দে আটখানা হয়ে, দু’জনকেই চটজলদি শুভরাত্রি জানিয়ে উঠে পড়লাম আমি। কাল ল্যাবে কাজ হোক বা না হোক, আজ সারা রাতটা আমার পড়াশোনাতেই কাটবে।
আমরা তিনজন কাজ ভাগ করে নিয়েছি। আমার দায়িত্বে পড়ছে প্রয়োজনীয় পড়াশোনা, যেমন কোথায় কোথায় যাব, কী তাদের গুরুত্ব, কোন রাস্তায় যাওয়া, কোন রাস্তা দিয়েই বা ফেরা ইত্যাদি। অর্থাৎ ব্যাক-স্টেজটা আমার, যা চিরকালই আমার দারুণ পছন্দের কাজ। লিনের দায়িত্বে লজিস্টিক্স। অর্থাৎ চলার পথে খাওয়াদাওয়া, বাজেট, হোটেল বুকিং ইত্যাদি। আর সবশেষে হাইমে, আমাদের সারথি, মানে গোটা ট্রিপটায় চালক ও-ই। ভয়লা!
***
সকাল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ আমরা রওনা হলাম। আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, যে তুরস্ক বা অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের অধিবাসীদের বেশিরভাগই গাড়ির কথা উঠলে এক কথায় জার্মান কোম্পানি ‘ফোক্সওয়াগন’-এর গাড়িই পছন্দ করেন। হাইমেও সেই পথের পথিক। বেছে বেছে ফোক্সওয়াগন-গলফ ভাড়া করেছে সে।

আমাদের ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস ইস্তানবুলের সমতল থেকে বেশ খানিকটা উঁচুতে। ভোর-ভোর শিরশিরে হাওয়ায় ক্যাম্পাস থেকে দৃশ্যমান মারমারা সাগরের বক্ষে উদীয়মান সূর্যের চোখ জুড়ানো ছবি খুব সুন্দর। ক্যাম্পাস ইস্তানবুলের পূর্ব প্রান্তে হওয়ায় এ যাত্রায় আমাদের বেশ খানিকটা সুবিধাই হয়েছে। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক সময় কম নষ্ট হবে । প্ল্যানটা এইরকম। প্রথমে ডি-৭ হাইওয়ে ধরে আমরা চলেছি তুরস্কের পূর্ব দিকে।
রাস্তা ধরে সোজা
সকাল সকাল ইরানি ‘সাজ়’-এর মিঠে সুর, তার সঙ্গে সদ্য বিদায় নেওয়া বসন্তের মাতাল সমীরণে মেজাজটা বেশ ফুরফুরে। ইস্তানবুল ছাড়িয়ে ডি-৭-এর আঁকাবাঁকা পথে ডান হাতে পড়ে ইজ়মিত, কোরুচুক, সাকারিয়ার মতো একাধিক শহর। সাকারিয়া ছাড়িয়ে খানিকটা এগিয়ে গেলেই ডি-৭ পূর্ব তুরস্কের প্রধান সড়ক ই-৮০-র সঙ্গে মিশে যায়। পথের পাশে ‘বোলু’ নামের আর একটি শহর পড়বে। বোলু নিজেও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক শহর।

তবে আমরা সেখানে থামব কিনা তা নির্ভর করছে আমাদের ক্ষিদে এবং সারথি, এই দুইয়ের মেজাজের উপর। তাছাড়া লিনের খাবারের ব্যাগ আমার পাশেই রাখা রয়েছে। লিন জিপিএস মেশিন হাতে বসেছে হাইমের পাশে- সামনের সিটে। বোলু ছাড়িয়ে খানিকটা এগিয়ে গেলেই আমরা ই-৮০ ছেড়ে বাঁ হাত বরাবর ডি-৭৬৫ ধরব। সে রাস্তা ‘কারাবুক’ নামক আর একটি প্রাচীন শহর থেকে দু’ভাগ হয়ে গিয়েছে। একটি যাবে ফিলিয়স, অর্থাৎ আমাদের পরবর্তী গন্তব্যে, আর অন্যটি পৌঁছে দেবে ‘সাফ্রানবোলু’ শহরে।
আসলে তার নাম পাফলাগোনিয়া
খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দে অর্থাৎ হেলেনিক-গ্রীক সময়কালে সাফ্রানবোলু অঞ্চলের নাম ছিল ‘পাফলাগোনিয়া’। হিটাইট রাজবংশের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে কাসকা নামের কিছু আদিম উপজাতি সে সময়ে পাফলাগোনিয়া শাসন করতেন। তবে এ তথ্য সম্বন্ধে বেশকিছু মতানৈক্য রয়েছে। যেমন হোমার ইলিয়াড কাব্যে বলে গেছেন যে সমসাময়িক আনাতোলিয়ার যে জনজাতি ট্রয় শহরকে ট্রোজান যুদ্ধে সাহায্য করেছিল, তারাই আসলে পাফলাগোনিয়ান।
সে যা-ই হয়ে থাকুক, সাফ্রানবোলু তূর্কিদের হাতে আসা পর্যন্ত সে অঞ্চল একে একে হিটাইট, পাফলাগোনিয়ান, সিমেরিয়ান, লিডিয়ান, পারস্য, হয়ে রোমান এবং একবারে শেষে অবশ্যই বাইজান্টিয়াম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই একাধিক হস্তান্তরের ফলে সাফ্রানবোলু নামটারও সাময়িক বিবর্তন ঘটেছে, অর্থাৎ বর্তমানে আমরা জায়গাটাকে যে নামে চিনি, তা মোটেই তার আদি নাম নয়। ইতিহাস ঘাঁটলে যে নামগুলো একে একে উঠে আসবে তা হল: দাদিব্রা, জালিফ্রে, বোরগ্লু, বুরগ্লু, বোরগুলু, বোরলু, তারাক্লি-বোরলু, তারাক্লি, জাফিরান-বোরলু, জাফিরানবোলু, জাফিরান-বেন্দেরলি, জাফিরানবোলু, জাফ্রানবোলু এবং অবশেষে সাফ্রানবোলু।
ঐতিহাসিকভাবে দাদিব্রার নাম বিশেষভাবে লক্ষণীয় না হলেও, দ্বিতীয়-তৃতীয় খৃষ্টাব্দে সেখানে পয়সা তৈরি কারখানা থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। রোমের সরকারি নথিপত্রেও পাফলাগোনিয়া অঞ্চলের ৬টি প্রধান শহরের মধ্যে দাদিব্রার নাম রয়েছে। তাছাড়া বিখ্যাত ক্যারাভান-রুট বা ব্যবসায়ীদের কাফেলা যাতায়াতের জন্য তৈরি রাস্তা এবং কৃষ্ণ সাগরের উপকূলবর্তী বন্দরগুলির কাছাকাছি হওয়ার ফলে শহরের গুরুত্ব ইতিহাসের হাত ধরে অনেকখানি বৃদ্ধি পেয়েছিল। এরই সঙ্গে সঙ্গে সাফ্রানবোলুর উচ্চতম টিলা বা ‘কালে’ থেকে ‘গুমুস’ জলধারা অবধি ছড়ানো একাধিক আঙুর-ক্ষেত বা ভাইনইয়ার্ড-এর প্রমাণও পাওয়া যায়। বাইজান্টাইন দাদিব্রা-শহরকে (হ্যাঁ সে সময়ে এতটাই তার বিস্তার) বাগে আনতে অটোম্যানদের পূর্ববর্তী সেলচুক সম্রাট মুহিদ্দিন মেসুদ শাহ-কে প্রায় চারমাস কসরত করতে হয়।
আরও পড়ুন: ড. রূপক বর্ধন রায়ের কলাম ‘ইতিহাসের শহর’: ফেয়ারি চিমনির দেশে পর্ব ১
চিঞ্চি হোজার দেশে
সেলচুক পরবর্তী সময় থেকে আতাতুর্ক পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত সাফ্রানবোলু- ইল্কহানিড, চোবানোলু, চান্দারোলু বংশের হাতে শাসিত হওয়ার পর সব শেষে অটোম্যান তুর্কিদের হাতে আসে। অটোম্যান শাসনকালে (১৫৩০ খ্রিস্টাব্দ) রাজকোষের কাগজপত্রে ১৬টি দোকান এবং গেব্রান (বর্তমান কিরানকয়) প্রদেশে সাতাশজন পারিবারিক স্থপতির হিসাব পাওয়া যায়।
১৬০০ শতাব্দীর পর সাফ্রানবোলুর মসনদে আসেন সুলতান ইব্রাহিম, এবং তার সঙ্গে সঙ্গেই শহরের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত হয় হুসেইন এফেন্দি তথা চিঞ্চি হোজার নাম। তুর্কি ভাষায় হোজা অর্থাৎ বেশ হোমড়া-চোমড়া ব্যাক্তি (আমাদের বড়দা গোছের ধরতে পারেন)। যেমন, আমাদের খুব চেনা মোল্লা নাসিরুদ্দিন সাহেব আসলে তুরস্কের নাসিরুদ্দিন হোজা। চিঞ্চি হোজা সুলতান ইব্রাহিমের মানসিক ব্যারাম সারিয়ে তোলেন এবং স্বাভাবিকভাবেই সুলতানের দাক্ষিণ্যে প্রচুর অর্থ এবং প্রতিপত্তির অধিকারী হন। সাফ্রানবোলুর প্রতি অন্ধ ভালবাসার দরুন চিঞ্চি হোজা দায়িত্ব নিয়ে শহরকে ঢেলে সাজান।
দুর্ভাগ্যবশত তার অল্প দিনের মধ্যেই সুলতান গত হলেন, এবং তারপরই চিঞ্চি হোজা নিজের জনাকয় সতীর্থদের হাতেই প্রাণ হারালেন। ফলস্বরূপ মসনদে আগত হলেন ইতিহাস খ্যাত সুলতান, চতুর্থ মেহমেত। মেহমেত পাশা-ই এরপর সাফ্রানবোলুকে তার বর্তমান রূপ দেন। শহরের মধ্যে একটি সুন্দর মসজিদ ছাড়াও তৈরি হয় ঝরনা-বাগানে ঘেরা অপূর্ব এক চত্বর বা ‘ময়দানি’। সেলচুক সময়ের গড়পড়তা নগর-পরিকল্পনা ছেড়ে বেরিয়ে আসে শহর।
ক্যারাভান রুটের বাণিজ্যকেন্দ্র
চেলালি বিদ্রোহে পর থেকেই ব্যবসায়িক কেন্দ্র হিসাবে ক্রমশ সাফ্রানবোলুর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। এর পিছনে বেশ কয়েকটা কারণ ছিল। ১৮০০ শতাব্দীর শুরু থেকেই তৎকালীন সুলতানরা ইস্তানবুলে বসে শহরের উপর কড়া নজর রেখেছিলেন। কাজেই সে শহর তখন ওসমানদের নয়নের মণি। দ্বিতীয়ত, চামড়ার কারখান বা ট্যানারী এবং তা থেকে বিভিন্ন ধরনের বাহারি জুতো (ইয়েমেনি– হাল্কা চালের হিল ছাড়া জুতো), চামড়ার সাজ পোশাক বানানোর জন্য সাফ্রানবোলুর নাম এমনিতেই মুখে মুখে ফিরত। তাছাড়া তৈরি হত তুরস্কের অন্যান্য জায়গার তুলনায় উন্নতমানের জাফরান (শহরের নামই তার প্রমাণ)।
সবশেষে ‘আইসিং অন দা কেক’ শহরের ভৌগোলিক অবস্থান; অর্থাৎ ১৮০০ শতাব্দীর শুরু থেকেই সাফ্রানবোলু ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ক্যারাভান রুট বা বাণিজ্যপথের মধ্যবর্তী গুরুত্বপূর্ণশহর। পাঠক খেয়াল করুন, এই উল্লিখিত ক্যারাভান রুট অবশ্যই ১৪০০ শতাব্দী পর্যন্ত চালু ঐতিহাসিক সিল্ক রুটেরই উত্তরসুরী। এই বাণিজ্যপথের সাহায্যে শুধু যে আর্থিক লাভই হয়েছিল তাই নয়, বিভিন্ন দেশ বিদেশের ব্যবসায়ী বা সদাগরদের যাতায়াতের ফলে এক প্রোজ্জ্বল সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবেও সাফ্রানবোলুর উত্থান হয়।

চামড়া কারখানার কথা যেমন আগেই উল্লেখ করেছি, সে সময় শহরে প্রায় ৮০টির বেশি ট্যানারির উল্লেখ পাওয়া যায়। ট্যানারি থাকায় ইয়েমেনি বা অন্যান্য জুতোর কারখানা আরও রমরমিয়ে চলতে শুরু করে। তাছাড়া ট্যানারির জন্য প্রয়োজনীয় চামড়ার জোগান চালু রাখতে একাধিক কাঁচা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানা তৈরি হয়। ১৮০০ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সাফ্রানবোলু শহরে প্রায় ৫৬০০ গবাদি পশু আমদানি করা হত।
এছাড়াও গোটা ক্যারাভান রুটের রেশম ব্যবসার বেশ খানিকটা সাফ্রানবোলুর নিজস্ব রেশম উৎপাদনের উপরই নির্ভর করত । ১৯২৩ সাল পর্যন্ত, ফুলে ফেঁপে ওঠা বিভিন্ন ব্যবসাবাণিজ্যের এই রমরমা বাজার স্বাভাবিকভাবেই বহু মানুষকে আকর্ষণ করত। সমকালীন আদমসুমারিতে লিখিত তথ্য অনুযায়ী ইতিহাসের এই উজ্জ্বল সময়ে প্রায় ৫০০০০ মানুষের ভরণ পোষণের ক্ষমতা ছিল শহরের।
তরুণ তুর্কি যখন এল
সমস্যা বাধল, ১৯২৩-এ কেমাল আতাতুর্কের হাত ধরে তরুণ তুরস্কের জন্মের পর। কেমাল পাশা পশ্চিমি আধুনিকীকরণের ধাঁচে পুরোদমে শিল্পায়ন শুরু করলেন। ইস্তানবুল, কারাবুক এবং অন্যান্য শহরে তৈরি হল আধুনিক ট্যানারি এবং তার পাশাপাশি লোহা ও ইস্পাতের কারখানা। ফলে গোটা দেশ থেকেই অতিরিক্ত অর্থোপার্জনের লোভে শ্রমজীবি মানুষ এই কারখানাগুলোয় চাকরিতে যোগ দেন।
সাফ্রানবোলুর পুরনো পদ্ধতিতে চলা কায়িক শ্রম-নির্ভর ট্যানারিগুলি আসতে আসতে গুরুত্ব হারাতে শুরু করে। ১৯৫৪ সালে গেরেদে-সাফ্রানবোলু সড়ক এবং তারপর আংকারা-জোঙ্গুলদাক রেল তৈরির সঙ্গে সঙ্গেই ঐতিহাসিক ক্যারাভান-রুটও তার জৌলুশ হারায়। সবশেষে গ্রেকো-তুর্কি যুদ্ধের পর হওয়া নাগরিক বিনিময়ের পর গ্রিস থেকে আগত মুসলমান নাগরিকরাও ক্রমে কাজ ও উপার্জনের সুবিধার্থে ইস্তানবুল, আংকারা ইত্যাদি বড় শহরগুলোতে বসবাস শুরু করেন। এর ফলে অটোমানদের নয়নমণি, তাদের সাধের সাফ্রানবোলু বেশ কিছু দশকের জন্য ইতিহাসের অন্ধগলিতে হারিয়ে যায়।

অবশেষে ১৯৭০ সালের পর গুন্দুজ ওজদেজের হাতে কারাবুক-সাফ্রানবোলু উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। ঠিক হয়, কারাবুক হবে প্রধান কার্যকরী শহর ও সাফ্রানবোলুকে নাগরিকদের বসবাসযোগ্য অঞ্চল হিসাবেই পুনর্গঠন করা হবে। সুবিধা হল অন্য জায়গায়। পুরনো গুরুত্বপূর্ণ নাগরিকরা শহর ত্যাগ করলেও, তখনও যাঁরা বাস করছিলেন, তাঁরা অন্যান্য বাড়ি-ঘরগুলোকে নষ্ট হতে দেননি। কাজেই শহরের কাঠামো এবং গুরুত্বপূর্ণ চত্বরগুলো মোটামুটি একইরকম ছিল।
কাউন্সিল অফ ইউরোপ, ১৯৭৫ সালটিকে, ‘ইউরোপিয়ান আরকিটেকচারাল হেরিটেজ ইয়ার’ ঘোষণা করায়, ইয়াভুচ ইঞ্চের হাত ধরে তুরস্ক সরকার সাফ্রানবোলুর ইতিহাসকে লোকচক্ষুর অন্তরাল থেকে ফের আলোয় ফিরিয়ে আনে।
আরও পড়ুন: ড. রূপক বর্ধন রায়ের কলাম ‘ইতিহাসের শহর’: ফেয়ারি চিমনির দেশে পর্ব ২
সাফ্রানবোলুকে নিয়ে চলা সপ্তাহব্যাপী আলোচনার নাম দেওয়া হয় ‘Safranbolu Architectural Values and Folklore Week’। এরপর ১৯৭৮ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে শহর-পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। ১৯৮৫ সালে গুরুত্বপূর্ণ পুরনো বাড়িগুলোকে চিহ্নিত ও নথিভুক্ত করা হয়, শুরু হয় কাজ। পুরনো বাড়ির অনেকগুলিকেই জমকালো বিলাসবহুল হোটেল করা হয়। ১৯৯০ সালে, সারা বিশ্বের পর্যটকদের জন্য সাফ্রানবোলুর দরজা আবার উন্মুক্ত করেন তুরস্ক সরকার।
অবশেষে, ১৯৯৪ সালে, তার বহুচর্চিত এবং বহুশতাব্দী ধরে সংরক্ষিত অটোম্যান স্থাপত্যগুলির কারণে UNESCO World Heritage Site খেতাবের হাত ধরে সমস্ত অবহেলা ঝেড়ে ফেলে পুনর্গৌরবে উঠে দাঁড়ায় আজকের সাফ্রানবোলু শহর। (চলবে)
*ছবি সৌজন্য: লেখক
ড. রূপক বর্ধন রায় GE Healthcare-এ বিজ্ঞানী হিসেবে কর্মরত। ফ্রান্সের নিস শহরে থাকেন। তুরস্কের সাবাঞ্চি বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করেছেন। বৈজ্ঞানিক হিসেবে কর্মসূত্রে যাতায়াত বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে। লেখালিখির স্বভাব বহুদিনের। মূলত লেখেন বিজ্ঞান, ইতিহাস, ঘোরাঘুরি নিয়েই। এ ছাড়াও গানবাজনা, নোটাফিলি, নিউমিসম্যাটিক্সের মত একাধিক বিষয়ে আগ্রহ অসীম।