‘ভালো লাগছে না রে তোপসে, ভালো লাগছে না। একটা নকশা, চোখের সামনে ভেসে ভেসে উঠছে। আবার মিলিয়ে যাচ্ছে।’
এই জায়গাটায় একবার আসুন। একটা টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। কথার ফাঁকে ফাঁকে, হাতের তালু খোলা বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কখনও ফেলুদার মুখের ওপর খেলে যাচ্ছে লালচে হলুদ আলো, কখনও মুখ ঢেকে যাচ্ছে অন্ধকারে। পরের দৃশ্যে প্রায়ান্ধকার ঘরে পায়চারি চলছে। শুনতে পাচ্ছি, ‘কয়েকটা লোক, তাদের কেউ কেউ মুখোশ পরে রয়েছে। কেউ বা আবছা আলোয়। কেউ বা অন্ধকারে।’
ঠাঠা রোদের ছবি সোনার কেল্লা। ব্রড ডে লাইটে গল্প এক স্টাইলে এগচ্ছে, কথোপকথনও ঝলমলে। একই গল্প চলছে, অথচ রাতের দৃশ্যে মেজাজটা আলাদা। টেনশনটা অন্য রকম। অনেক কথা না বলা থেকে যাচ্ছে, না দেখানো দৃশ্যাংশে। কেন, সে তো সত্যজিৎ-গবেষকরা বলবেন। নিজের লেখা, মারি সিটন বা অ্যান্ড্রু রবিনসনে আছে কিনা মনে পড়ছে না। এইটুকুই জানি, ছবির ক্ষেত্রে আলো থাকলে সব দেখা যায়, বা দেখানো হয়। যেটা মুখে বলা হল না, না দেখিয়ে সেটি নিশ্চিতভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হল দর্শকের কল্পনাকে উস্কে দিয়ে, স্ক্রিপ্টটা দর্শককে দিয়েই লিখিয়ে নিয়ে। লুকোছাপার এই খেলা শিল্পের মধুরতম অধ্যায়। স্টিল, মুভি, দু’ক্ষেত্রেই।
[the_ad id=”266918″]
এবার রবীন্দ্রনাথকে ধরি। আলো ছায়ার অজস্র, অনন্ত নকশি কাঁথা তাঁর সংগ্রহে। ছবির মতো গান তাঁর। কম আলো, ফটোগ্রাফিক চিত্রভাষায়, লো-লাইটে উনি কেমন এক্সপোজ়ার দিতেন দেখে নিই একবার। বিক্রম সিংয়ের গলায় শুনেছি, ‘যখন এসেছিলে অন্ধকারে, চাঁদ ওঠেনি সিন্ধুপারে।’ পরের লাইনে, যেহেতু যিনি এসেছিলেন, স্পষ্ট দেখা যায়নি, অনুভবের রোম্যান্সে তাঁকে বরণ করে নিলেন কবি। সাউন্ড ডিজ়াইনটাও চমকপ্রদ। স্পর্শের অনুরণন, প্রাণের পরে। ‘তুমি’… একটু স্পেস দিয়ে.. ‘গেলে যখন একলা চলে।’ অতন্দ্র ছায়ান্ধকার থেকে কবি শ্রোতাদের তুলে আনলেন মোলায়েম আলোয়। ‘চাঁদ উঠেছে রাতের কোলে।’ ওই আলোতেই, আজকের দিনে আধুনিকতম ক্যামেরাতেও যে দৃশ্য ধরে রাখা প্রায় অসম্ভব, ‘তখন দেখি, পথের কাছে মালা তোমার পড়ে আছে– ড্যাশ। ক্যামেরা ফেড আউট করার আগেই বা ক্ষণিকের মধ্যেই ‘বুঝেছিলাম অনুমানে এ কণ্ঠহার দিলে কারে।’ এই নির্মম বিরহসুখের চিত্রায়ন রোমান হলিডের আলোয় হত না। অপরাধ নেবেন না বঙ্গসংস্কৃতির দুই লাইটহাউস, অনেকবার বিদ্রোহের মশাল জ্বালাতে ব্যর্থ হয়ে আপনাদের ছায়াতেই আমাদের চলাফেরা, আপনাদের আলোকবর্তিকা ধার না করে বক্তব্য প্রতিষ্ঠায় নেহাতই অপারগ এই আজকের আমরা।
**
সেই কবে মানুষ কাচ দিয়ে বানিয়েছিল লেন্স। এর একপারের উজ্জ্বল দৃশ্য অন্য পারের অন্ধকার দেওয়ালে উল্টো চেহারায় দেখে, প্রাথমিক ঘোর কাটতেই শুরু করেছিল ছায়া ধরার খেলা। চকচকে রুপোর জারক রসে ভিজিয়ে শেষ পর্যন্ত ধরেওছিল তাকে। প্রথমে ধাতব পাত, পরে ফিল্ম। নেগেটিভ ফিল্ম, অর্থাৎ দিনকে রাত, রাতকে দিন। আবার লেন্সের শরণাপন্ন হয়ে এর ভেতর দিয়ে আলোকে দৌড় করিয়ে রূপাসিক্ত কাগজে ধরে ফেলেছিল রাসায়নিক ছবি। এবারে ঠিক যেমন দেখা, অবিকল তেমনই। ফটোগ্রাফ।

নগরদৃশ্য করায়ত্ত হতেই শুরু হয়ে গেল আমি আমি করা। অর্থাৎ নিজেকে ছবিতে দেখা ও দেখানোর জয়যাত্রা। অমরত্বের সহজ চাবিকাঠি। এদিকে আলোছায়াবাজি নিয়ে তুমুল হল্লা শুরু হয়ে গেলো অঙ্কনশিল্পীদের মধ্যে। দীর্ঘ সময় নিয়ে, মুন্সিয়ানার সঙ্গে রঙিন প্রতিকৃতি সৃষ্টি বনাম অদ্ভুতুড়ে যন্ত্রসৃষ্ট পোর্ট্রেট করার দৌড়ে মস্ত চ্যালেঞ্জ টের পেলেন সবাই। যদিও সাদাকালো, কিন্তু নিখুঁত অবিকল চেহারা দেখা গেল কলের ছবিতে। স্রেফ সাদা থেকে কালো এবং অজস্র মধ্যবর্তী গ্রে, কোটর থেকে তুলে আনল জ্যান্ত চোখ, ঠোঁটের ওপর ন্যূনতম ঝিলিক ফিরিয়ে দিল প্রাণবন্ত লাস্য। সবথেকে বড় কথা, যত খুশি প্রিন্ট করার সুবিধে। সাদা থেকে কালো, আলো থেকে অন্ধকারের টোনাল মায়ায় আলোকচিত্র ও মুদ্রণশিল্পের বাড়বাড়ন্ত মানুষের জীবনে নিয়ে এলো নয়া আয়তক্ষেত্র।
[the_ad id=”266919″]
একটা জাম্পকাট হোক এবারে। কালার এল, ফিল্ম গেল, সংখ্যায় বাঁধা পড়ল হিউম্যান রেস। মোবাইল ফোনে আজ হ্যালো হ্যালোর জায়গা ছিনিয়ে নিয়েছে আমি আমি। উইন্ডোজ় শব্দটা অন্য জানলা খুলে দিয়েছে বহু বছর আগেই। ডেটার আলোর ঝর্ণায় আমাদের প্রাত্যহিক স্নান। অন্ধকার মহাকাশে স্যাটেলাইটের সিগনালের ছায়ায় জীবন রহস্যময়। এই চলছে অবিরত।
**
উজ্জ্বলতম আলোকচ্ছটা কোনটি? সূর্যকে রেহাই দেব, কারণ সে আমাদের হিসেবের বাইরে। তার ঔজ্জ্বল্যের মাপ আজও অধরা। পদার্থবিদ্যা এখনও খুব স্পষ্ট কিছু বলেনি। বরং উল্লেখ করি আণবিক বিস্ফোরণের কথা। রবার্ট জুনকের ‘ব্রাইটার দ্যান এ থাউজ়েন্ড সানস’ পড়তে পারেন। নিউক্লিয়ার সায়েন্সের গোড়ার ইতিহাস। না পেলে নারায়ণ সান্যালের ‘বিশ্বাসঘাতক‘। চোখে দেখা যায় না, আণবিক বস্তুর আনাগোনা, চলন, ঘাত প্রতিঘাতে সৃষ্ট অকল্পনীয় শক্তির আবিষ্কার শেষ পর্যন্ত হাজির করেছিল মারাত্মক ধংশ ও নির্মাণের যৌথ সম্ভাবনা। ফেটেছিল অ্যাটম বোমা। এসেছিল আণবিক শক্তি প্রয়োগ।
[the_ad id=”270084″]
১৯৪৫ সালে ম্যানহ্যাটান প্রোজেক্টের শেষ ও চরম ঘটনা প্রসঙ্গে এর কাণ্ডারি রবার্ট ওপেনহাইমারের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। শক্তির ভয়ঙ্কর উদগিরণ ও অবর্ণনীয় আলোকোচ্ছাস দর্শনের পর ভাগবতগীতার বাণী শোনা গিয়েছিল ওঁর মুখে। অমিত শক্তিধর বিস্ফোরণের সৃষ্টিসুখে অথবা যন্ত্রণায় উনি উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন ‘হাজার সূর্যের আলোক সম্পাতে আকাশ যদি ফেটে পড়ে, তাহলে নিশ্চিত বুঝতে হবে এ আর কিছুই নয়, এই হল ঈশ্বরের চূড়ান্ত শক্তিরূপ।’ পরে আবারও বলেছিলেন, অর্জুনকে বলা কৃষ্ণের কথা ‘আমিই এখন মৃত্যু, দুনিয়া ধ্বংসের কান্ডারি।’
বিক্রম সিংয়ের গলায় শুনেছি, ‘যখন এসেছিলে অন্ধকারে, চাঁদ ওঠেনি সিন্ধুপারে।’ পরের লাইনে, যেহেতু যিনি এসেছিলেন, স্পষ্ট দেখা যায়নি, অনুভবের রোম্যান্সে তাঁকে বরণ করে নিলেন কবি। সাউন্ড ডিজ়াইনটাও চমকপ্রদ। স্পর্শের অনুরণন, প্রাণের পরে। ‘তুমি‘… একটু স্পেস দিয়ে.. ‘গেলে যখন একলা চলে।’ অতন্দ্র ছায়ান্ধকার থেকে কবি শ্রোতাদের তুলে আনলেন মোলায়েম আলোয়।
বিশ্বজুড়ে বিতর্ক ও অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়েছিল এই দর্শনে। ধ্বংসের অন্ধকার কীভাবে অত্যুজ্জ্বল মানবধর্মের পরিচায়ক হয়? ঈশ্বর, তিনি যেই হোন না কেন, যুগে যুগে প্রায় সর্বধর্মেই তাঁর দ্যুতিময় রূপের বর্ণনা পাওয়া যায়। নিদেনপক্ষে মাথার পিছনে এক আলোর আভা, যা স্রষ্টাকে সৃষ্টির ওপরে আসীন করে। আলোর নীচেই অন্ধকার, বা বলা উচিত আলোকহীন অঞ্চলেই ছায়ার আগ্রাসনে জমি দখল করে অন্ধকার। এ হেন ঘোর গভীরতার উল্লেখও রয়েছে কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক ও কথাকারদের রচনায়। প্রায়ান্ধকার আলোর রঙকেও ছুঁয়ে যাই একবার। এক ভীষণ রাগি যুবক কিন্তু লিখে গেছেন ‘শহরে জোনাকি জ্বলে না নয়তো, কুড়োতাম সে আগুন নীল হয়তো, যা কিছু নেই, নাই বা হল সব পাওয়া, না পাওয়ার রঙ নাও তুমি।’ এর আগের যুগের অন্য আলোয় ভেসে গেছে উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা, ‘চৈত্রের রৌদ্রে, উদ্দাম উল্লাসে।’
**
আর একবার ছবির দুনিয়ায় ফেরা যাক। এক্সট্রিমকে নিয়ে মাতামাতি করার পাশাপাশি মধ্যমালোকের প্রসঙ্গ তুলি। আঁকা বা তোলা ছবিতে মিডল টোনের আসন আরও পোক্ত। জীবনের সর্বাংশই ওয়াশড আউট বা ব্ল্যাক আউট হতে পারে না । কনট্রাস্টের আপাত-ঝঙ্কার আমাদের থমকে দিতে পারে। বিস্তার আর গভীরতর খননে আগ্রহী হলে নামতে হবে মাঝেরহাটে। প্রাচীনতম আগ্রহ ও উত্তেজনার বিষয় হল আদিম আকর্ষণের জৈবিক ও মানুষিক টানাপোড়েন। এ নিয়েই করে খাচ্ছেন সব শিল্পীরা। ‘বেসিক ইনস্টিংক্ট‘এর কুখ্যাত উরুবদল দৃশ্যের অনেকবছর পরেও আমরা দৌড়ই ‘ফিফটি শেডস অফ গ্রে‘ দেখতে। চরমের ব্র্যাকেটের মধ্যে নরমের পেলব বিস্তারকে চিত্রায়িত করে গেছেন অনেক যুগপুরুষ। নিশ্চয়ই ভুলে যাননি সত্যজিতের ক্যামেরাশিল্পী সুব্রত মিত্রকে। সাদা কাপড় টাঙিয়ে বাউন্স লাইট দিয়ে স্বাভাবিক আলোর পরিবেশ সৃষ্টিতে যাঁর ছিল জগৎজোড়া সম্মান। থিয়েটারে এটি শক্ত কাজ, কারণ দর্শকের চোখের আড়াল থেকে তীব্র একপেশে আলো প্রক্ষেপ করা ছাড়া উপায় নেই। তাই নাটকের অভিজ্ঞতা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অতিনাটকীয়। প্রাক-সুব্রত পর্বে সিনেমাও এই আলোকদোষে দুষ্ট ছিল।
নগরদৃশ্য করায়ত্ত হতেই শুরু হয়ে গেল আমি আমি করা। অর্থাৎ নিজেকে ছবিতে দেখা ও দেখানোর জয়যাত্রা। অমরত্বের সহজ চাবিকাঠি। এদিকে আলোছায়াবাজি নিয়ে তুমুল হল্লা শুরু হয়ে গেলো অঙ্কনশিল্পীদের মধ্যে। দীর্ঘ সময় নিয়ে, মুন্সিয়ানার সঙ্গে রঙিন প্রতিকৃতি সৃষ্টি বনাম অদ্ভুতুড়ে য্ন্ত্রসৃষ্ট পোর্ট্রেট করার দৌড়ে মস্ত চ্যালেঞ্জ টের পেলেন সবাই। যদিও সাদাকালো, কিন্তু নিখুঁত অবিকল চেহারা দেখা গেল কলের ছবিতে।
এই মুহূর্তে আবার ফিরে এসেছে অপ্রত্যাশিত চড়া আলোর আক্রমণ। সুবিখ্যাত আন্তর্জাতিক চিত্রসংস্থা ম্যাগনামে নবতম ভারতীয় শিল্পী সৌরভ হুডার কাজে এটি টের পাবেন। আবার প্রকৃতিতে, যেখানে ক্যানভাসটা বড়, নরম আলো নিয়ে মীড়ের কাজ সহজেই দেখতে পাই আনসেল অ্যাডামসের সাদা কালো ফটোগ্রাফি থেকে শুরু করে অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, রামকিঙ্করের টোনাল মাধুর্যে। পিকাসো, হুসেন খেলতেন খণ্ডিত কনট্রাস্টে। গণেশ পাইন নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারে। ছবির কাজই হল মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর বারান্দায় হাতছানি দেওয়া। একই মাধ্যমের বিশ্বস্ত হাত ধরে আমরা নিশ্চিন্তে এগিয়ে যাই ওই একই বারান্দা থেকে প্রায়ান্ধকার বেডরুমে। ব্যাটম্যান আলোর মুখ দেখেন না। সুচিত্রা মুখে ধরে রাখেন যথোপযুক্ত আলো। ঝলক ও পলকের মধ্যে এক্কাদোক্কা খেলে চলি আমরা।
শুভময় মিত্র আদতে ক্যামেরার লোক, কিন্তু ছবিও আঁকেন। লিখতে বললে একটু লেখেন। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে অনেকরকম খামখেয়ালিপনায় সময় নষ্ট করে মূল কাজে গাফিলতির অভিযোগে দুষ্ট হন। বাড়িতে ওয়াইন তৈরি করা, মিনিয়েচার রেলগাড়ি নিয়ে খেলা করা, বিজাতীয় খাদ্য নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করা ওঁর বাতিক। একদা পাহাড়ে, সমুদ্রে, যত্রতত্র ঘুরে বেড়াতেন। এখন দৌড় বোলপুর পর্যন্ত।




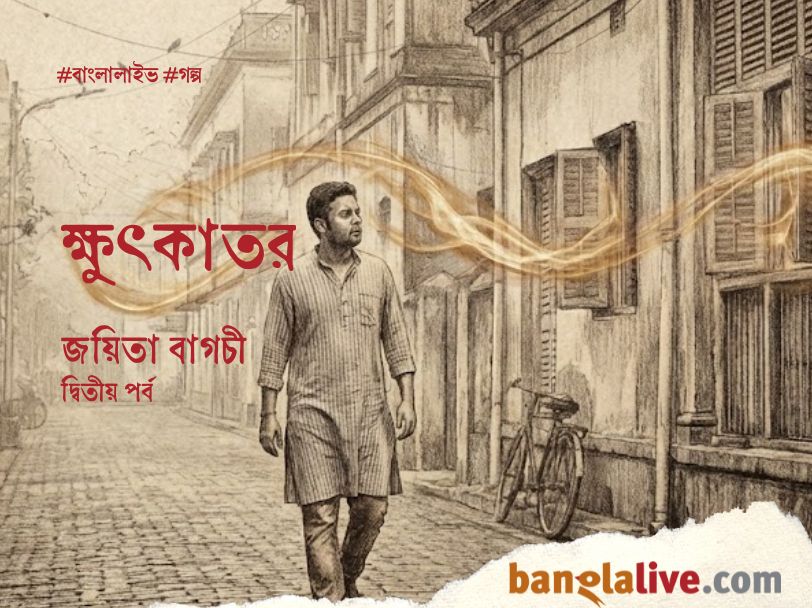



















One Response
আলোকের এই ঝরনাধারায় …