ভোররাতে ঘুম ভাঙতেই দেখি জাহাজ কখন নোঙর ছেড়ে ভেসে পড়েছে জলে। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে লাউঞ্জে আসি। আমরা পৌঁছেছি আসোয়ানের শেষ প্রান্তে। জাহাজের সঙ্গে ঘাটের যোগাযোগ হতেই নদীর পুব পাড়ে চলে আসি। প্রকৃতি এখনও আধোঘুমে। বাঁধানো রাস্তা পেরিয়ে খানিকটা উঁচুতে কোম ওমবো মন্দিরে উঠে আসতেই দেখি ভোরের আলো পড়েছে মন্দিরের সোনা-রঙা পাথরে। মন্দির এখনও বন্ধ, তাই একটা উঁচু পাথরে বসি। এখানে নীলনদের (Nile) বিস্তার খুব বেশি। এত ওপর থেকে তার নীল জলরাশি, ওপারের লালচে মরুভূমি, ছোট বড় জলযান মিলিয়ে এক ক্যানভাসে আঁকা ছবি মনে হচ্ছে। নদী কখনও ছবি আঁকে, কখনও সে নিজেই ছবি হয়ে যায়।
৭টায় মন্দিরের দরজা খুলতেই ভিতরে ঢুকলাম। কোম-ওমবো মন্দিরটি আসলে যুগ্ম মন্দির। দক্ষিণে দেবতা সোবেকের অধিষ্ঠান, রূপ যার কুমিরের। উত্তরে আছেন বাজপাখির রূপধারী দেবতা হারোয়েরিস। ট্যলমিদের তৈরি এই মন্দির, তাদের স্থাপত্যের মনোমুগ্ধকর নিদর্শন। খুঁটিয়ে দেখে যখন জাহাজে ফিরলাম, রবির আলো আঁকিবুঁকি কাটছে নদীর জলে।

স্নানের পর ব্রেকফাস্ট সারার ফাঁকেই জাহাজ ভেসে ভেসে পৌঁছে গেছে এডফু বন্দরে। আবার সেই বোর্ডিং পাশ হাতে নিয়ে নেমে আসতেই চোখে পড়ল রেলিং-এর ওপারে অপেক্ষারত শয়ে শয়ে এক্কা গাড়ি। গাইডের নির্দেশিত গাড়িতে উঠে বসতেই ঘোড়ায় টানা গাড়ি ছুটল ঘিঞ্জি শহরের মাঝখান দিয়ে। যেতে যেতেই দেখলাম ফুটপাথে বেঞ্চে অথবা চেয়ারে বসে স্থানীয়দের চায়ের কাপ হাতে তুমুল আড্ডা চলছে, সঙ্গে গড়গড়ায় সুখটান। মিনিট চল্লিশ পর গাড়ি থামল মিশরের দ্বিতীয় বৃহত্তম ও একমাত্র অক্ষত মন্দির এডফুর সামনে। মন্দির চত্বরটি প্রায় ২০ ফুট উঁচু পাঁচিল দিয়ে দুর্গের মতো ঘেরা। এই মন্দিরটি বাজপাখিরূপী দেবতা হোরাসের। ভিতরে ঢুকতেই সামনের প্রাঙ্গণে হোরাসের বিশাল পাথরের মূর্তি। এছাড়াও এখানে আছে হাইপোস্টাইল হল, উঁচু থাম, প্রকাণ্ড তোরণদ্বার, গর্ভগৃহ ও গ্রিক-রোমান স্থাপত্যের নিদর্শন। মন্দিরের সব জায়গায় প্রাচীন মিশরীয় লিপি খোদাই করা। বিশালত্বে কারনাকের পরেই এর স্থান।

জাহাজে ফিরে চললাম ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আলাপ করতে। পাঁচতারা জাহাজের সবাই স্যুটেড–বুটেড হলেও, ক্যাপ্টেনের পোশাক কিন্তু সাদা আলখাল্লা। মানুষটি অমায়িক, কিন্তু ইংরাজি জানেন না, তাই আলাপ বেশিদূর এগোলো না। পরে জেনেছিলাম, এরা বিশেষ লেখাপড়া জানে না, অভিজ্ঞতার নিরিখে এদের নিয়োগ করা হয়।
কেবিনে ফিরে ব্যালকনিতে বসে চেয়ে রইলাম নীলনদের (Nile) দুই-তীরের চলমান দৃশ্যের দিকে। দক্ষিণ মিশরে মহীরুহ বলতে কিছু নেই। বনজ বৃক্ষ বলতে শুধু খেজুর গাছ। অবারিত দৃষ্টি তাই বহুদূর চলে যায়। পূর্বপাড়ে দেখছি সবুজ চাষের খেত, খেজুর গাছের সারি, মাটির ঘরবাড়ি। নদীর ধারে চরছে ঘোড়ার দল। পশ্চিমতীরে শুধুই রুক্ষ লালচে খয়েরি রঙের পাহাড়। নদী প্রতি মুহূর্তে এঁকে চলেছে কত যে ছবি! নদীর বুকে মাঝে মাঝে রয়েছে ছোট ছোট দ্বীপ। দ্বীপগুলির কোনওটি জনহীন, কোথাও রয়েছে মানুষের বসতি। হঠাৎ নদীতীরের রেললাইন দিয়ে, লালচে মরুভূমির গা ঘেঁষে ঝমঝমিয়ে ছুটে চলে গেল ট্রেন। উটের গাড়িতে শস্য বোঝাই করে, গ্রামের পথে ঘরে ফেরে চাষি।
মাছের লোভে পানকৌড়ি চক্রাকারে ঘুরতে থাকে জলের ওপর। হাওয়ার টানে ভেসে চলে ফেলুকা। রকমারি জাহাজ চলছে রাজকীয় ভঙ্গিতে। ঢেউ ভাঙছে ছলাৎ ছলাৎ। কখনও কখনও নদীর দুই পাড় কাছাকাছি এসে কানাকানি করে, আবার সরে যায় দূরে।
শুধু নীলনদের (Nile) চলমান ছবি দেখেই কাটিয়ে দেওয়া যায় বেশ কয়েকটা দিন।

দিন ফুরাতেই পশ্চিম পাড়ে সূর্য মরু পাহাড়ের পিছনে মুখ লুকালো, আর জাহাজ পৌঁছল এসনা লকগেটের কাছে। লকগেট খোলার আগেই তৈরি হয় এক অন্য ছবি। ছোট ছোট ডিঙি-নৌকায় পশরা সাজিয়ে আফ্রিকান উপজাতিরা নৌকা ভেড়ায় জাহাজের কাছে। এরপর জিনিসগুলো প্লাস্টিকে মুড়ে ছুড়ে দেয় ডেকে। চিৎকার করে চলে দরাদরি। পছন্দ হলে ক্রেতাও একই পদ্ধতিতে টাকা ছোড়ে নৌকায়, দোভাষীর কাজ করে গাইড। জীবিকার প্রয়োজনেই আবিষ্কার হয় কত অভিনব পদ্ধতি!
কিছুক্ষণ পরে লকগেট খুলতেই জাহাজ একটি খোপে ঢুকে পড়ল। গেটের দুপাশের জলস্তর দুরকম। জাহাজ ঢুকতেই পেছনের গেট বন্ধ হয়ে গেল। এবার জলস্তর নামিয়ে সামনের দিকের জলস্তরের সঙ্গে সমান করতেই জাহাজ অনায়াসে বেরিয়ে গেল। ডেকে দাঁড়িয়ে সমস্ত ব্যাপারটি আমরা খুব উপভোগ করলাম।
ভোররাতে ঘুম ভাঙতেই দেখি একটু একটু করে জেগে ওঠার প্রস্তুতি নিচ্ছে প্রকৃতি। দুয়েকটা নৌকা পাতলা অন্ধকারেই ভেসে পড়েছে জলে। প্রত্যুষের আলোয় চমৎকার লাগছে পশ্চিমতীরে মরুপাহাড়ের গায়ে রানি হাথসিপুটের মন্দির।

নদীসঙ্গ ছাড়তে ইচ্ছা না করলেও সারাদিনের ঠাসা প্রোগ্রামের কথা ভেবে তৈরি হয়ে নিলাম। প্রতিদিনের মতো নানা সুখাদ্যে পেট বোঝাই করে বেরোতেই দেখি সারারাত চলার পর জাহাজ এখন লুক্সরের জাহাজঘাটায়, কিন্তু তার আগে রয়েছে বেশ কয়েকটি জাহাজ। একে একে এরকম ৫টি জাহাজের ভিতর দিয়ে এসে ঘাটে অপেক্ষারত বাসে উঠলাম। বাস ছুটল শহরের পথে। মসৃণ, পরিচ্ছন্ন, রাস্তার পাশের বাড়িগুলিতে আভিজাত্যের ছাপ, ঐতিহাসিক শহর বলে নামী দামি হোটেলও প্রচুর। শহর ছাড়াতেই গ্রাম, চাষের খেত। মরু বিজয়ের কেতন উড়িয়ে সবুজ মাঠ ফসলে ভরিয়ে তুলছে চাষি। মোটরগাড়ির সঙ্গে এক্কা গাড়িও চলছে রাস্তায়। দূরে দেখা যাচ্ছে রঙিন পাহাড়।
গ্রাম ছাড়িয়ে, সেতু পেরিয়ে মরুপ্রান্তরের মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে বাস চলল নদীর পশ্চিমপাড়ের সেই পাহাড়-শ্রেণীর কাছে। আমাদের সামনে, ডাইনে, বাঁয়ে প্রায় ৩০০ মাইল বিস্তৃত এই পাহাড়ের মধ্যেই রয়েছে লুকানো সমাধিক্ষেত্র, যা কিংসভ্যালি নামে পরিচিত।

প্রথমে রাজাদের তৈরি মন্দিরে, তাদের মৃতদেহ শুদ্ধিকরণ করে মমি তৈরির প্রক্রিয়া চলত। ৭০ দিন পরে সেই মমি লোকচক্ষুর অগোচরে নিয়ে যাওয়া হত, আগে থেকে পাহাড়ের গুহায় তৈরি এইসব গোপন সমাধিকক্ষে। মমির সঙ্গে থাকত জীবিত অবস্থার সমস্ত বিলাস উপকরণ। গুহাকক্ষ অলংকৃত করা হত নানা ধরনের ভেষজ রং দিয়ে। সমস্ত কিছু সম্পন্ন হলে, গুহামুখ পাথর দিয়ে বন্ধ করা হত, যাতে বাইরে থেকে কিছু বোঝা না যায়। কালের প্রবাহে মানুষ ভুলে যায় এই গুহাগুলির কথা। প্রায় ৪,০০০ বছর পর যখন এগুলি আবিষ্কৃত হয়, তখন দেখা যায় কঠোর গোপনীয়তা সত্ত্বেও ভিতরের ধনসম্পদ লুণ্ঠিত হয়ে গেছে।
টিকিট হাতে নিয়ে ভিতরে ঢুকতেই ট্রলি ট্রেন নামিয়ে দিল গুহাগুলির সামনে। এখানে প্রায় ৬৪টি গুহা বনাম সমাধিকক্ষ আছে, যার মধ্যে ৬২ নম্বর গুহাটি তুতানখামেনের। সৌভাগ্যবশত এটি একমাত্র গুহা, যেটি ধনসম্পদসহ আবিষ্কৃত হয়েছিল।
সবগুলি সময়াভাবে দেখা সম্ভব নয়, তাই আমরা মাত্র ৩টি গুহা দেখলাম। গুহাগুলির প্রবেশপথের দুপাশের দেওয়াল, সিলিং, সমাধিকক্ষের চিত্রাঙ্কণ এত নিখুঁত ও উজ্জ্বল যে দেখে বিস্ময় লাগে। ভাবতে অবাক লাগে, সভ্যতার সেই আদি যুগে মানুষ সব বিষয়ে কত পারদর্শী ছিল!
এখান থেকে বাস আমাদের নিয়ে এল মিশরের প্রথম মহিলা ফ্যারাও হাথসিপুটের মন্দিরে। অসাধারণ মন্দিরটি পাহাড় কেটে তৈরি এবং আল-বাহারি নামে পরিচিত। এর ঠিক উল্টোদিকে নদীর অপর তীরে রয়েছে বিখ্যাত কারনাক মন্দির। মন্দিরে শতাধিক মূর্তি থাকলেও সবচেয়ে আকর্ষণীয় এর অবস্থান ও স্থাপত্য।

আজ অবকাশ খুব কম। জাহাজে ফিরে লাঞ্চের পর আড়াইটে নাগাদ রওনা দিলাম বিশ্বের এবং অবশ্যই মিশরের বৃহত্তম মন্দির কারনাকের উদ্দেশে। প্রাচীনকালে মিশরীয়রা বিশ্বাস করত প্রতিদিন পুবাকাশে একটি নূতন সূর্যের উদয় হয় এবং দিনান্তে পশ্চিমাকাশে তার মৃত্যু হয়। মিশরের অন্যান্য মন্দিরের মতো কারনাকের মন্দিরও তাই পূর্বদিকে আর সমাধিক্ষেত্রগুলি নদীর পশ্চিম তীরে।
কারনাক সূর্যদেবতা আমন ও রা-এর উদ্দেশে নিবেদিত। প্রধানত সূর্যমন্দির হলেও, কারনাক বস্তুত বহু মন্দিরের সমাহারে এক সুবিশাল মন্দির কমপ্লেক্স। এখানে বিশাল এলাকা জুড়ে যে প্রত্ন-নিদর্শন ছড়িয়ে আছে, তা কয়েক ঘণ্টায় দেখা অসম্ভব। এই জন্য একে পৃথিবীর বৃহত্তম ‘মুক্ত সংগ্রহশালা‘ বলা হয়। কারনাকের বিশালত্ব বোঝানোর জন্য দুটি উদাহরণ যথেষ্ট। এখানে যে হাইপোস্টাইল হল আছে তার আয়তন প্রায় দুশো বিঘে। হলে প্রায় ১৫০টি থাম আছে, যেগুলি প্রায় সাততলা সমান উঁচু। থামগুলির গায়ে খোদাই করা আছে দেবতা ও রাজাদের জীবনের নানা ঘটনা, যুদ্ধ ও শাস্তির বর্ণনা। এছাড়া ফ্যারাওরা একক পাথরের খণ্ডকে ত্রিকোণাকৃতি দীর্ঘ স্তম্ভের আকারে কেটে শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে স্থাপন করতেন, যাদের বলা হত ওবেলিস্ক। বর্তমান মিশরে যে সাতটি ওবেলিস্ক আছে, তার মধ্যে তিনটিই আছে কারনাকে। এখানকার সর্বোচ্চ ওবেলিস্কটি ৯০ ফুট উঁচু, ওজন প্রায় ১৫০ টন।

কারনাক মন্দিরের গঠন, তার স্থাপত্যশৈলী, বিশালত্ব, ভাবনার অভিনবত্বে বিস্মিত হলেও, আপ্লুত হলাম অন্য কারণে। আজ এখানে প্রচুর স্থানীয় মানুষের ভিড়। তাদের ভালবাসা ও আন্তরিকতার বন্যায় আমরা ভেসে গেলাম। নবীন-প্রবীণ সবার মুখেই এক কথা— ‘লাভ ইন্ডিয়া‘। প্রত্যেকে এগিয়ে এসে করমর্দন করছে, ছবি তুলছে, জড়িয়ে ধরছে। এখানে না এলে অজানা থেকে যেত ভারতবর্ষ কত আদরণীয় এদের কাছে।
ভরা মন নিয়ে পড়ন্ত বিকেলে চলে এলাম লুক্সর মন্দিরে। কারনাকের মতো না হলেও এর পরিধিও বিশাল। এটিও সূর্যদেবতা আমন-রা’র মন্দির। আগে এই দুটি মন্দির নীলনদ থেকে খনন করা একটি খাল দিয়ে যুক্ত ছিল। প্রাচীন মিশরের ‘ওপেট‘ উৎসবের সময় লুক্সরের দেবতাকে নৌকা করে ওই খাল দিয়ে কারনাকে নিয়ে যাওয়া হত। ১৫ দিন পর একই পথে দেবতা লুক্সরে ফিরে আসতেন।
মূল তোরণদ্বার পেরিয়ে আমরা একটি বিশাল হলঘরে পৌঁছলাম। এরপর গর্ভগৃহ, যেখানে দেবতা বিরাজমান। রোমান আমলে হলটি তাদের উপাসনাস্থল হিসাবে ব্যবহৃত হত। ভাস্কর্য ও স্থাপত্যে, তাদের শিল্পকলার ছাপ এখানে স্পষ্ট।

সন্ধ্যা নামতেই আলোকমালায় সেজে উঠল মন্দির। এক অসাধারণ দৃশ্যের সাক্ষী হয়ে জাহাজে ফিরে আসতে আসতে দেখলাম নদীর বুকেও আলোর বন্যা। অসংখ্য আলোকোজ্জল জাহাজ, ফেলুকা, নৌকা ভাসছে তার বুকে।
নদীবক্ষে আজ আমাদের শেষ রজনী। জাহাজ কাল যাত্রা শুরু করবে আসোয়ানের দিকে, আমরা ফিরে যাব কায়রোয়। ডিনারের পর অপেক্ষা করছিল বিরাট চমক। জাহাজ কতৃপক্ষ নিয়ে এলেন এক বিশাল কেক, যার ওপর লেখা ‘Good Bye’। শুরু হল ওদের সম্মিলিত নাচ ও গান। ভাষা না বুঝলেও সুরের মূর্ছনা, ঝঙ্কার, আন্তরিকতায় আমাদের হৃদয় কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেল।
কেবিনে ফিরে চলে এলাম ব্যালকনিতে। বিজন রাতে বহমানা নদীর দিকে অনিমিখে তাকিয়ে আছে, আধফালি চাঁদ। দেখতে দেখতে মনে হয়, সেকালে যেমন, একালেও এই নীলনদ মিশরের প্রধান অবলম্বন। সভ্যতার সেই আদিম যুগে, বর্তমান মরুভূমি অঞ্চল এই নদীর তীরভূমি ঘন জঙ্গলে আবৃত ছিল। এই নদী তীরবর্তী অঞ্চলেই ৫,০০০ বছর আগে মিশরীয় সভ্যতার উদ্ভব। প্রাচীন আফ্রিকার যেসব জাতি কৃষি ও পশুপালন প্রক্রিয়া রপ্ত করে, তাদের মধ্যে নীলনদের অববাহিকার লোকেরা ছিল অগ্রগণ্য। পরে এই জায়গার নাম হয় মিশর। এখানকার অধিবাসীরা নীলনদের বন্যাকে কাজে লাগাতো। বন্যার জল সরে গেলে যে পলিমাটি জমতো, তাতে তারা শস্য ও পশুচারণের ঘাসের চাষ করতো। নীলনদের বন্যার ফলেই খাদ্য উৎপাদনে মিশর সাফল্য লাভ করে ও লাঙ্গলের প্রচলন হয়। এই জন্যই মিশরকে নীলনদের দান বলা হয়।
রাত গভীর হয়ে আসছে, কাল ভোরেই কদিনের ভাসমান আবাস ছেড়ে যাত্রা করব নতুন গন্তব্যে। বড় উপভোগ্য ছিল এই জলযাত্রা। শুধু ইতিহাস, স্থাপত্য, ভাস্কর্য নয়, চিত্রকর নীলনদের জন্যও আমি আবার এদেশে আসার জন্য ব্যাকুল প্রতীক্ষায় থাকব।
(সমাপ্ত)
প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক, ভ্রামণিক, পর্বত-পদযাত্রী, ভ্রমণ লেখক, ট্রাভেল রাইটার্স ফোরামের সদস্য...











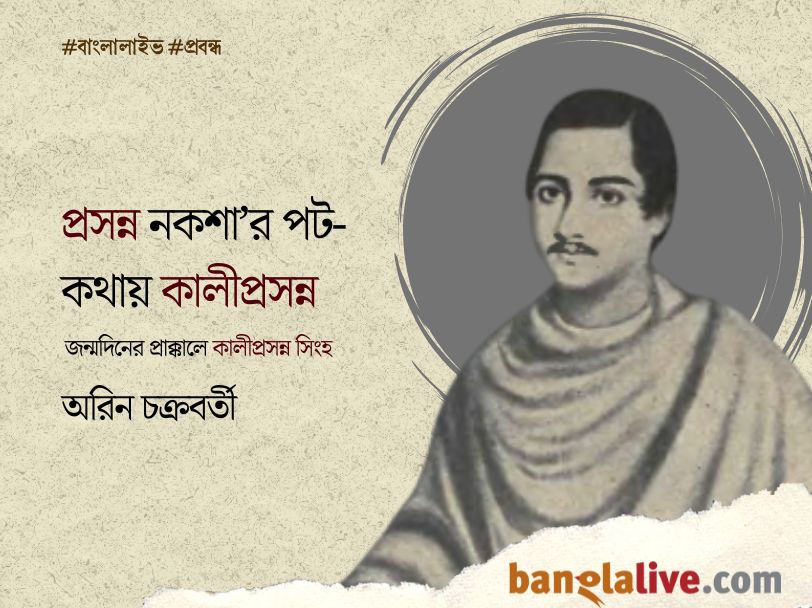






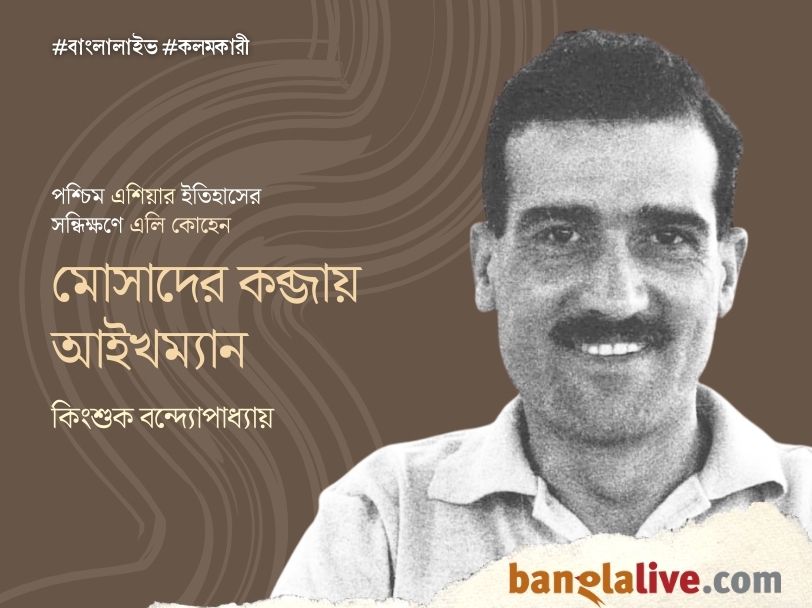







One Response
ভালো লাগলো। বিস্তারিত বিবরণ।