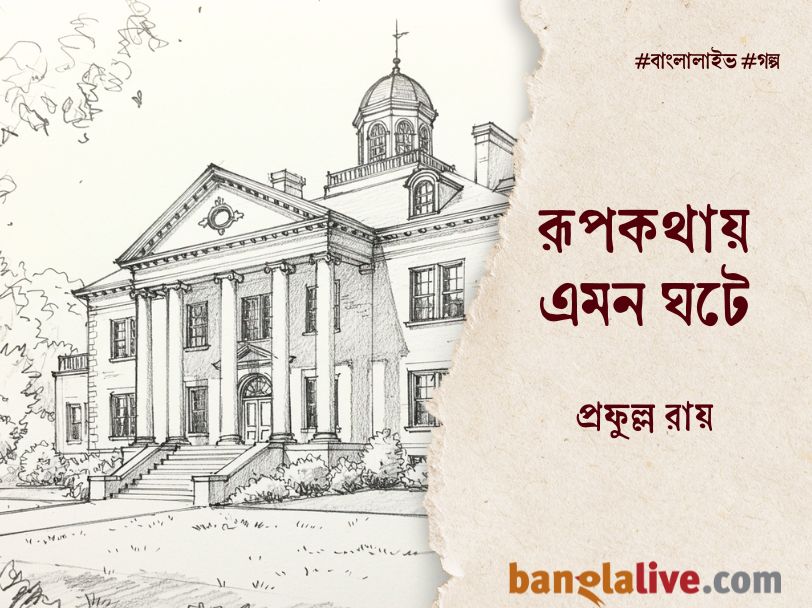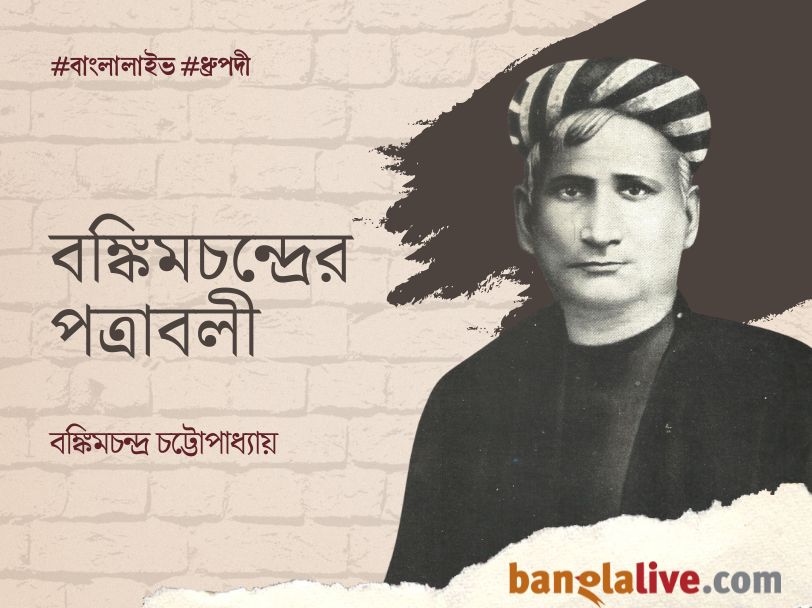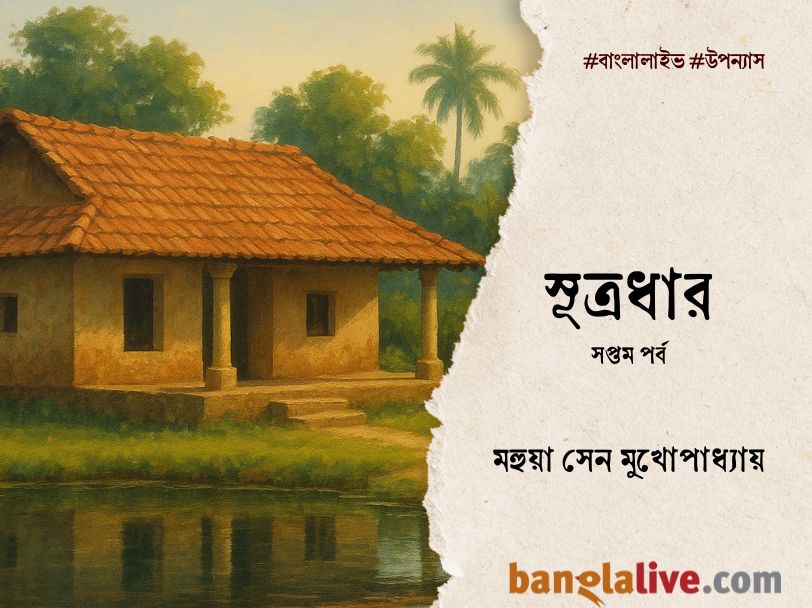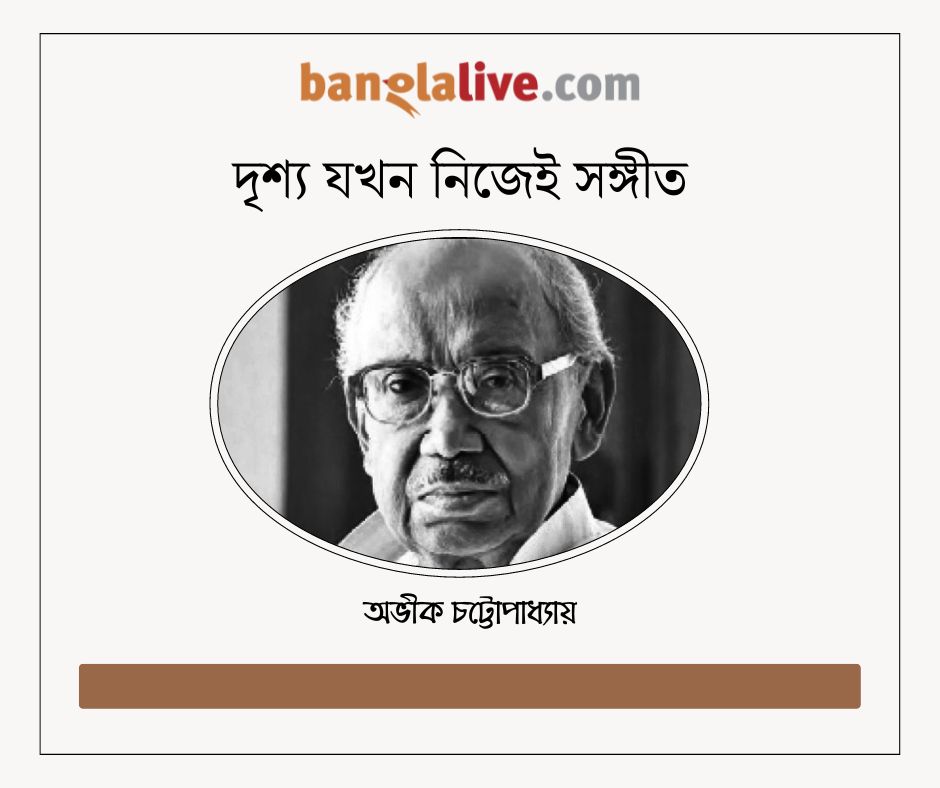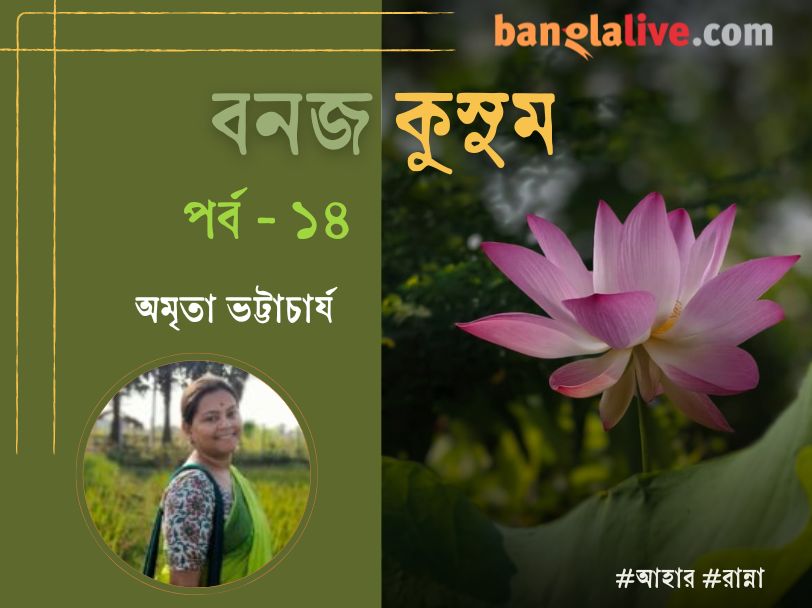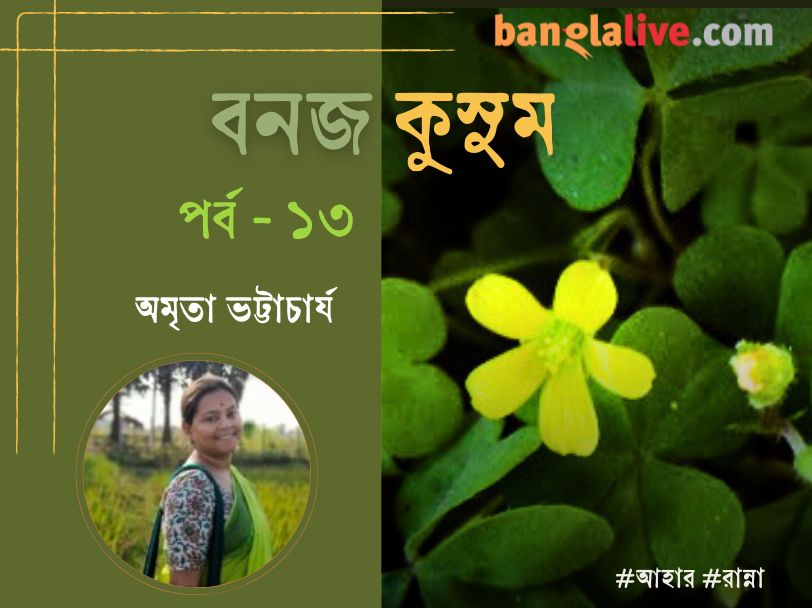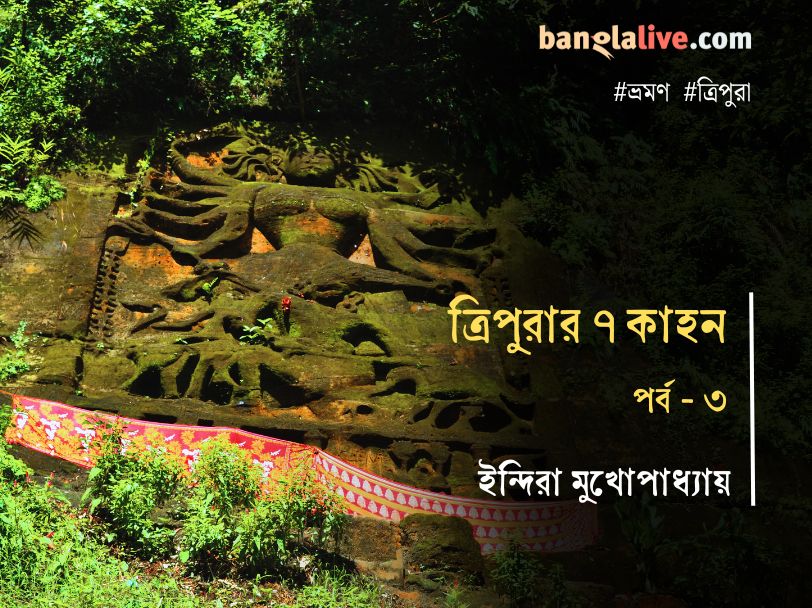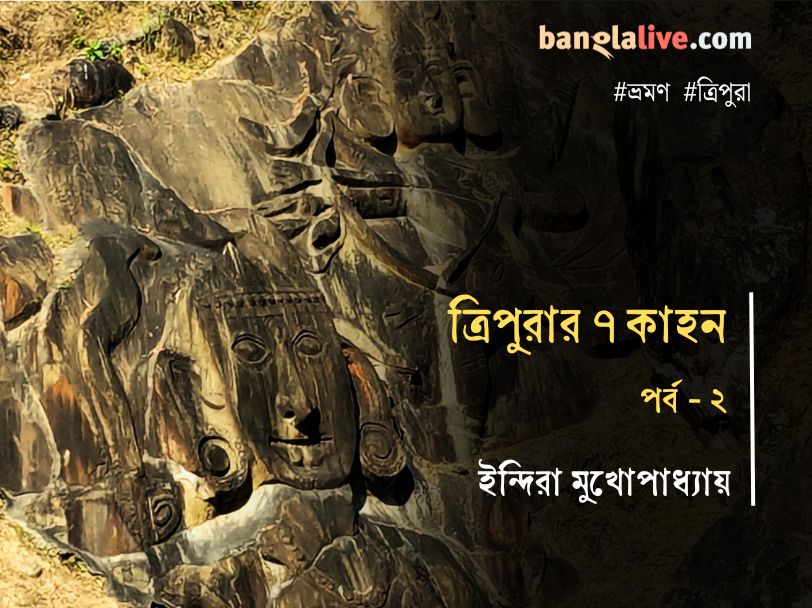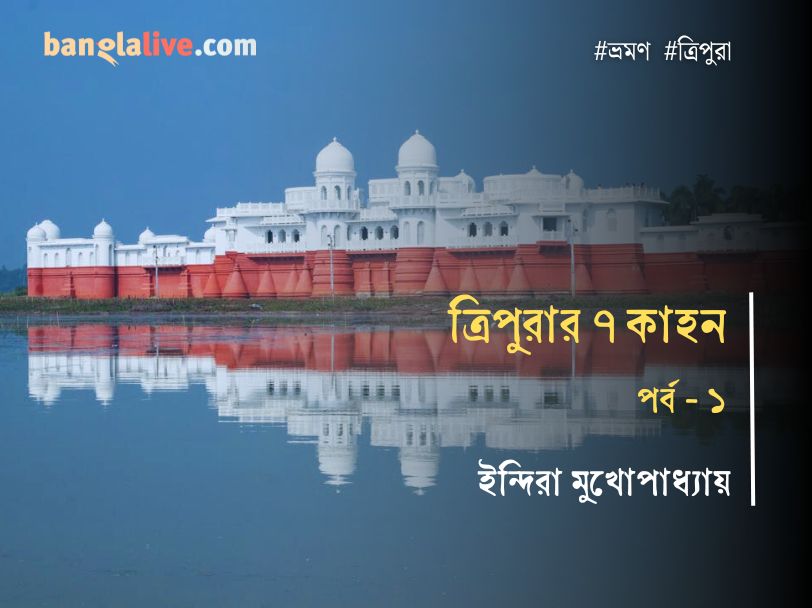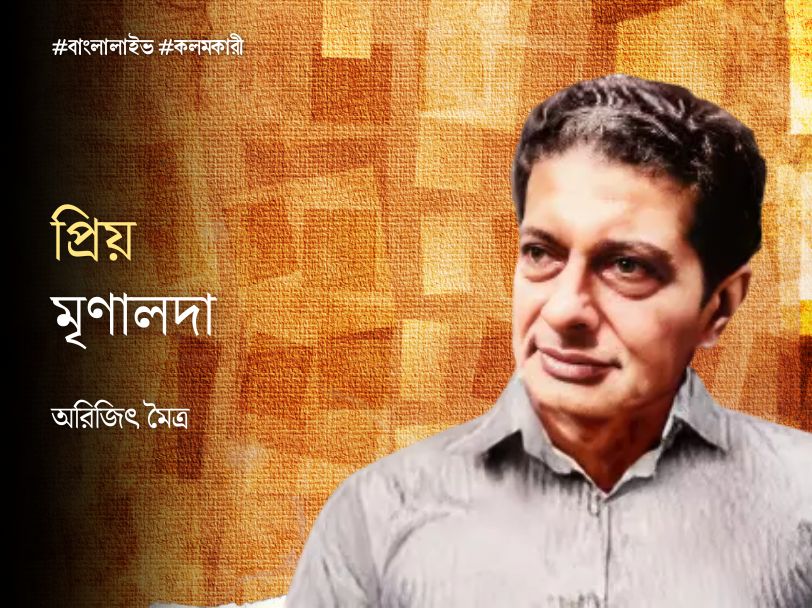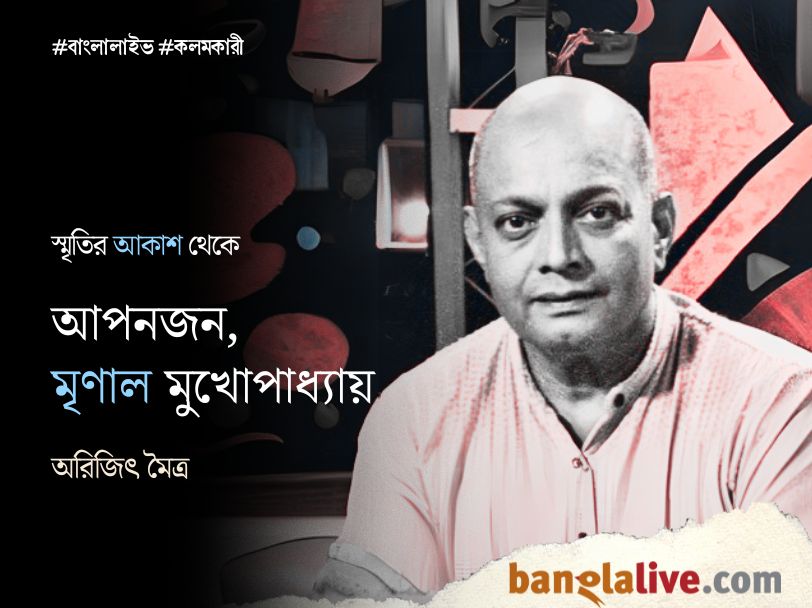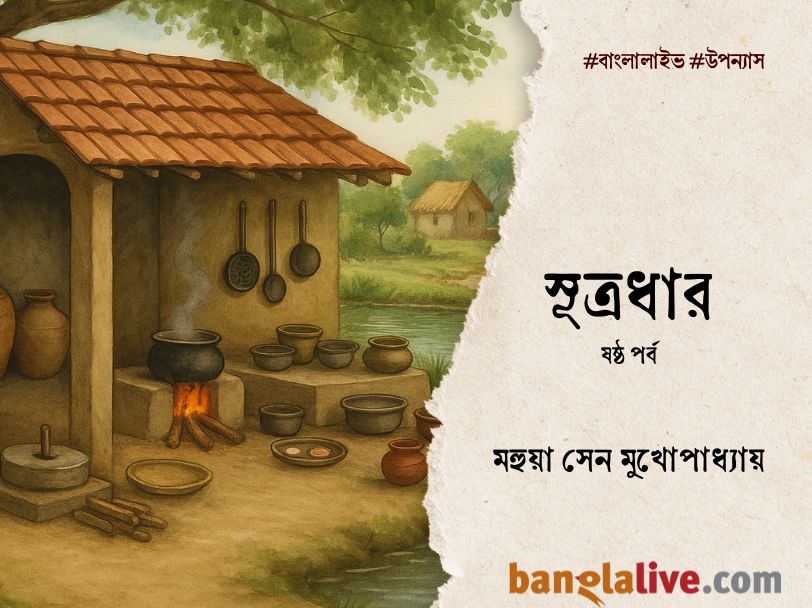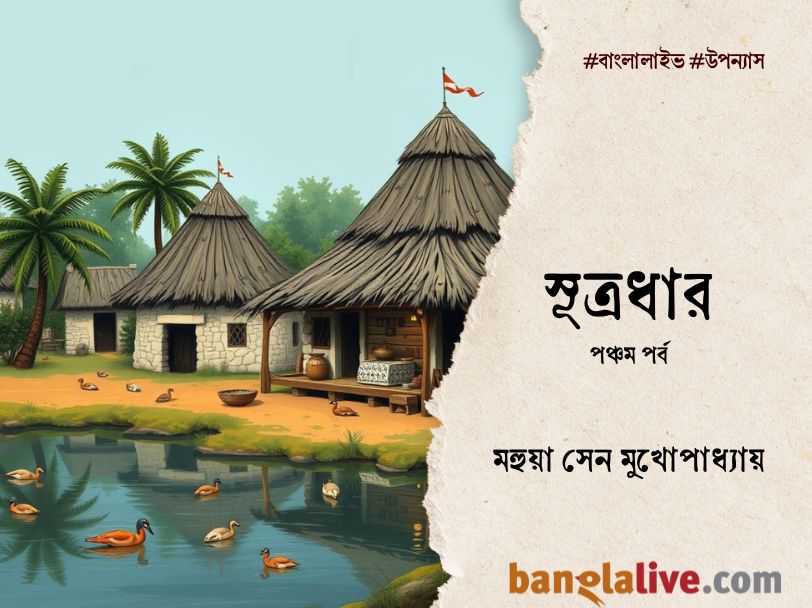খাদ্য গবেষক নীলাঞ্জন হাজরার ‘কাবাব কিসসা’ বইতে রাজস্থানের মেবারের “রামায়ণ পুথি”-র একটি অনবদ্য রঙিন ছবি রয়েছে ১৬৪০ সাধারণাব্দে আঁকা। সেখানে রামচন্দ্রের পারিবারিক ভোজনের দৃশ্য আমাদের অনেক কথা বলে। ছবিটিতে মন দিয়ে একজন শিক কাবাবের অনুরূপ কিছু বানাচ্ছেন।
শিশ একটি তুর্কি শব্দ, যার অর্থ ছুঁচলো মুখের দণ্ড। আবার সিখ তার সমার্থক ফারসি শব্দ। এসবের অর্থ হল, রামায়ণের আমলেও ভারতবর্ষে কাবাব বানানোর রেওয়াজ ছিল। নয়তো মেবারের চিত্রশিল্পী কেন এমন ছবি আঁকবেন?
রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডেই রয়েছে শিকার করে আনা হরিণের মাংস ঝলসে খাওয়ার কথা। তবে এর আগে, মানে বেদের যুগেও সে প্রমাণ মেলে। মহাভারতে ঋষি বৈশম্পায়ন রাজা দুষ্মন্তর শিকারাভিযানে ঝটিতি পশুর মাংস পুড়িয়ে ভক্ষণের বর্ণনা দিয়েছেন। হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য অনুদিত বাল্মীকি রামায়ণের সুন্দরবন কাণ্ডে সোনার লংকার বর্ণনায় রয়েছে এমন…
“ঐ পানগৃহে বিবিধরূপে আহার্য বস্তু প্রস্তুত; মৃগ, মহিষ ও বরাহ মাংস স্তূপাকারে সঞ্চিত আছে। প্রশস্ত স্বর্ণ পাত্রে অভুক্ত ময়ূর ও কুক্কুট মাংস, দধিলবণ সংস্কৃত বরাহ, বাধ্রীনস মাংস এবং শূল পক্ব মৃগমাংস নানারূপ কৃকল, ছাগ, অর্ধভুক্ত শশক এবং সুপক্ব এক শল্য মাংস প্রচুর পরিমাণে আহৃত আছে… পাত্রে সুরা পরিপূর্ণ আছে…” যার অর্থ দাঁড়ায় দই আর নুন সহযোগে ম্যারিনেট করা বিভিন্ন পশুর মাংস শূলপক্ব বা শিক কাবাব রীতিতে বানিয়ে খাওয়ার রেওয়াজ নতুন নয়।

কাবাব মূলত পারস্য এবং তুরস্কের মধ্যযুগীয় রান্নাঘরে তৈরি এক অভিনব মাংসের রেসিপি। এটিকে মধ্যপ্রাচ্যের প্রাগৈতিহাসিক মাংসের পদও বলা যেতে পারে। রামায়ণ মহাভারতেও খরগোশ, হরিণ, মহিষের মাংস খোলা আকাশের নিচে আগুন জ্বেলে শূল্যপক্বের পাশাপাশি বাঙালির প্রাচীন ইতিহাসের গোড়াতে মাছের পাশাপাশি ছিল মাংসের রমরমা। চর্যাপদেই ছিল, সে সময়কার অন্যতম আমিষ মৃগমাংসের কথা। “অপনা মাংসেঁ হরিণা বৈরী/খনহ ন ছাড়অ ভুসুক অহেরী”– ভুসুকুপাদ রচিত চর্যাপদের এই শ্লোকে হরিণের মাংসের কথা আছে, যার অর্থ হল, হরিণের মাংস তার জন্য শত্রু। অথচ ভুসুক ক্ষণিকের জন্য শিকার ছাড়বে না। কে জানে, উত্তরোত্তর হরিণবধের প্রবণতা থেকে মানুষকে নিরস্ত করানোর জন্যই বুঝি এমন লেখা হয়েছিল!
কবি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে মা অন্নপূর্ণার হেঁশেলে একজায়গায় শূলে গেঁথে যে ‘অন্যমাংস’ রাঁধার কথা আছে, তা যে কাবাব, বুঝতে বাকি থাকে না। আর এক জায়গায় দেবী অন্নপূর্ণা রাঁধেন “অন্নমাংস সিকভাজা কাবাব করিয়া” অর্থাৎ বাঙালির পোলাও-মাংস আর শিককাবাব সেই ভারতচন্দ্রের আমল থেকেই জনপ্রিয়।
ইবন বতুতার মতে, দিল্লি সুলতানতের সময় থেকেই (১২০৬-১৫২৬) রাজপ্রাসাদে কাবাব পরিবেশিত হত। এমনকি সাধারণ মানুষেও প্রাতঃরাশে রুটি বা পরোটার সঙ্গে এটি উপভোগ করত। সুশ্রুতসংহিতায় রাই সরষের গুঁড়ো ও সুগন্ধি মশলা দিয়ে মাখিয়ে উনুনে মাংস ঝলসানোর উল্লেখ আছে। বিশিষ্ট প্রত্নতত্ত্ববিদ বসন্ত শিন্দের গবেষণায় খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দে সিন্ধু সভ্যতায় তন্দুরির মতো মাংসের খাবারের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। সেই সূত্রেই বলা যায় আমাদের পাঞ্জাবের উনুনগুলিও হয়তো বা সিন্ধু সভ্যতার অনুরূপ, যার নাম তন্দুর! আর এই তন্দুরি মাংসও তবে আমাদের দেশি কাবাবের সমগোত্রীয়। নরেন্দ্রনাথ সেন তাঁর আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ বইয়ে বলেছেন, শূল্যমাংস অমৃততুল্য, রুচিজনক, অগ্নিবর্দ্ধক, লঘু, কফঘ্ন, বায়ুনাশক, বলকারক ও কিঞ্চিৎ পিত্তজনক।

আমাদের মনের মণিকোঠায় অবশ্য কাবাব বলতেই গাঁথা রয়েছে দিল্লির কাবাবওয়ালি গলি কিম্বা হায়দ্রাবাদের ইউসুফেন দরগা সংলগ্ন নামপল্লি অথবা লখনউয়ের চওক অঞ্চলে গলির মধ্যে একরত্তি দোকান টুন্ডে কাবাবি অথবা শ্রীনগরের হজরতবল মসজিদের পাশের পাড়ার কথা। মানে কাবাব যেন মুসলমানি খাদ্যসংস্কৃতির চূড়ান্ত প্রতীক। কিন্তু ওপরের মহাকব্যিক তথ্যগুলি এ ধারণা ভণ্ডুল করে দেয়।
তাহলে সখি, বলুন দেখি কাবাব কারে কয়? নীলাঞ্জন বাবু জানাচ্ছেন, এনসাইক্লোপিডিয়া অনুযায়ী “কাবাব” শব্দটি প্রথম যখন এল আধুনিক ভাষায়, তখন তা আরবিতে মোটেই ঝলসানো মাংস নয়। সেদ্ধ করা মাংসের মুইঠ্যা বা যাকে বলা হয় মিট বল। কাবাবের অনেক নাম। কেবাব, কেবাপ, ক্যাবব। এসব শব্দ এসেছে মধ্যপ্রচীয় আরমিয়হ্ ভাষা থেকে। সেই ভাষায় কাবাব হল মাংসের কিমা শিকে লাগিয়ে ঝলসানো।
তবে এই কাবাবের আবার রকমফের আছে। ইরানে বড় বড় ম্যারিনেটেড মাংসের টুকরো শিকে গেঁথে মধ্যে মধ্যে পেঁয়াজ, মাশরুম, টমেটোর টুকরো দিয়ে ঝলসানো কাবাবকে বলা হয় শাসলিক। আমেরিকায় আবার মশলা মাখানো মাংস আগুনে ঝলসে নেওয়াকে বলে বারবিকিউ। ক্রিস্টোফার কলম্বাসের কৃপায় সারা পৃথিবীতে এই বারবিকিউ ছড়িয়ে পড়েছিল। কলম্বাস উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যবর্তী একটি দ্বীপে প্রথম জাহাজ নোঙর করেন। এই দ্বীপের আদিম অধিবাসী টাইনোদের আগুনের শিখায় ঢিমে আঁচে মাংস রান্নার এক বিশেষ কৌশল রপ্ত করে স্প্যানিশরা। এরপর তারা আমেরিকার অন্যান্য অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করার সময় টাইনোদের সেই রান্নার কৌশল ছড়িয়ে দেয়। এটিই বারবিকিউয়ের জনপ্রিয়তার কারণ।

কলকাতায় কাবাবের আগমন মুসলিম শাসকদের হেঁশেল থেকে হলেও কালেকালে তা কলকাতার নিজস্ব রেসিপি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা এখন পথচলতি রেস্তোরাঁর কল্যাণে রেশমি কাবাব থেকে শিক কাবাব, পাহাড়ি কাবাব, কলমি কাবাব, সুতলি কাবাব, শাম্মি কাবাব, এসব নাম জেনে গেছি। শাম্মি নামটি এসেছে বিলাদ আল-শাম (সিরিয়া)-কে বোঝানো হয়। ‘শাম’ থেকে আগত বাবুর্চিরা মোঘল দরবারে সর্বপ্রথম এই কাবাব প্রস্তুত করেছিল। তাই তাদের সম্মানে এই কাবাবের নামকরণ হয় শাম্মি কাবাব।

লখনউয়ের ‘টুন্ডে কে কাবাব’ নিয়ে লিখতে বসে শতরূপা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, লখনউ ও হায়দ্রাবাদের মোগলাই রান্নার মূল পার্থক্যের কথা। লখনউ ঘরানা তুলনামূলকভাবে হালকা। অন্যদিকে হায়দ্রাবাদের রান্নায় তেল ও মশলার পরিমাণ অনেক বেশি। তবে উভয়েই সুস্বাদু। মশলা ব্যবহারের বৈচিত্র্যে আর পদ্ধতির রকমফেরে দিল্লির ‘মুর্গ অঙ্গারে’ই হোক কিম্বা হায়দ্রাবাদের ‘নেজা কাবাব’– মাংসই সেখানে মূল কথা। তবে নিরামিষাশীদের কথা ভেবে আজকাল দিল্লির দহি কাবাব, পনির টিক্কা, সিন্ধির হরিয়ালি কাবাব বা হরাভরা কাবাবও খুব চালু। তবে এসব কাবাবকে কয়েক গোল দিতে পারে মোগলাই শাম্মি কাবাব, গলৌটি কিম্বা বোটি কাবাব।
ছবি সৌজন্য: NDTVFood, americangarden.us, Tripadvisor, Freshhaka, Naira
*তথ্যঋণ: কাবাব কিসসা (ধানসিড়ি) / নীলাঞ্জন হাজরা
খাবাদের স্বাদকাহন – শুভশ্রী
রসায়নের ছাত্রী ইন্দিরা আদ্যোপান্ত হোমমেকার। তবে গত এক দশকেরও বেশি সময় যাবৎ সাহিত্যচর্চা করছেন নিয়মিত। প্রথম গল্প দেশ পত্রিকায় এবং প্রথম উপন্যাস সানন্দায় প্রকাশিত হয়। বেশ কিছু বইও প্রকাশিত হয়েছে ইতিমধ্যেই। সব নামীদামি পত্রিকা এবং ই-ম্যাগাজিনে নিয়মিত লেখেন ছোটগল্প, ভ্রমণকাহিনি, রম্যরচনা ও প্রবন্ধ।