২০২০ র জুন মাসের পয়লা তারিখে, আমার মার্কিনী অভিবাসী জীবন, ৪৬ বছরে পা দিল। জীবনের পর্বে পর্বে ভিন দেশকে মানিয়ে গুছিয়ে নেওয়ার অভিজ্ঞতায় গ্রহণ, বর্জন ও পরিবর্তনে বিদেশী প্রভাব কিছুটা তো পড়েই। তারই মধ্যে চিরন্তন সাবেকী রান্না ও খাদ্যাভ্যাস অটুট রাখা বেশ কঠিন। সব দেশী উপকরণ না পেলে, বিদেশী বিকল্পে কী করে একই স্বাদ আনা যায়, তা নিয়ে ঘরে ঘরে চলে নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা। অভিবাসী জীবনের স্মৃতিচারণায় এর মূল্য অপরিসীম। ৪৬ বছর অনেকটা সময়। অল্প পরিসরে সমস্ত অভিজ্ঞতা বলা কঠিন। দেখি কতটা বলতে পারি।
বিয়ের অনেক আগে, সেই কৈশোর থেকেই-রান্নার প্রতি আমার এক অদ্ভুত আকর্ষণ। আমার উচ্চমাধ্যমিকে গৃহবিজ্ঞান ও অর্থনীতি ছিল তাই প্রথমে, প্রয়োজনের খাতিরে ও পরে, নিজের উৎসাহেই রান্নাঘরে পদার্পণ। রান্না সংক্রান্ত কলাকৌশল খুব কঠিন, এমন কখনও মনে হয়নি। শুধু শিলের ওপর মশলা বাটা আর বঁটিতে তরকারি কোটার কাজ ছাড়া। রান্নার গন্ধ তা যেকোনও সাধারণ রান্নাই হোক বা বিভিন্ন উৎসবে বাড়িতে বানানো মিষ্টির গন্ধই হোক, দেশে থাকতেও আমাকে মোহিত করে দিত। এখনও করে। তাই যেকোনও নতুন পদ চাখার পর, প্রথমে তাতে কী কী মশলা আছে সেটা আন্দাজ করার একটা চেষ্টা চলে। তারপর শুরু হয় সেটা তৈরির প্রচেষ্টা।

দেশের নিরামিষ, আমিষ বহু খাদ্যের বিকল্প সন্ধানেও একটা মজা খুঁজে পাই। মাত্র কয়েক বছর আগেও এঁচোড়, মোচার বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করেছি আর্টিচোক এবং বিন-স্প্রাউট। অ্যাসপ্যারাগাস দিয়ে বানিয়েছি কচুর শাক। আমিষ এর মধ্যে ক্যাটফিস দিয়ে বানিয়েছি মায়ের কাছে শেখা আড়মাছের ভাঙ্গা শুকো। কিন্তু এর কোনওটাই সম্ভব ছিলনা্ ৭০-৮০ র দশকে। এখন এখানে প্রায় সব বাঙালি মশলাই পাওয়া পাওয়া যায়। কিন্তু সেই সময়ে, রান্না করে লোক খাইয়ে বেশ একটা অন্য আনন্দ ছিল কারণ বাঙালি ও আমেরিকান বন্ধুরা, বাড়ি থেকে এতদূরে থাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রীরা, সকলেই খুব খুশি হত সাবেকী রান্না খেয়ে। তাদের সেই উচ্ছ্বাস আর তৃপ্তি করে খাওয়া -আজও মনে গেঁথে আছে।
১৯৭৪-এর জুন থেকে ২০২০-এর জুন অবধি চারটে স্টেট এ থেকেছি। তার মধ্যে কলম্বাস ওহায়োতে প্রথম তিন মাস থাকার পরেই আমরা চলে যাই রাজধানী ওয়াশিংটনের গায়ে মেরিল্যান্ড স্টেট-এ। সেখানে দুই ছেলেমেয়ের জন্ম হয় ১৯৭৬ এবং ১৯৮০ তে। ১৯৮০ তেই, চার বছরের ছেলে ও তিন মাসের মেয়ে নিয়ে, চলে যাই নিউ ইয়র্ক স্টেট-এর রচেস্টারে। সেখান থেকে ১৯৮৪ সালে নিউজার্সি চলে আসা এবং থেকে যাওয়া। রচেস্টার এ থাকার সময়, সেখান থেকে বাফেলো আর নায়াগ্রা জলপ্রপাতের কাছে কানাডার বর্ডার পেরিয়ে টরন্টো যেতাম। সেখানে গিয়ে দিদির বাড়িতে উইক এন্ড কাটিয়ে, জেরার্ড স্ট্রিট থেকে প্রচুর মশলাপাতি, চাল ডাল কিনে নিয়ে আসতাম। জেরার্ড স্ট্রিট যা কিনা এখন লিটল ইন্ডিয়া নামে খ্যাত, ছিল ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে আসা প্রবাসিদের কাছে স্বর্গ।

শীতের জায়গা। বাচ্চারাও ছোট ছিল। বাড়িতে রকমারি পরীক্ষানিরীক্ষা মূলক রান্নাবান্নার করে, লোক খাইয়েই শীত কেটে যেত। নিউজার্সিতে এসেও প্রথম প্রথম জার্সি সিটি, নিউ ইয়র্ক এর জ্যাকসন হাইট বা চায়না টাউনে বাজার করার দিন ভোলার নয়। এসবের পেছনে ছিল একটাই উদ্দেশ্য — চিরন্তন রান্নার ধারাটাকে বজায় রাখা।
অনেক পরে, নব্বইএর দশকে আমাদের এখনকার বাসস্থান নিউজার্সিতেই, সাহেব ছাত্রছাত্রীদের জন্য নেওয়ার্ক মিউজিয়ামের চত্বরে বাঙালি রান্নার ক্লাস দিতে হয়েছিল। পাশাপাশি বাংলাদেশের কর্মজীবিদের বিখ্যাত জ্যাকসন হাইটস অঞ্চলে আমার বাংলা স্কুল ‘মৃত্তিকার’ (মৃত্তিকার বয়স এখন ৩২ বছর) ছাত্রছাত্রী ও বাবা মায়েদের নিয়ে ফিল্ড-ট্রিপ করিয়েছিলাম। সেই ট্রিপে বাঙালি মশলার দোকান যাওয়ার ঘটনা ছিল মনে রাখার মতো। হাট বাজার নামে এক বিখ্যাত বাংলাদেশী খাবারের দোকানে জমিয়ে খাওয়াদাওয়া করে, পান খেয়ে, মিষ্টি দই কিনে বাড়ি ফিরেছিলাম সেদিন।
আর একটা কথা না বললেই নয়। আমার মা আমাকে একটি শক্ত মলাটে বাঁধানো বই দিয়েছিলেন, এ দেশে সংসার পাতার সময় কাজে লাগবে বলে। তাতে সাবেকী বাঙালি রান্নার অসাধারণ সব রেসিপি আছে যা তখন অভিজ্ঞতার অভাবে রান্না করা খুব সহজ ছিলনা। কিন্তু পরে সেই বই এর রেসিপি দেখে করা রান্না খেয়ে লোকজনের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছিল। রান্নাগুলো কেন সহজ ছিলনা, একটু বলি। বইটির প্রচ্ছদে একটা রঙিন ছবি আছে – এক মহিলার ছবি, যিনি তরকারি কুটতে কুটতে দিশী উনুনে রান্না করছেন। ওপরে লেখা ‘রান্নার বই’। বইটা আগাগোড়াই কঠিন কঠিন সব ‘রন্ধন প্রণালী’ ও তার উপকরণ তালিকায় ভর্তি।

তার থেকেও কঠিন রন্ধন সামগ্রীর ‘মাপ’। এই বইয়ে দেওয়া নির্দেশাবলীতে, নুন চিনির ব্যবহারের মাপের জায়গায় লেখা আছে -’পরিমাণ মত’। মশলার মাপের জায়গায় লেখা আছে ‘সেইমত পরিমাণ’। জলের পরিমাণ বোঝাতে লেখা আছে ‘আন্দাজমত’! সুতরাং এই নির্দেশ তখন, সদ্য বিদেশে আসা আমার পক্ষে, কেন কঠিন ছিল আশা করি পাঠকদের বোঝাতা পারলাম!
মাপের ব্যাপারে সাংঘাতিক এই সমস্যায় সমাধান কীকরে করা যায় যখন ভাবছি, তখন আমার কর্তামশাই আমাকে একটি পাকিস্তানী এয়ার লাইন্স এর কুকবুক কিনে দিয়ে আমার মুশকিল আসান করলেন। সেখানে সমস্ত মাপ- চা-চামচ, টেবিল চামচ, কাপ ইত্যাদির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে। মশলা, চাল, আটা ময়দা, তরল উপকরণ- সব সেই মাপ অনুযায়ী করার নির্দেশ দেওয়া আছে। আর এখন তো আমরা এতেই অভ্যস্ত। ওই একই মাপের ব্যবহার বাড়িতে মিষ্টি বানানোর ক্ষেত্রেও অপরিহার্য। এখানকার বাঙালিদের মধ্যেও তখন রান্নার রেসিপি আদানপ্রদান চলতেই থাকত। এখানে এসে শিখেছি কীভাবে ছানার বদলে আমেরিকার রিকোটা চিজ ব্যবহার করে রসগোল্লা, সন্দেশ বানানো যায়। আজও সেই পদ্ধতি মেনে মিষ্টি তৈরি করা চলছে।

১৯৭০-১৯৮০-এর দশকে সেলিব্রিটি রাঁধুনীর অনলাইন শো কিংবা ইউটিউবে রান্না শেখার সুবিধে ছিলনা। ছিলনা গুগল-খোঁজ অথবা রেসিপি এক্সচেঞ্জ ক্লাব। রান্নার সৃজনশীলতার দেওয়া নেওয়ার সর্বাধিক প্রচলিত মাধ্যম ছিল নীল এয়ারোগ্রাম চিঠিপত্র যা আজ প্রায় অবলুপ্ত। আমার দিদির পাঠানো ধোঁকার ডালনা, মার পাঠানো ফুলকপির রোস্ট আর শ্বাশুড়িমায়ের এর ভাজা শুক্তোর রেসিপি আমার কাছে রত্নসম্ভার।
১৯৯০ থেকে ২০২০ র এই দীর্ঘ পর্বের লেখায় ,ইতি টানা সহজ নয়।
নতুন কারিগরী বিদ্যার জোয়ারে সাবেকী রান্নার হাল ধরার সময় এসেছে। ব্যস্ত মানুষের জীবনে সময় গিয়েছে কমে। গজিয়ে উঠেছে বাণিজ্যিক ফ্রোজেন খাবারের সমারোহ, যার বেশিরভাগই মাইক্রোওয়েভ এ গরম করে খেয়ে নেওয়া যায়। এখন এখানকার ভারতীয় দোকানে এঁচোড়, মোচা, কচু, পটল সবই পাওয়া যায়। এখন শুধু মনে পড়ে, মার দেওয়া সেই ‘রান্নার বই’ থেকে ‘নিরামিষ ডিমের ডালনা’ করে আমেরিকান বন্ধুদের খাইয়েছিলাম সেই সত্তরের দশকে। আজকের বাণিজ্যিক রান্নার প্রচারের সমারোহে কোন চ্যালেঞ্জ নেই। না সাবেকীয়ানায়, না তার বিকল্প রান্নার চেষ্টায়। কিন্তু স্মৃতি তাকে ধরে রাখবে আমৃত্যু অমলিন — এই আশায় ভর করে লেখা শেষ করলাম।।
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর করে বিবাহসূত্রে মার্কিনমুলুকে পাড়ি। ৪৬ বছরের প্রবাস জীবনে নানা ভূমিকায় দেখা গেছে ধৃতি বাগচিকে। কখনও তিনি 'মৃত্তিকা'র বাংলা শিক্ষার সঞ্চালক, কখনও বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের সক্রিয় সদস্য, কখনও শিল্পী। দীর্ঘদিন মার্কিন রিয়েল এসটেট শিল্পের সঙ্গেও যুক্ত থেকেছেন।






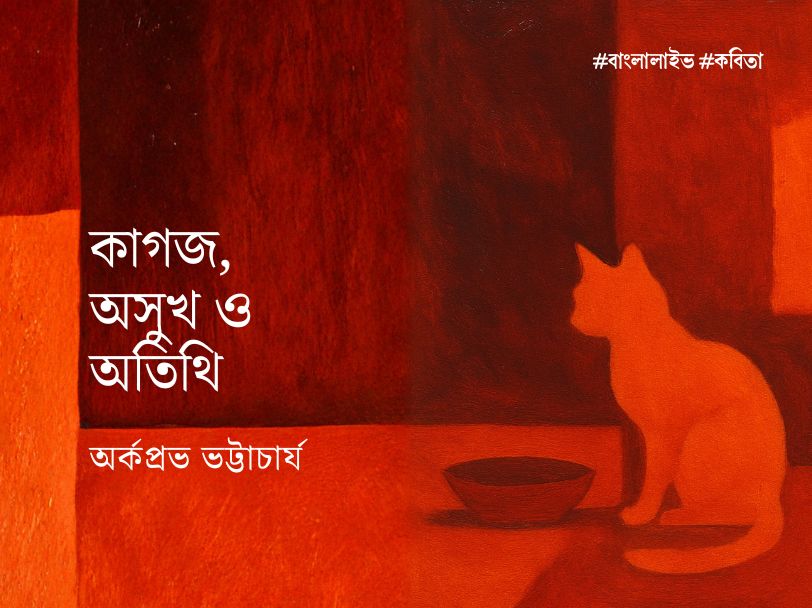








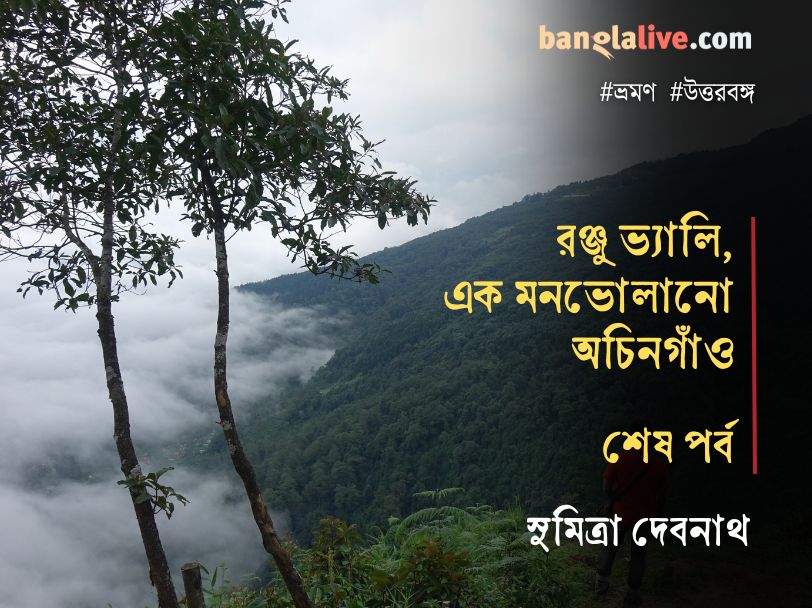







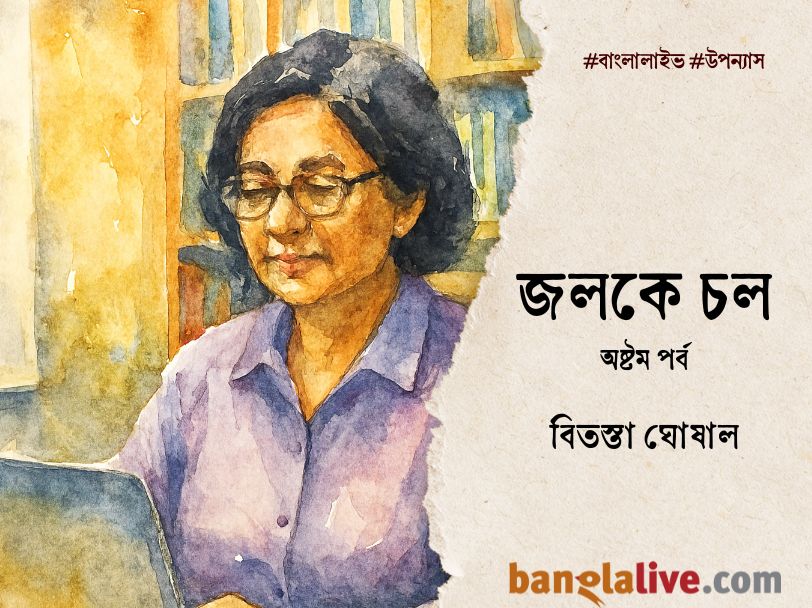
3 Responses
“রন্ধন একটি মূল্যবান শিল্প”– এই কথাটি এতদিন কেবলমাত্র শুনে এসেছি। আজ প্রত্যক্ষ করলাম। লেখনীগুণে রন্ধন শিল্পও সাহিত্য হয়ে উঠল। আসলে একজন মানুষ যখন আদ্যোপান্ত শিল্পী মনষ্ক হন, তখন তিনি যাই করেন সেটাই শিল্প হয়ে যায়। দিদির হাতে দীর্ঘদিন প্রচুর সাধারন উপাদানে, “রন্ধনগুণে” ভালো ভালো খাবার খাওয়ার অভিজ্ঞতা আমার আছে। কত সাধারণ খাদ্যবস্তুকেও ধৃতিদি মন দিয়ে রান্নার ফলে এক অসাধারণ টেস্টি খাবার বানাতে আমি দেখেছি। আর ভালো খাবার? যেমন ইলিশ, মাংস, মিষ্টি ইত্যাদি উঃ রান্নার সময় ফোন টেলিভিশন সমস্ত রকম কমিউনিকেশন বন্ধ রেখে এক মনে যে মানুষ রান্না করেন, সেই রান্না শিল্প পর্যায়ে যাবে না তো, কোন রান্না যাবে। অনায়াসে একা হাতে ৭৫ জনের রান্না করতে আমি দেখেছি। আমার স্ত্রী রূপা, দিদি খাবারের একনিষ্ঠ ভক্ত। রূপা নিজেই রান্না করে, কিন্তু খাবার সময় বার বার বলবে “দিদির মত হয়নি”। অ্যাসপারাগাস আমি প্রথম দিদির কাছেই খেয়েছি। আর যে তেলাপিয়া মাছ আমি সারা জীবনে কতবার খেয়েছি, দিদির হাতে তেলাপিয়া নতুন টেস্ট পেল।
বেশ ভালো রে। চাকা বোধ হয় নতুন নতুন করে আবিষ্কার করতে হয়। তোর মৈত্রেয়ীদিও রিকোতা চিজ দিয়ে রসগোল্লা বানাত। শ্যাড বা সিলভার ফিশের মাথা দিয়ে ছ্যাঁচড়া, যাতে ব্রোকোলিও দেওয়া যেতোটি উপাদেয় হত। বিদেশি রান্নাও নিশ্চয়ই কিছু করিস। চিজের মধ্যে অ্যাসপারাগাস দিয়ে একটা চমৎকার ব্যঞ্জন বানাত, আর বেগুন আর চিজের একটা ঝোল, সে এখনও মুখে লেগে আছে। ক্যাটফিশ ব্যাটারে ডুবিয়ে, বা স্মেল্টও, ভাজা খেয়েছি চমৎকার।
ধৃতি রন্ধন পটিয়সী, এ কথা বহুজন বিদিত l তার একটি খন্ডচিত্র পেলাম, এই লেখার মাধ্যমে l এবার একটি নিমন্ত্রণের অপেক্ষায় l