‘কমলকুমার নো’জ় অল দ্য আর্টস’ – বলেছিলেন সত্যজিৎ রায়। বাস্তবিকই, সাহিত্য হোক বা নাটক, সিনেমা হোক বা ভাস্কর্য, কমলকুমারের পরীক্ষানিরীক্ষার শিল্প ছিল সর্বব্যপী, সর্বগ্রাসী। আর এই সমস্তকিছুর পরেও কোথাও যেন থেকে যেতেন ধরাছোঁয়ার বাইরে এক নির্লিপ্ত সন্ন্যাসীর মতো। শাণিত ব্যঙ্গের ফলা চকচক করে উঠত মাঝে মাঝেই। উইট আর হিউমরের সূক্ষ্ম মাদারি কা খেলের মধ্যে কষ্টসাধ্য ব্যালেন্স করতে হত না। আবার তিনিই এমন এক স্বতন্ত্র গদ্যশৈলী সৃষ্টি করতেন অনায়াসে, যাকে দুরূহ, দুষ্পাঠ্য, দুর্বোধ্য আখ্যা দিয়ে কেঁদে বাঁচত না তদানীন্তন মেনস্ট্রিম লেখক-পাঠক-বোদ্ধার দল। নইলে…
“আলো ক্রমে আসিতেছে। এ নভোমন্ডল মুক্তোফলের ছায়াবৎ হিম নীলাভ। আর অল্পকাল গত হইলে রক্তিমতা প্রভাব বিস্তার করিবে, পুনর্ব্বার আমরা, প্রাকৃতজনেরা, পুষ্পের উষ্ণতা চিহ্নিত হইব। ক্রমে আলো আসিতেছে।”
… এমন একটি বাক্য দিয়ে উপন্যাস শুরু করবার কথা কে কবে ভাবতে পেরেছিল? আলো আসবে নয়, আলো আসছে নয়, আলো এসে গিয়েছে তো নয়ই। অন্ধকারও কিন্তু নয়। ‘অন্ধকার ক্রমে কাটিতেছে’- তা-ও নয়। আলো ক্রমে আসিতেছে। কমলকুমারকে পড়তে গেলে মনে হয় এই অমোঘ বাক্যবন্ধটিই যথেষ্ট। আর কী বলা যায় তাঁর লেখা নিয়ে?
আসলে কমলকুমারের বেড়ে ওঠার মধ্যেই ছিল সেই স্বাধীন শিল্পের অঙ্কুর। স্কুলের শিক্ষা তাঁর পোষায়নি। ভাই, (পরবর্তীতে প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী) নীরদ মজুমদারের সঙ্গে একজোটে স্কুল পালাতেন। বাংলা মিডিয়াম স্কুল, মিশনারি স্কুল কোথাও মন বসে না। ভবানীপুরে সংস্কৃতের টোলে ভর্তি হলেন, বিরাট এক চৈতন নিয়ে বাড়ি ফিরলেন দুজনে— বোন (আর এক বিখ্যাত শিল্পী) শানু লাহিড়ী তাঁর ‘স্মৃতির কোলাজ’ বইতে লিখেছেন এ কথা। কখনও সেতার শিখছেন, কখনও সংস্কৃত লিখছেন, কখনও ফরাসিতে নিমগ্ন, কখনও কাঠখোদাই করে ছবি তৈরি করছেন। সত্যি কথা বলতে কী, ফরাসি ভাষায় কমলকুমারের তুল্য বৈদগ্ধ্য সেকালে কেন, এ কালেও হয়তো দুর্লভ। বিশ্ববিশ্রুত ফরাসি লেখক নাতালি সারোৎ-এর সঙ্গে গড়গড়িয়ে ফরাসিতে ঘরোয়া আড্ডা দেওয়ার সে কাহিনি অনেকেই শুনেছেন, পড়েছেন।
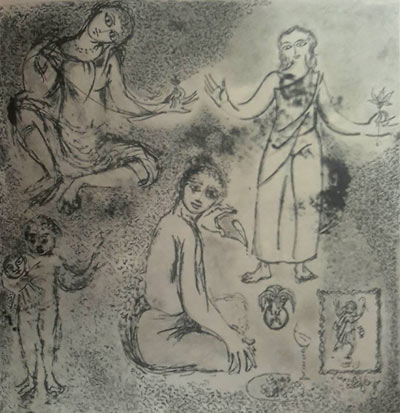
প্রশান্ত মাজী কমলকুমার মজমদারের শতবর্ষে তাঁকে নিয়ে লিখেছেন এক দীর্ঘ গবেষণাগ্রন্থ। নাম ‘কমলকুমার।’ সেখানেই পাই –
‘…আড্ডায় তিনিই হয়ে উঠতেন কথকঠাকুর। সকলকে সম্মোহিত করতে পারতেন বিচিত্র সব বিষয়ে কথা বলে – সুন্দরবনের ইটিন্ডা ঘাটের তৈরি মাটির পাত্র তৈরির প্রণালি বিষয়েই হোক বা সাহেবদের কাছে কলার মোচা কী করে কাটতে হয় তার বর্ণনা করেই হোক, অথরিটি নিয়ে কথা বলতেন প্রবল ঝাঁঝে – ফলে তাঁর সঙ্গে তর্ক করবে কে? দ্য রিভার ছবির শুটিং কলকাতায় করতে এসে রেনোয়াঁ নাকি মুগ্ধ হয়েছিলেন কমলকুমারের সান্নিধ্যে। বলেছিলেন ফিরে যাওয়ার সময় – কমলকুমারের মতো ব্যক্তিত্ব বঙ্গভূমে তিনি আর দ্বিতীয়জনকে পাননি। কমলকুমারের স্মৃতি তাঁর জীবনেও স্মৃতি হয়ে থাকবে, এরকমও জানিয়েছিলেন।’
কমলকুমার মজুমদার ছিলেন এক স্বয়ংসম্পূর্ণ শিল্পী। বাঙালি ভক্তকূল যথাবিহিতভাবে তাঁর খামখেয়ালি, মদ্যপ, মুখখারাপ, বাউণ্ডুলে স্বরূপের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে তাতে আবেগের জবাফুল চড়িয়ে বছরের পর বছর অতিপাত করছে। অথচ ‘অন্তর্জলী যাত্রা’ ছাড়া তাঁর সাহিত্যকীর্তির সঙ্গে কতটুকু পরিচয় আমাদের? কতটুকু সখ্য? তাঁর প্রথম প্রকাশিত ছোটগল্প ‘লালজুতো’র কথাই ধরা যাক। আটপৌরে দাম্পত্যপ্রেমের আটপৌরেপনা শেষ লাইন পর্যন্ত ধরে রেখেও এক আশ্চর্য রূপকল্পময় মায়াবাস্তবের অবতারণা, এ গল্পের জাত চেনায়। কিংবা ধরা যাক ‘মতিলাল পাদরী’র কথা।
ষাটের দশকে এক প্রত্যন্ত গ্রামের নিচু জাতের বাসিন্দাদের মধ্যে কিছু খ্রিস্টানও ছিল। আর ছিল এক গির্জা আর তার ধর্মপ্রাণ বাঙালি পাদরী, যে সাঁওতাল রমণীর প্রসব করা পুত্রকে যিশু বলে মেনে নিতে চেয়েও বিশ্বাসের সারল্যে ধাক্কা খায়, সাঁওতাল মেয়ে ভামরের অকপট ‘প্রমিসক্যুইটি’ মতিলালকে ফাঁপরে ফেলে দেয়। অথচ শিশুর ‘বা-ও-বা’ ডাক শুনে সে কেঁপে ওঠে বারবার। ধর্মপ্রাণ মতিলাল শিশুর কাছে বলে ফেলে ‘আমি সত্যি ক্রিশ্চান নাই গো বাপ।’ আর হয়ে ওঠে মানুষপ্রাণ মতিলাল। রক্ত মাংসে গড়া, অপত্যস্নেহে জরজর, প্রাণময়তার স্পর্শে মুগ্ধ মতিলাল।

‘নিম অন্নপূর্ণা’, ‘তাহাদের কথা’, ‘প্রিনসেস’, ‘মল্লিকা বাহার’ এমন অনেক গল্পের কথাই বলা যায় একের পর এক। বাংলা সাহিত্যের গবেষক, অধ্যাপকেরা আরও বিশদে লিখে গিয়েছেন তাঁর উপন্যাসগুলির কথাও। ‘গোলাপ সুন্দরী’ বা ‘সুহাসিনীর পমেটম’ বিশ্বসাহিত্যে বিশিষ্টতার দাবি রাখে, এ কথা বুদ্ধিজীব বাঙালির অজানা নয়। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের মতো কেউ কেউ পারতেন কমলকুমারের ভাষার ব্যবচ্ছেদ ভাষা দিয়ে করতে। করেওছিলেন ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে। লিখেছিলেন –
‘আসলে চিন্তা করে আমাদের সমস্ত শরীর, আমাদের রক্ত আমাদের জন্য চিন্তা করে, আমার পেট, আমার কিডনি, আমার ফুসফুস ও হার্ট, আমার হাড়গুলি ও তাদের অভ্যন্তরস্থ মজ্জাও আমার জন্য চিন্তিত আমি টের পাই – পা থেকে মাথা পর্যন্ত আমার শরীর, এই আমার সমগ্র জীবন, আমার শরীরময় সমস্ত জীবন আমার জন্যে চিন্তা করে। এবং আমরা এমন একটা ভাষা চাই, এমন একটা ভাষা আছে, আমরা টের পাই, যা আমাদের মধ্যে আমাদের ঐরূপ, শরীরময়, জীবনের জন্যে চিন্তা করে। সম্ভবত এটাকে ভাষা বলা যাবে না, বোধকরি এটা অভাষা। যে ভাষায় আমরা নাকি চিন্তা করি তা দিয়ে, নতুন ও পুরাতন রীতি, প্রচলিত বা অপ্রচলিত ছাঁচ এ-সব দিয়ে তো চুলও ছেঁড়া গেল না, যে-জন্যে, আজ, অবশেষে খোঁজ পড়েছে ঐ অভাষার, বিশ্বব্যাপী যখন এই শেষ চেষ্টা চলছে, তখন কমলবাবু মাথার ভেতর থেকে টেনে ওড়াতে চাইছেন ভাষার পতাকা, ভাষা দিয়ে কিছু জানাতে চাইছেন, ভাষা দিয়ে চাইছেন চিন্তা করতে।’
সাধারণ পাঠক, অবোধ পাঠক, নিমগ্ন পাঠক হিসেবে তাই বলতে ইচ্ছে যায়, দুর্বোধ্যতা, যতিহীনতার আড়ালে ভাষার এক ছন্দোময় লালিত্যের চর্চা কমলকুমার করে গিয়েছেন আমৃত্যু। তাঁর নিজেরই কথায়, ‘তীর সম্মুখ গতি যাইবার নিমিত্তে পিছু হটে, সর্পও দংশন করিবার পূর্বে আপনাকে পিছন পানে টানিয়া লয়।’ অর্থাৎ যে দুর্বোধ্যতাকে অন্তরায় হিসেবে দেখিয়ে কমলকুমারকে মগডালে তুলে রাখল বাঙালি, তাকে ক্লাসিকের সহজ আসনে বসাল না, আসলে সেই দুর্বোধ্যতার পরিসর পেরিয়ে কমলকুমারের ভাষা, আঙ্গিক এবং বিকল্প ন্যারেটিভ বাংলা সাহিত্যকে এগিয়ে দিয়ে গেল অনেকটা পথ।
রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যের অঙ্গনে যেসব লেখকদের নিয়ে বাঙালি মাথায় তুলে নাচে, তাদের পাশ কাটিয়ে নীরবে একাকী গঙ্গাতীরে অপেক্ষমান থাকলেন কমলকুমার মজমদার, আধুনিকতার ডিঙিনৌকো কবে আসবে, সে আশার অনিঃশেষ অন্তর্জলী যাত্রায়। আর বাঙালির পাতে পড়ে রইল একফালি কোটেশন, যা দিয়ে সে আজীবন কমলকুমারকে সরলরৈখিক সাহিত্যযাপনের কোণটিতে ফ্রেমে বাঁধিয়ে রেখে দেবে। বলবে, ‘…কোথাও এখনও মায়া রহিয়া গেল।’
তথ্যসূত্র:
কমলকুমার মজুমদার: অন্তর্জলী যাত্রা, ছোটগল্প সমগ্র, গোলাপ সুন্দরী, সুহাসিনীর পমেটম
প্রশান্ত মাজি: কমলকুমার
প্রশান্ত মাজী: ক্রমে আলো আসিতেছে (প্রবন্ধ; কালি ও কলম)
শুদ্ধসত্ত্ব ঘোষ: করবী তরুতে সেই আকাঙ্খিত গোলাপ ফোটেনি (প্রবন্ধ; দেশকাল)
মানস মাইতি: প্রথাভাঙার প্রতিক্রিয়াশীল স্রষ্টা কমলকুমার (প্রবন্ধ; স্রোত নববর্ষ সংখ্যা)
সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়: সুহাসিনীর পমেটম, ভাষা ও অমরত্ব (পুনঃপ্রকাশ: ৯’য়াদশক)
*ছবি সৌজন্য: Prothomalo, Goodreads, Aparjan
লিখতে শিখেই লুক থ্রু! লিখতে লিখতেই বড় হওয়া। লিখতে লিখতেই বুড়ো। গান ভালবেসে গান আর ত্বকের যত্ন মোটে নিতে পারেন না। আলুভাতে আর ডেভিলড ক্র্যাব বাঁচার রসদ। বাংলা বই, বাংলা গান আর মিঠাপাত্তি পান ছাড়া জীবন আলুনিসম বোধ হয়। ঝর্ণাকলম, ফ্রিজ ম্যাগনেট আর বেডস্যুইচ – এ তিনের লোভ ভয়ঙ্কর!!






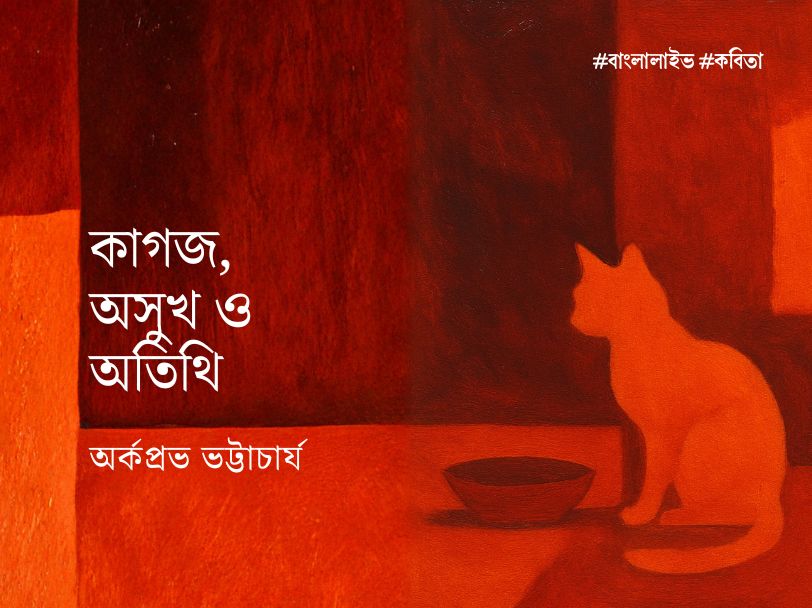
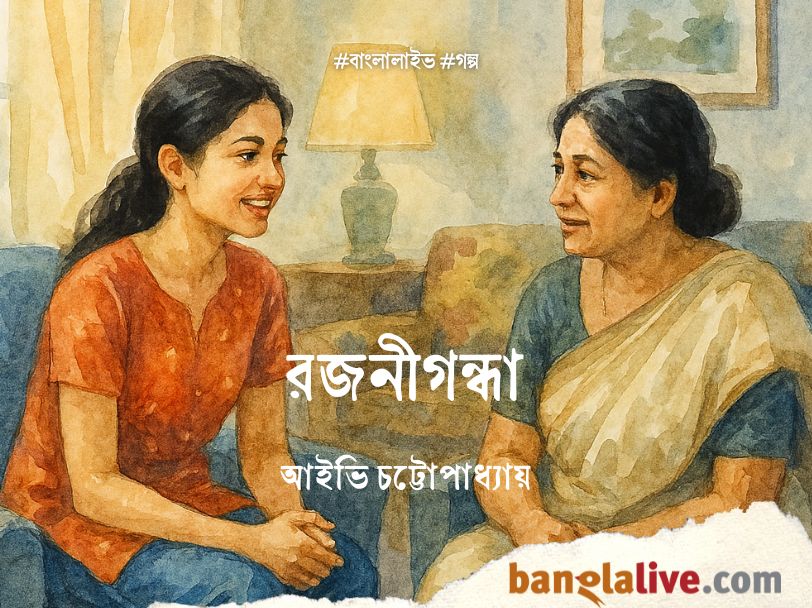
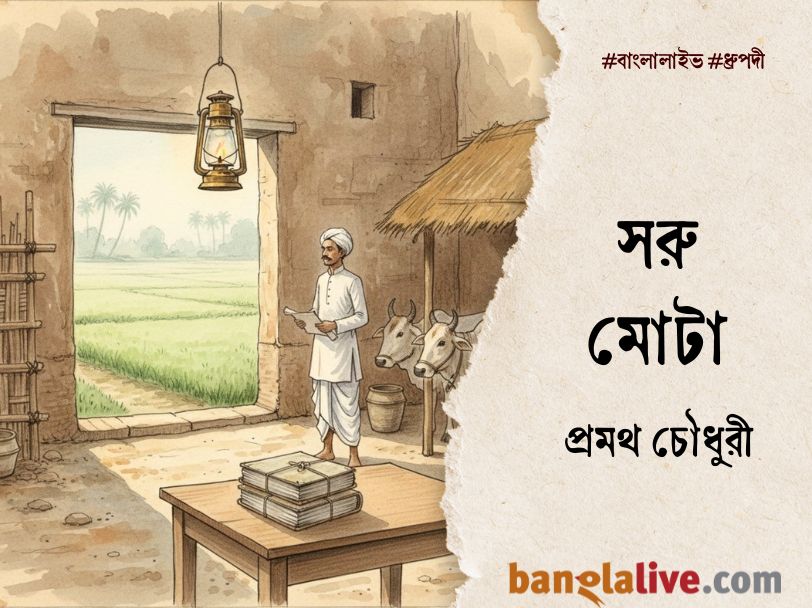








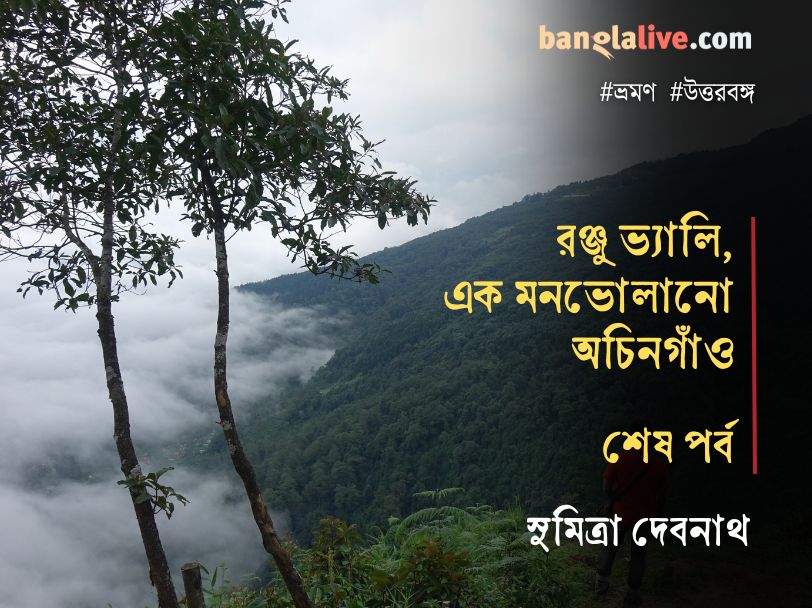


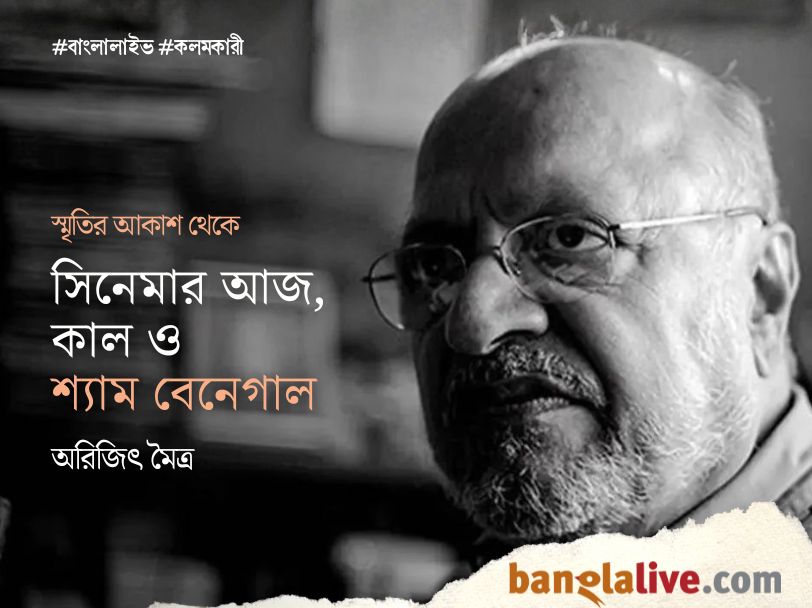




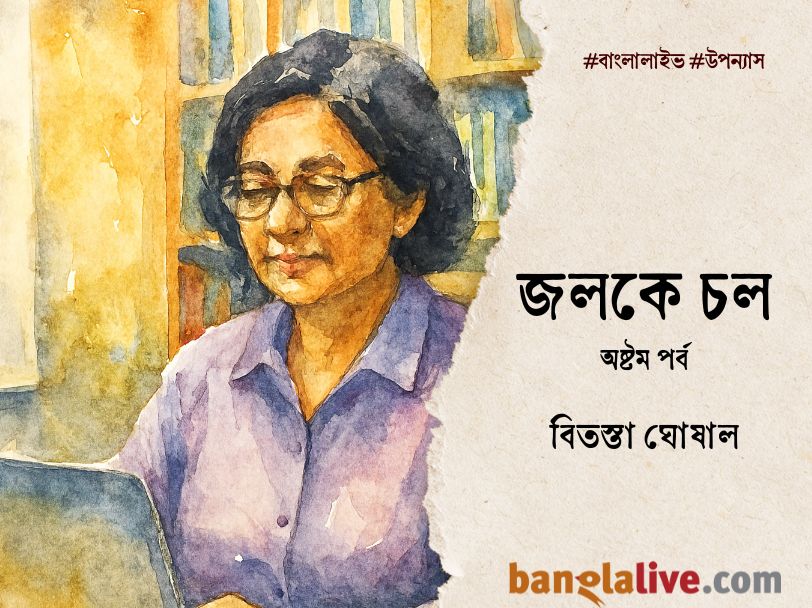
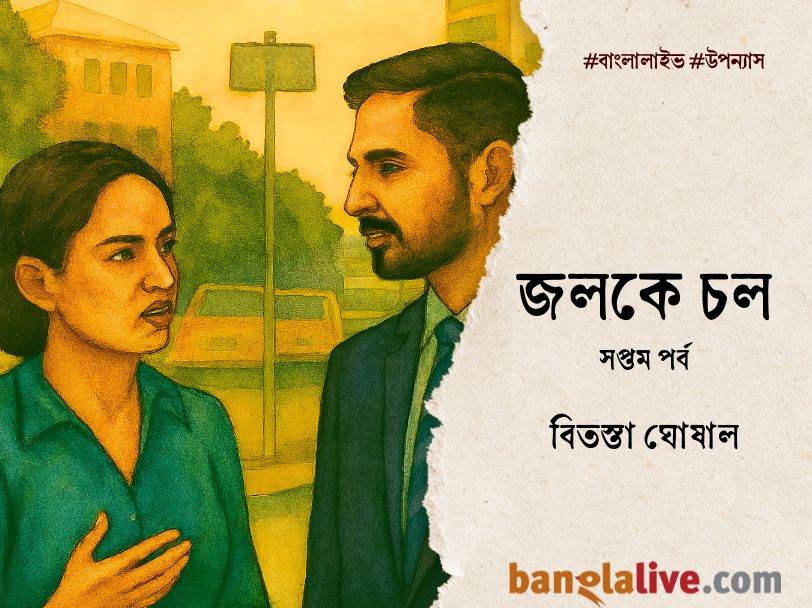
2 Responses
অল্পকথায় কমলকুমারকে সঠিকভাবে ধরার চেষ্টা। লেখিকা নিজেও সম্ভবতঃ জানেন যে এই পরিসরে কমলকুমারকে, বিশেষতঃ তাঁর বৈদগ্ধ, ব্যাক্তিত্ব,ভাষা ও বিষয়ের বিচিত্র সম্ভারকে বিশ্লেষণ করা যায়না।তবু তিনি সব দিক সুন্দরভাবে ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছেন। ধন্যবাদার্হ তিনি।
‘..কোথাও এখনও মায়া রহিয়া গেল।’
বিশদ বিস্তৃত প্রবন্ধ না হয়েও এই লেখা কমলকুমারের বৈদগ্ধ ও তাঁর রচনার বিস্তার পাঠক মনে প্রভাব ফেলবে।