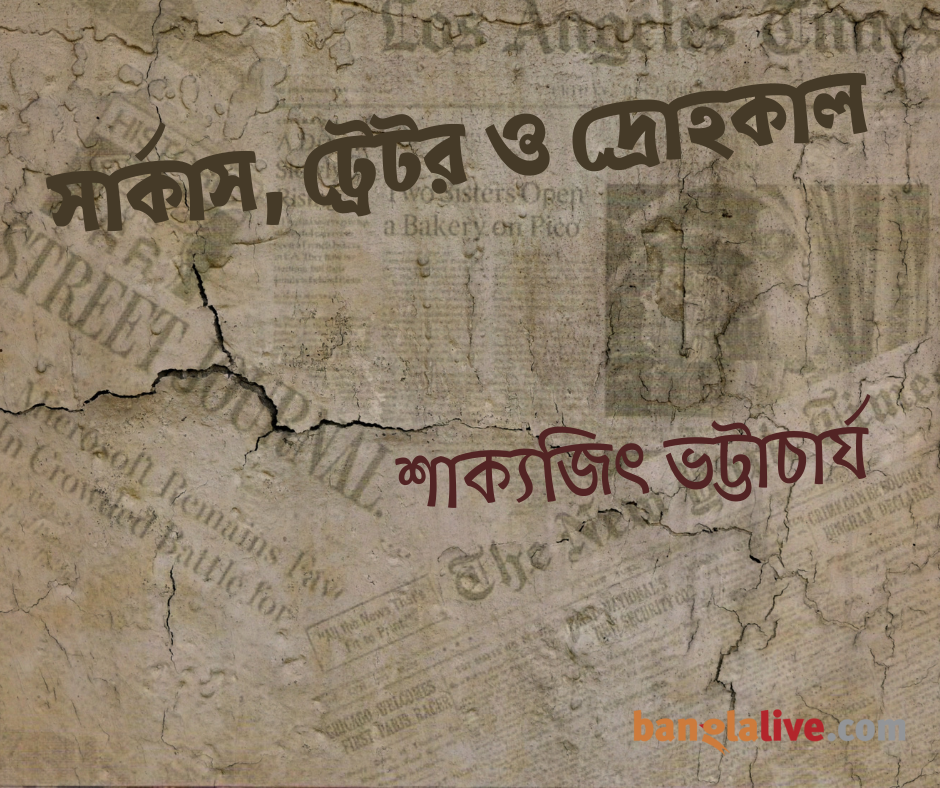আগের পর্ব পড়তে: [১] [২] [৩] [৪] [৫] [৬] [৭] [৮] [৯]
নষ্টপ্রতিমার আঘ্রাণ
‘পাখি জানে, আমার পুকুর নেই, রচনা-প্রতাপ নেই কোনও
সে শুধুই উড়ে যায় শুভেচ্ছা-সফরে, যায় বঙ্গদরশনে
আজ থেকে আর লিখবো না আমি। শৈবালিনী গেলে যাক
খ্যাতিতে মুদ্রণে।’
–সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়
দুর্গাপুজোর কিছুদিন আগে এক সকালবেলা ফেসবুকের পাতা ওলটাতে গিয়ে আমি আতঙ্কগ্রস্ত হই। আমার চোখে ধাক্কা মারে একের পর এক শারদ সংখ্যার ঘোষণা, এক একজনের ঝুলিতে আড়াইশ-র ওপর লেখক কবি। আমি দেখি, অনেক তথাকথিত লিটল ম্যাগাজিন ঝাঁ চকচকে কর্পোরেটধন্য পত্রিকা বানিয়েছে। তাদের ঝুলিতে সেইসব সাহিত্যিকেরা, যাঁরা সারাজীবনে লিটল ম্যাগাজিনে লেখেননি। আবার অনেক সাহিত্যিক যাঁরা এক সময়ে লেখালেখিকে একটা সৃষ্টিশীল ও রাজনৈতিক টাস্ক হিসেবে দেখেছেন, তাঁদের দেখি কুড়ি বাইশ জায়গায় গল্প উপন্যাস কবিতা লিখতে, তাদের মধ্যে চরম বামপন্থী থেকে চরম দক্ষিণপন্থী কাগজ সবই পড়ে। আমি দেখি, তাঁরা প্রশংসায় ভরিয়ে দিচ্ছেন সেইসব কাগজকে যেখানে তাঁদের লেখা বেরিয়েছে, এবং নীরব অন্যগুলোর সম্পর্কে। বাণিজ্যিক বিগ হাউসের শারদ সংখ্যাতে লেখা বেরলে আলাদাভাবে তাঁরা সেগুলোর বিজ্ঞাপন করছেন। বহু নতুন ও পুরনো লেখক যাঁরা মূলত লিটল ম্যাগাজিনেই লিখেছেন সারাজীবন, তাঁদের লোভ চকচকে মুখমণ্ডল দেখে আমি আতঙ্কে ভুগি। কিছুদিন আগে এই সিরিজেরই একটা লেখায় ফেসবুক এসে ক্ষমতার বৃত্ত ভেঙে দিয়েছে বলে যে ঘোষণা করেছিলাম, তার বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে মনে করি কলমের প্রায়শ্চিত্ত করার সময় এসেছে।
আমি ব্যক্তিগতভাবে অবশ্যই বিশ্বাস করি না যে অবস্কিওরিটি একজন লেখকের সাধনার মূলমন্ত্র হওয়া উচিত। লেখার পর তা যদি কানেক্ট করতে না চায় তাহলে ছাপাবার দরকার থাকে না, লিখে কুলুঙ্গিতে তুলে রাখলেই হয়। অখ্যাতি ও হা হা অন্ধকারের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে রাজপুত্রের তরবারি, এমন রোমান্টিকতাতেও সহমত পোষণ করি না। কিন্তু তারপরেও দুটো কথা থেকে যায়। বাণিজ্যিক কাগজ তাদের নিয়মেই পুজোসংখ্যা, ঈদসংখ্যা, দোলসংখ্যা, গণেশপুজো সংখ্যার জন্য ফরমায়েশি লেখা উৎপন্ন করবে—এই স্বাভাবিকতাকে আমি প্রশ্ন করছি না। এমনকি বাণিজ্যিক কাগজে লিখলেই লেখকের জাত চলে যাবে তাতেও বিশ্বাসী নই। কিন্তু ক্রমে ক্রমে একটা ভাষার সবথেকে সাহসী ও স্পর্ধার জায়গা ছিল যে লিটল ম্যাগাজিনগুলো সেগুলোও যদি একই রাস্তা অনুসরণ করে, সারাজীবন প্যারালাল তকমা বয়ে যাওয়ার দুঃসাহস নিয়ে লিখতে এসে একজন লেখক যদি বড় বাড়ির ডাক পেয়ে আহ্লাদিত হয়ে ফেসবুকে সে কথা সাতমুখে প্রচার করেন অথবা ক্যাম্পেইন করেন সেই সব পত্রিকাগুলোর যেখানে তাঁর লেখা বেরিয়েছে, তাহলে বুঝতে হবে যে সেই লেখক আসলেই মনে মনে কমার্শিয়াল হতে চেয়েছেন সারাজীবন, এবং স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোটা তাঁর হয় ছল অথবা সুযোগ না পাবার জন্য একপ্রকার সাময়িক আপোষ ছিল।

পৃথিবীর আর কোনও দেশের লেখকের কথা আমি জানি না যাকে বছরে চারটে কি পাঁচটা উপন্যাস লিখতে হয়, নিয়ম করে বছরের একটা কি দুটো বিশেষ সময়ে লিখতে হয় গুচ্ছখানেক কবিতা। এখানে হয়। কারণ এখানে প্রকাশনা ব্যবসা শুধু বৃহৎ সংবাদপত্রই চালায় না, চালায় লিটল ম্যাগাজিনের মুখোশ পরে ছোট ছোট অনেক ক্ষমতার কেন্দ্রও, যোগ্যতার অভাবেই একমাত্র যারা লিটল। আমি রাজনীতির প্রত্যাশা করি না, কারণ ভিন্নধারার লেখালেখি যে একটা রাজনৈতিক প্রক্রিয়া সে সত্য বহুদিন আমরা ভুলেছি। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে কীভাবে একজন কমিটেড লেখককে হত্যা করা হচ্ছে সেটাকে যদি চিহ্নিত না করা যায়, তাহলে অন্যধারার লেখালেখির পরিণতি সেটাই হতে পারে, পঞ্চাশের দশক থেকে যা হয়ে এসেছে। কেরিয়ারের শুরুতে প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে গা গরম ভাষণ শুনিয়ে তারপর যেই বিগ হাউসে লেখার সুযোগ মিলবে, মাথা নীচু করে সেই কনভেনশনের খোঁয়াড়ে ঢুকে পড়া। ব্যাপারটা এমন নয় যে আমি এগুলো প্রথম বলছি। আমার আগেও অনেকে বলছেন, পরেও বলবেন। কিন্তু কয়েক দশক ধরে বৃহৎ পুঁজি এবং লগ্নিশাসিত যে সাহিত্যবাজার এখানে তৈরি হয়েছে, লিটল ম্যাগাজিনগুলোও তার বাইরে থাকছে না। সেখানে লেখালেখি আর বাণিজ্যকে তফাত করা যাচ্ছে না এই মুহূর্তে। এটুকুর বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্ন ক্রোধ, চোয়ালচাপা রাগী প্রবন্ধ এবং আবারও লিটল ম্যাগাজিন গোষ্ঠী তৈরি হওয়া বাদে আর কিছুই হয়নি, হয়নি কোনও সম্মিলিত প্রতিরোধ। সেই গোষ্ঠীগুলোও দিনে দিনে আরেকটা বিগ হাউসই হচ্ছে। তাই আমাদের সত্যভাষণে নিজেদের ইগো সন্তুষ্ট হওয়া বাদে আর কিছু হচ্ছে না।
আর তার ফলে মূলত ভুগছে ভাষা। বহুদিন হল আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক লেখালেখির ভাষা সাংবাদিকতার ভূষণ পরিধান করেছিল। কিন্তু তাদের বাইরে একটা বিশাল স্রোত ছিল, যেখানে ছিল সাহসী পরীক্ষার উন্মুক্ত অঞ্চল। আজকাল লিটল ম্যাগাজিন আর সংবাদপত্রশাসিত সাহিত্যের মধ্যে আলাদা করা যাচ্ছে না, সবার ভাষাই এক। সেই গোয়ালঘর, যার ভেতর প্যারালাল ও কমার্শিয়াল একই জাবনা থেকে জল খায়, সেখান থেকে যে বস্তুগুলো বেরচ্ছে তাদের অভিধা পরকীয়া প্রেম, নিষিদ্ধ যৌনতা, মধ্যবিত্তর পারিবারিক সংকট, তন্ত্র, হরর এবং গোয়েন্দা ক্রাইমের জঞ্জাল। এক মেদুর গোধূলি এসে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে মুড়ি ও মিছরির পৃথক বস্তাদের। ভাষাহীনতায় লীন হয়ে যাচ্ছে আমাদের সাহিত্যজগৎ, যেখানে একজনের লেখা থেকে অন্যজনেরটা আলাদা করা যাচ্ছে না। আর গোটাটাই করা হচ্ছে সাহিত্যপ্রসবের নামে, কিন্তু পেছনে ক্রিয়াশীল থাকছে অঙ্ক। শুধুই আর্থিক হিসেবের অঙ্ক নয়। খ্যাতি, পুরস্কার, গ্রান্ট, পাঠক সমাজে রেলেভান্ট থাকার বাসনা, সারাজীবন নির্জনে লেখালেখির পর প্রৌঢ়ত্বে এসে ‘দাম পাহিলাম না’ ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়া ইত্যাদি নানাবিধ সমীকরণ।
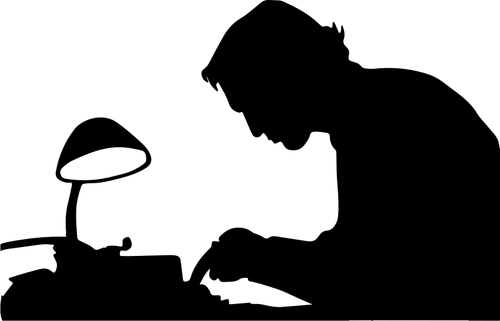
আমি কিন্তু অকবি বা অলেখকের কথা বলছি না। সেরকম সব যুগেই লাখে লাখে ছিল, এখনও আছে। তাঁরা বরাবর লিখে এসেছেন, সেরকম পত্রিকাও অনেক আছে যেখানে তাঁদের লেখা ছাপানো হয়েছে এবং হয়। সুবিধেটা হল তাঁদের চিহ্নিত করা যায়। আমি এমনকি মূলধারার বাণিজ্যিক লেখকদের কথাও বলছি না, কারণ তাঁরা আর কিছু না হোক একটা গোষ্ঠীর পাঠককে বই পড়িয়ে এসেছেন যুগের পর যুগ, তাঁরা বরং প্রণম্য। আমি বলছি প্রতিষ্ঠানবিরোধীতার মুখোশধারীদের কথা, ছদ্ম-নিরীক্ষাপ্রবণদের কথা, যাঁদের চিহ্নিত করা কঠিন বলেই বেশি বিপজ্জনক। আমাদের ভাষাপ্রচেষ্টাকে হত্যা করার পেছনে তাঁদের ভূমিকা কম নয়। তাঁদের উপস্থিতি সমান্তরাল ও মূলধারা দুয়েতেই সমান সক্রিয়, এবং তাতে কারোও ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না, কারণ তাঁদের নির্বিষ ভাষার আপাতচমক পঞ্চাশ বছর আগেই নিঃশেষিত। তাই তাঁরা সবার পক্ষেই নিরাপদ। কোনওকালেই এবং কোনও পক্ষই অমিয়ভূষণ মজুমদারকে নিয়ে সিরিয়াস চর্চা করবে না, কিছু দশ পনেরো ভক্ত-সমন্বিত পেজ অথবা মুষ্টিমেয় কাগজের দায়সারা আলোচনা বা স্মৃতিচারণ বাদ দিলে। অমিয়ভূষণ মজুমদার অবস্কিওর, কারণ তাঁর লেখা পাঠক পড়ে না। পাঠক পড়ে না কারণ আলোচনা হয় না। আলোচনা হয় না কারণ তিনি মুষ্টিমেয় কাগজের বাইরে অন্যত্র ডাক পাননি। ডাক পাননি কারণ তিনি ডিফিকাল্ট। এবং তিনি ডিফিকাল্ট কারণ তিনি অবস্কিওর। এই ভিসাস সার্কল তৈরির পেছনে পাঠকের ক্যালাসনেস দায়ী তো বটেই, কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাঁদের দৃষ্টি বড় প্রকাশনার বাইরে যায় না। কিন্তু সমানভাবে দায়ী এসব তথাকথিত লিটল ম্যাগাজিনগুলোও, যারা সিরিয়াস সাহিত্যচর্চার নামে সেইসব লেখকদেরই বেশিরভাগ সময়ে তুলে ধরে যাঁরা মনেপ্রাণে-অন্তরে মূলধারার, তাঁদের লিখনভঙ্গীমাও কোনওদিক থেকে ছক ভাঙার কথা বলে না। কিন্তু মূলধারাতে জায়গা পান না বলে অল্টারনেটিভের ছদ্মবেশ ধারণ করেছেন। লেখার শুরুতেই বলেছি, ক্ষমতার হায়ারার্কি ভাঙায় ফেসবুকের ভূমিকা সম্পর্কে ভুল লিখেছিলাম। সেটা ভুল ছিল, কারণ নতুন ক্ষমতার হায়ারার্কি তৈরি হয়েছে, এবং বাণিজ্যিক সংবাদপত্র শাসিত সাহিত্যকে হটিয়ে অথবা তারই পাশে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে জায়গা বানিয়ে নিয়েছে যেসব তথাকথিত বিকল্পের দল, তারা এই নতুন হায়ারার্কিতে শিখরে থাকে। তাদের আশেপাশে অসংখ্য পরজীবী, উপসেনাপতি, অমাত্য ও পাত্র-মিত্রদের বসবাস। সবাই এমন তা নয়। এর মধ্যেও অনেক ভালো কাগজ সত্যিই নিষ্ঠাভরে কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু তারা প্রান্তিক। প্রান্তেরও যে প্রান্ত থাকে, তাদের না দেখলে বোঝা যেত না।
তবু এর উল্টোদিকে রেজিস্টান্স থাকবেই। ভাষাকে ছেনে তার অভ্যন্তরের অন্ধকার মহাদেশ খুঁজে আনতে প্রাণপাত করলেন যে লেখক, খনির ভেতর থেকে দুর্মূল্য আকরিক তুলে আনার মতো শব্দ তুলে এনে ডায়নামাইটের তার বিস্তার করলেন যে কবি, প্রচলিতকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তথাকথিত অবস্কিওরিটির থমথমে সিঁড়িতে পা রাখলেন যে তরুণ গল্পলেখক, তাঁদের জায়গা থেকে যাবে। তাঁরা জগত ওলটাতে না পারুন, তাঁদের লেখালেখি দিয়ে কারোর কিছু না যায় আসুক, তবুও সেগুলো থাকবে। পুজোর লেখার তোয়াক্কা তাঁরা করবেন না। প্রতিষ্ঠা ও অর্জনের মুখ না চেয়েই তাঁরা বছরের পর বছর ধরে লিখে যাবেন একটা গল্প, বা একটাই উপন্যাস। শুধু তফাত হবে দ্রোহের নিশানায়। এখন যদি দ্রোহকালকে সৎ হতে হয়, তাহলে তার গাদাবন্দুক-প্রচেষ্টার অভিমুখ শুধুমাত্র বৃহৎ সংবাদপত্রশাসিত কাঠামোর উদ্দেশ্যেই নয়, বাড়িয়ে ধরতে হবে ছদ্ম-প্যারালালের দিকেও।
ছবি সৌজন্য: Pixnio, Publicdomainvectors,
শাক্যজিৎ ভট্টাচার্যের জন্ম ১৯৮২ সালে কলকাতায়। প্রথম গল্প বেরিয়েছিল পরিকথা পত্রিকায়, ২০০৩ সালে। এ পর্যন্ত লিখেছেন সাতটি উপন্যাস ও প্রায় চল্লিশটি ছোটগল্প। মূলত লিটল ম্যাগাজিনই তাঁর লেখালেখির জায়গা। এ পর্যন্ত পাঁচটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।