আমরা অনেকেই হয়তো বাংলার বনেদী বাড়ির দুর্গাপুজো নিয়ে মাতামাতি করি কিন্তু পৌরাণিক মতে বাংলায় প্রথম দুর্গাপুজো করেছিলেন যে সুরথ রাজা তাঁর রাজধানী বীরভূমের সুপুরের দুর্গাবাড়ির পুজোর কথা জানি না। সেখানেই গিয়েছিলাম এবার সুরথের জমিদারির দুর্গাবাড়ির ঠাকুরদালানে খড় জড়ানো মায়ের মূর্তির ওপর মাটি লেপা কাঠামোয় চোখ রাখতে। তবে এই দালানেই সুরথ হয়তো দুর্গাপুজো করেননি তা এই প্রবন্ধেই লিখেছি পরে। পুজো এখনও টিকিয়ে রেখেছেন তাঁর উত্তরসুরীর পরবর্তী জমিদার পরিবার। (Birbhum)

বোলপুর থেকে ইলামবাজারের রাস্তায় মাত্র ৮ কি.মি দূরে বর্ধিষ্ণু গ্রাম রূপে সুপুরের রমরমা ছিল ঈর্ষণীয়। কিংবদন্তী বলছেন সুপুরের চন্দ্রবংশীয় সুশাসক রাজা সুরথ কর্ণাট দেশ জয় করতে ব্যর্থ হলে তাঁর প্রজাবর্গ তাঁকে প্রত্যাখান করেন। রাজার দুরাবস্থার সুযোগে তাঁরই অমাত্যরা রাজার ধনসম্পদ ও রাজ্য অধিকার করে নেয়। রাজা নিরূপায় হয়ে মা ভগবতীর আরাধনায় সে রাজ্য পুনরায় ফিরে পান। মা ভবানীর পুজোয় একলক্ষ বলি দেওয়ার কারণে এই অঞ্চলের নাম হয় বলিপুর ও পরে বোলপুর। মারাঠা বর্গী আক্রমণে বিধ্বস্ত সুপুরের গল্প এখনও এখানকার জলে জঙ্গলে, অলিগলিতে, জমিদার বাড়ির আনাচেকানাচে প্রতিধ্বনিত হয় ঐতিহাসিক নীল চাষীদের গল্পের সঙ্গে। সেইসঙ্গে ভূগোল প্রমাণ করে আজও বাঙলার হৃত গৌরব এই সুপুর নামক নৌবন্দরের গল্প। (Lost seaport)
পৌরাণিক কাহিনিতে সুরথের রাজ্য চ্যুত হওয়া এবং দুর্গাপুজো করে সেই হৃত রাজ্য ফিরে পাওয়ার ঘটনাটি পরপর ছত্রে ছত্রে বর্ণিত মার্কণ্ডেয় পুরাণে।
মারাঠা বর্গী আক্রমণে বিধ্বস্ত সুপুরের গল্প এখনও এখানকার জলে জঙ্গলে, অলিগলিতে, জমিদার বাড়ির আনাচেকানাচে প্রতিধ্বনিত হয় ঐতিহাসিক নীল চাষীদের গল্পের সঙ্গে।
স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত এবং সম্পাদিত শ্রী শ্রী চণ্ডী (উদ্বোধন কার্যালয়) গ্রন্থে চণ্ডীর ষট্ সংবাদ কথায় রয়েছে একই সঙ্গে মেধস মুনি, সমাধি বৈশ্য এবং রাজা সুরথের নাম। দেবী মাহাত্ম্যে সেই সুপুর বা স্বপুরের নাম আজও ভাস্বর।
“তত: স্বপুরমায়াতো নিজদেশাধিপোহভবৎ।
আক্রান্ত: স মহাভাগস্তৈ স্তদা প্রবলারিভি:॥ ৭”
“মেধাস্তু কথয়ামাস সুরথায় সমাধয়ে।
সা কথা কথিতা পশ্চাৎ মার্কণ্ডেয়েন ভাগুরৌ।। ১”
অর্থাৎ অনন্তর মহাভাগ সুরথ প্রবল শত্রুগণ দ্বারা পরাভূত হয়ে নিজের রাজধানীতে ফিরে এসে স্বদেশের অধিপতি রইলেন।
“অমাতৈ:বলিভি:দুষ্টে:দুর্বলস্য দুরাত্মভি:।
কোষো বলঞ্চাপহৃতং তত্রাপি স্বপুরে তত:॥ ৮”
অর্থাৎ অনন্তর স্বীয় রাজধানীতেও দুষ্ট, দুরাশয় ও বলবান অমাত্যগণ অধুনা বলহীন রাজার রাজকোষাগার ও সৈন্যদের অধিকার করল।
“ততো মৃগয়াব্যাজেন হৃতস্বাম্যঃ সঃ ভূপতিঃ
একাকী হয়মারুহ্য জগাম গহনং বনম্।। ৯”
অর্থাৎ অনন্তর সেই রাজা রাজ্যপাট হারিয়ে মৃগ শিকার করতে একাকী অশ্বারোহণে গভীর অরণ্যে গমন করলেন।
“সঃ তত্রাশ্রমমদ্রাক্ষীদ্ দ্বিজবর্যস্য মেধসঃ।
প্রশান্তশ্বাপদাকীর্ণং মুনিশিষ্যোপশোভিতম্।। ১০”
অর্থাৎ সুরথ সেই হিংস্র পশু পরিপূর্ণ শান্তভাবাপন্ন বনমধ্যে মুনি শিষ্য শোভিত দ্বিজবর মেধস ঋষির আশ্রম দেখতে পেলেন।
“তস্থৌ কঞ্চিৎ সঃ কালঞ্চ মুনিনা তেন সৎকৃতঃ ।
ইতশ্চেতশ্চ বিচরংস্তস্মিন্ মুনিবরাশ্রমে।। ১১”
অর্থাৎ সেই মুনিবর কর্তৃক সমাদৃত হয়ে রাজা সুরথ আশ্রমে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে কিছু কাল অতিবাহিত করলেন।
এভাবে মেধস ঋষির সঙ্গে বিশদ আলাপচারিতায় উঠে এল সুরথের পূর্বপুরুষ চৈত্রাদিগণ প্রসঙ্গ এবং তাঁদের পরিত্যক্ত রাজ্যপাট, ধন সম্পত্তি সামলানোর কথা। কিন্তু সুরথ মোটেও ভুলতে পারেন না তাঁর সন্তানসম প্রজা, অমাত্যদের কথা। ঠিক সেইসময়েই আশ্রম সমীপে দেখা গেল সমাধি বৈশ্যকে।
“এতচ্চান্যচ্চ সততং চিন্তয়ামাস পার্থিবঃ।
তত্র বিপ্রাশ্রমাভ্যাসে বৈশ্যমেকং দদর্শ সঃ।। ১৬”

এরপরেই আমরা দেখি শ্রী শ্রী চণ্ডী জুড়ে মেধা ঋষি এবং সুরথ ও বৈশ্য এর কথোপকথনে কীভাবে চণ্ডী তথা দুর্গার মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে পরবর্তী বেশ কয়েকটি অধ্যায়ে এবং দুর্গার দ্বারা মহিষাসুরবধের সেই কালজয়ী আখ্যান শ্রবণ করে কীরূপে সুরথ ও বৈশ্য শত্রু দমনে ব্রতী হন দুর্গাপুজো করবেন বলে।
ত্রয়োদশ অধ্যায়ে মেধস ঋষি বলছেন, হে সুরথ, তোমাকে এই সর্বার্থসাধক দেবীমাহাত্ম্য বললাম।
“এতৎ তে কথিতং ভূপ দেবীমাহাত্ম্যমুত্তমম্” (২)
- হে মহারাজ, সেই পরমেশ্বরীর শরণাগত হও। তাঁর আরাধনাতেই মুক্তি প্রদান হবে তোমার। “তামুপৈহি মহারাজ শরণং পরমেশ্বরীম্”।
সেসব শ্রবণ করেই সমাধি বৈশ্য এবং সুরথ দেবী দুর্গার আরাধনা করতে গমন করেছিলেন নদীতটে। আর মৃন্ময়ী মূর্তি গড়ে সেখানেই মা দুর্গার পুজো করেছিলেন তাঁরা। শ্রী শ্রী চণ্ডীর ত্রয়োদশ অধ্যায়েই সে কথা রয়েছে।
“স চ বৈশ্যস্তপস্তেপে দেবীসুক্তং পরং জপন্।
তৌ তস্মিন্ পুলিনে দেব্যাঃ কৃত্বা মূর্তিং মহীময়ীম্।। ১০”
কিন্তু সুরথ মোটেও ভুলতে পারেন না তাঁর সন্তানসম প্রজা, অমাত্যদের কথা। ঠিক সেইসময়েই আশ্রম সমীপে দেখা গেল সমাধি বৈশ্যকে।
রাজা সুরথকে চৈত্রী বা চিত্রগুপ্তের বংশধর হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে দুর্গা সপ্তশতী দেবী মাহাত্ম্য এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণে। তিনি তাঁর রাজ্য এবং সমস্ত সম্পত্তি হারিয়ে নিজের ভাগ্য ফেরাতে রাজধানী বলিপুর ত্যাগ করেন। পরে বণিক সমাধি বৈশ্যের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। যিনিও সেই মুহূর্তে সব হারিয়ে দেউলিয়া। বৈশ্য সৌভাগ্যক্রমে মেধস মুনির আশ্রমে যেতে মেধস ঋষি তাঁদের ভাগ্য ফিরে পাওয়ার জন্য তাঁদের দেবী দুর্গার পুজো করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন।
এই সুরথ নামক ধার্মিক, প্রজাবৎসল রাজা যে তাঁর প্রজাদিগকে নিজের ঔরসজাত পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করতেন সে উল্লেখও রয়েছে শ্রী শ্রী চণ্ডীর প্রথম অধ্যায় “মধুকৈটভ বধে”। সেইসময় কোলাবিধ্বংসী (শূকর হত্যাকারী) যবন নরপতিগণ রাজা সুরথের রাজ্য আক্রমণ করলে তখন তাঁর প্রজাবর্গ সব পূর্ব কথা বিস্মৃত হয়ে রাজার শত্রু হল।
“তস্য পালয়তঃ সম্যক্ প্রজাঃ পুত্রানিবৌরসান্।
বভূবঃ শত্রবো ভূপাঃ কোলাবিধ্বংসিনস্তদা।। ৫”

শ্রী শ্রী চণ্ডী মতে, রাজা সুরথ এবং সমাধি বৈশ্য দুজনে মিলে পশ্চিমবঙ্গের গড় জঙ্গলে (আজকের পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরে) মেধস মুনির আশ্রমে মাটি দিয়ে দেবী দুর্গার মূর্তি গড়ে পুজো করেছিলেন। এই গড়জঙ্গলের বোয়ালখালিতে মেধসঋষির আশ্রমের এই দুর্গাপুজোই বাংলার প্রথম বাসন্তী দুর্গোৎসব যার কথা কালিকাপুরাণ ও কামাখ্যা পুরাণেও রয়েছে, এমনটি জানিয়েছেন বর্তমান আশ্রমের সভাপতি অধ্যাপক সচ্চিদানন্দ রায়চৌধুরী। এখন এই আশ্রমের প্রবেশদ্বারে লেখা রয়েছে “শ্রী শ্রী চণ্ডীতীর্থ মেধস আশ্রম”- এই বলে। দুর্গাপুজোয় এখনও সেখানে মহা ধূম করে দুর্গোৎসব হয় আর দুর্গা সেখানে শ্যামরূপা নামে পূজিতা হন।
এইরূপেই শ্রী শ্রী চণ্ডীর মাহাত্ম্য কালে কালে পরম্পরা ক্রমে প্রচলিত এবং প্রচারিত হলেও বাঙালি হয়তো ভুলে গেছে বোলপুরের সুরথ রাজার রাজধানী সুপুর এবং দুর্গাপুরের মেধস ঋষির আশ্রমকে।
এই গড়জঙ্গলের বোয়ালখালিতে মেধসঋষির আশ্রমের এই দুর্গাপুজোই বাংলার প্রথম বাসন্তী দুর্গোৎসব যার কথা কালিকাপুরাণ ও কামাখ্যা পুরাণেও রয়েছে
নিজের সমস্ত হারানো সম্পত্তি, রাজ্যপাট ফিরে পেলে তাঁর রাজধানী বলিপুরে ফিরে আসেন সুরথ। আর এই সুরথের দুর্গাপুজোই ছিল বাংলার প্রথম দুর্গাপুজো। তবে তা অনুষ্ঠিত হয়েছিল চৈত্রমাসে। বসন্তকালের বাসন্তী পুজো নামে তা খ্যাত। রাজ্য ফিরে পেতে সুরথ আবার বোলপুরে প্রতিষ্ঠা করেন সুরথেশ্বর শিব মন্দির যেটির নবতম সংস্করণ আমরা দেখতে পাই প্রাচীন মন্দিরের ওপরেই। মন্দিরের অভ্যন্তরে গর্ভগৃহে বিশাল শিবলিঙ্গটি কালাপাহাড় দ্বারা ভাঙা হয়েছিল। জানালেন বর্তমান মন্দিরের পূজারী। এই শিবলিঙ্গ পুজো করতেন সুরথ। সুরথেশ্বর মন্দির বোলপুর-ইলামবাজার সড়কের পাশেই শিবতলায় অবস্হিত৷ সুরথেশ্বর মন্দির একসময় ঘন জঙ্গলাবৃত ছিল৷ প্রায় একশো বছর আগে গজপতিনাগ নামে এক শৈব সাধু এই মন্দিরের আংশিক সংস্কার সাধন করেন৷ ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে রাইপুরের জমিদার বংশজ প্রমথনাথ সিংহের স্মৃতির উদ্দেশ্যে তাঁর অর্ধাঙ্গিনী শ্রীমতি সুভাষিনী দাসীর সহায়তায় সুরথেশ্বর মন্দির নতুন করে তৈরি হয়৷ মন্দির গাত্রের প্রস্তর ফলকেই লেখা দেখলাম।

সুপুর রাজবাড়ির সে ঠাটবাট, রাজকিয়তা বা কৌলিন্য হয়তো তেমন নেই তবে বিশাল অরণ্যময় চত্ত্বর জুড়ে ঠাকুরদালান, দুর্গাবাড়ি, ভোগঘর, সম্বলিত প্রাচীন শিবমন্দিরের টেরাকোটার ভগ্নাবশেষ আর নিলয় অলিন্দে চামচিকের আনাগোনা দেখে বেশ মাহাত্ম্য প্রতিভাত হয়। এখন সেখানে অস্থায়ী প্রাইমারি স্কুল চালায় কোনও এনজিও। রাজবাড়ির প্রধান ফটকে তেমনই লেখা দেখলাম। গেটে তালা বন্ধ ছিল রবিবারের ভোরে। পাশের গ্রামে জিজ্ঞাসা করায় এক অশীতিপর বৃদ্ধা লাঠি হাতে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এলেন হাতে চাবি নিয়ে। তাঁর নাম পুষ্প যিনি একসময় ছিলেন সেখানকার খাস রাঁধুনি। সুরথের রাজবাড়িতে বংশানুক্রমে যে জমিদারবাড়ির প্রতাপ প্রতিপত্তি বহুবছর ধরে টিকে ছিল ছিলেন। জানালেন পুষ্প। সুপুরে পরবর্তীকালে জমিদারত্ব দেখা যায়। সুপুরের জমিদাররা গুপ্তিপাড়া হতে আগত গোপাল মজুমদার৷ আমার সঙ্গে আলাপ হওয়া পুষ্পর মুখে নাম শুনলাম মজুমদারদের। রাজা সুরথের স্মৃতিতে হাটসেরান্দীর গোমস্তা চাটুজ্জেরা বাসন্তীপুজার প্রচলন করলেন পুরনো হাটতলায়৷ জমিদারদের কিছু গৃহ নতুন করে মেরামত করে উত্তরসূরীরা বাসযোগ্য করে তুললেও সুপুরের জমিদারদের প্রভাব প্রতিপত্তি কালে কালে ক্ষয়িষ্ণু হয়।
এখন সেখানে অস্থায়ী প্রাইমারি স্কুল চালায় কোনও এনজিও। রাজবাড়ির প্রধান ফটকে তেমনই লেখা দেখলাম। গেটে তালা বন্ধ ছিল রবিবারের ভোরে।
বোলপুরের ৩ কি.মি দক্ষিণে অজয় নদের তীরে সুপুর আজও স্বামহিমায় এক সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রাম। সুপুরের বিভিন্ন পুরনো বাড়ি থেকে আজও উঁকি দেয় দেওয়ালের ইট আর পোড়ামাটির মন্দির গাত্রে থাকা বট, অশথের শিকড়। সেসব আজও বহু প্রাচীন ইতিহাসের সাক্ষ আঁকড়ে ধরে রয়েছে। অতীতে সুপুরের নাম ছিল ‘স্বপুর’ বা ‘সুবাহুপুর’৷ আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে রাঢ়বাংলায় রাজত্ব করতেন রাজা সুবাহু সিংহ৷ তাঁর প্রতিষ্ঠিত জনপদ সুবাহুপুরই হল আজকের সুপুর৷ অতীতে সুপুর ছিল একটি রাজ্য৷ রাজা সুবাহুর পরবর্তী এক বংশধর ছিলেন রাজা সুরথ৷ কিংবদন্তি ঘটনা অনুযায়ী পৌরাণিক রাজা সুরথ রাজ্যহারা হয়ে এখানেই আশ্রয় নেন। আর মার্কন্ডেয় পুরাণ অনুযায়ী তিনিই নাকি নতুন করে প্রথম বসন্তকালীন দুর্গা পূজা শুরু করেন৷ হারিয়ে যাওয়া গৌরব ফিরে পেতে তিনি গ্রাম্যদেবী ভগবতী শিবিক্ষা বা সুবিক্ষার উপাসনার জন্য লক্ষ বলি দেন বলে জনশ্রুতি আছে৷ এই বলি সুপুরের বাঘালা পুকুরের পার্শ্ববর্তী সুবিক্ষা মন্দির থেকে শুরু করে রজতপুরের মহামায়া মন্দির হয়ে বোলপুরের ডাঙ্গালি কালিতলা পর্যন্ত হয়েছিল৷ এরপরই ডাঙ্গালি কালীতলা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল বলিপুর নামে খ্যাত হয়। এই বলিপুরই কালক্রমে হয়ে ওঠে আজকের বোলপুর। শিবিক্ষা মন্দিরের পশ্চিম কোণে বাঘালা (বাঁধা ঘাট) পুকুর৷ পরবর্তী আমলে তৈরি পুকুরটির পূর্ব পাড়ে বাঁধানো সিঁড়ির সম্মুখেই ছিল দুটি বাঘের মূর্তি যা কালে কালে বিলুপ্ত ৷ এই বাঘ মূর্তি থেকেই পুকুরের নাম বাঘওয়ালা বা বাঘালা পুকুর৷

বোলপুর তখনও শহর হয়ে ওঠেনি। তার আগেই সুপুর ছিল বাংলার একটি উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য কেন্দ্র৷ সুরথ বন্দর নামে খ্যাত এই নৌবন্দরটি সুপ্রসিদ্ধ ছিল। অজয়নদের তীরে মঙ্গলকোট ছাড়া এত বড় বন্দর আর দ্বিতীয় ছিল না। অজয় নদীপথে হাজারিবাগ, সুরাট, চন্দ্রকেতুগড়, তিব্বত, অসম সহ নানা জায়গা থেকে আসা পণ্যসামগ্রীর ব্যবসা-বাণিজ্য রমরমিয়ে চলত সুপুরে৷ ব্যবসার জন্য বাংলার উপকূলে তখন আসতে শুরু করেছে পর্তুগিজরা৷ সেই সময় বাংলায় নুনের ব্যবসা করতে একদল ব্যবসায়ী আসে গুজরাট থেকে৷ তারাই আজকের গন্ধবণিক চন্দ্র নামে বাংলায় সুপরিচিত৷ কাটোয়ার গঙ্গার ধারে লবণগোলাই ছিল এদের ব্যবসার কেন্দ্র৷ এক সময় জমি জায়গা কিনে শ্রীবাটি গ্রামে স্থায়ী হয়েছিল তারা৷ এখান থেকে সুপুর বন্দরে লবণ আসত৷ সুপুরের অজয় তীরে দুটি ঘাট ছিল৷ বর্তমান সুপুর দক্ষিণ পাড়ার পশ্চাতে ছিল ‘মাঠতলার’ ঘাট, আর একটু পশ্চিমেই ছিল ‘নুন ভাঙা ঘাট’, এখানে ভিজে নুন শুকিয়ে গুঁড়ো করা হত।
পুরনো নৌবন্দর সুপুর কীভাবে হারাল তার গৌরবময় ইতিহাস! অজয়ের তীরের ইটান্ডা, সুপুর, ইলামবাজার বন্দরগুলি ফলস্বরূপ বিলীন হতে থাকল একে একে।
যে স্থানে ব্যবসায়ীরা তাদের পসরা সাজিয়ে বসতেন, সেটি বর্তমানে হাটরসুলগঞ্জ নামে পরিচিত৷ ১৮৫০ সালে খানা থেকে সাঁইথিয়া গামী রেলপথ নির্মাণের জন্য অজয় নদের উপর রেল ব্রীজ (বত্রিশ ফোঁকর) তৈরি হল৷ এর রূপকার ছিলেন রাইপুরের জমিদার পরিবারের নীলকণ্ঠ সিংহের পুত্র রুদ্রপ্রসন্ন সিংহ এবং স্টেম্বার সাহেব৷ তাই সুপুর বন্দরের গুরূত্ব কমতে থাকে আর রসুলগঞ্জের হাট উঠে গিয়ে বসল বর্তমান বোলপুর হাটতলায়৷ বোলপুরের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্ববর্তী রাইপুর, মির্জাপুর, রজতপুর, সুপুর, সর্পলেহনা, রূপপুর, বেড়গ্রাম, দেবগ্রাম, গয়েশপুর, চন্দনপুর সহ নানা গ্রামগুলি থেকে মানুষজনের ঢল নামত বোলপুরে। বোলপুর থেকে মাত্র ৩ মাইল দক্ষিণে হাজার বছরের পুরনো নৌবন্দর সুপুর কীভাবে হারাল তার গৌরবময় ইতিহাস! অজয়ের তীরের ইটান্ডা, সুপুর, ইলামবাজার বন্দরগুলি ফলস্বরূপ বিলীন হতে থাকল একে একে। অথচ ঘনরামের ধর্মমঙ্গল কাব্য থেকে কবি রামভদ্রের সত্যনারায়ণের পাঁচালি… সবখানেই রয়ে গেল এই সুরথবন্দর সুপুরের উচ্ছ্বসিত বর্ণনা। সেসব ছবি হাজার বছর আগের নৌবন্দর সুপুরের এক গৌরবময় অভিলেখ যেখানে নৌবন্দর সুপুরের বিকিকিনির ছবিখানিও সুস্পষ্ট। রামভদ্রের পাঁচালিই তার প্রমাণ।

আরও পড়ুন: একাত্তরের মুক্তির গান
গৌড়ের বণিক সাধু ধনপতি তাঁর একমাত্র কন্যার সঙ্গে শৈশবে পিতৃমাতৃহীন চন্দ্রকেতু সদাগরের বিয়ে দেন। একবার গৃহজামাতা চন্দ্রকেতু কে সঙ্গে নিয়ে বণিক ধনপতি বাণিজ্য যাত্রায় যান। বহু নদ নদী অতিক্রম করে তাঁর সপ্তডিঙা নিয়ে সুরথবন্দর সুপুরে উপস্থিত হন তাঁরা। রাজা সুরথকে যথাযোগ্য ভেট দান করে সন্তুষ্ট করলে সেই সুপুর বন্দরের বিশাল বাণিজ্যকেন্দ্রে পণ্য বেচাকেনার অধিকার লাভ করেন ধনপতি। এমনকি রামভদ্রের বর্ণনায় সেই বন্দরে তুর্কি, টাঙ্গন ও ভাজি শ্রেণীর ঘোড়া বিক্রয়ের গল্পও রয়েছে। নদীপথে সুরথবন্দর সুদূর গুজরাট, কর্ণাটক, সেতুবন্ধ, চাকুল বা চন্দ্রদ্বীপ এর পাশাপাশি আমাদের পরিচিত হাজিবাগ, ধনেখালি, মালদা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বালানন্দ শহরের সঙ্গেও যুক্ত ছিল এই সুপুর। ডঃ সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতে গৌড়ে ঘোড়ামারা নদী তীর থেকে ঘোড়া আনা হত। সুপুর বন্দরের অদূরবর্তী একটি অঞ্চল আজও ঘোড়ামারা নামে খ্যাত। ঘোড়া মারা নদীতীরবর্তী অঞ্চল থেকে আগত ঘোড়াগুলি এখানকার বাজারে বিক্রীত হত, তাই এই নাম। এই ঘোড়াপাড়া এখন সম্পূর্ণ মুসলনমান অধ্যুষিত যার নিকটেই মহারাজ সুরথের “রজতভাণ্ডার” রূপে খ্যাত রজতপুর গ্রাম। সুরথ আরাধিত শ্রী শ্রী চণ্ডী মায়ের মূল ধাতব মূর্তিটি এখনও সে গ্রামে বিরাজমান।

আজ এই সুপুর বন্দর নিশ্চিহ্ন। নদীপথ পরিত্যক্ত। ১৮৫০সালে রেলসেতু অজয়ের গতিপথ প্রশস্ত বুকে গতিপথ রুদ্ধ করে। নদীতীরের গ্রাম গঞ্জ, বন্দর নির্জন অরণ্যে পর্যবসিত হয়। হাওড়া সাহেবগঞ্জ লুপে অজয় সেতু অতিক্রমকালে পশ্চিমদিকে সুপ্রাচীন সুরথ বন্দরের ধ্বংসস্তূপ আজও চোখে পড়ে।
এই ঘোড়াপাড়া এখন সম্পূর্ণ মুসলনমান অধ্যুষিত যার নিকটেই মহারাজ সুরথের “রজতভাণ্ডার” রূপে খ্যাত রজতপুর গ্রাম।
সুপুরের প্রধান আকর্ষণ শিখর দেউল পদ্ধতিতে নির্মিত প্রসিদ্ধ জোড়া শিব মন্দির, যা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭১৭ সালে৷ এটি ছিল একটি পারিবারিক মন্দির যা তৎকালীন সময়ে স্থানীয় কোনও এক ময়রা পরিবার কর্তৃক তৈরি হয়েছিল৷ বর্তমানে মন্দিরটি আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার তত্ত্বাবধানে সংরক্ষিত রয়েছে৷ বর্ধমান থেকে গুসকরা হয়ে ভেদিয়াঘাটে অজয় নদ পেরিয়ে বোলপুরে ঢোকবার কিছু আগেই বাঁ দিকে দেখা যাবে এই দুই জোড়া শিব মন্দির। এই দুই মন্দিরের টেরাকোটার প্যানেলে দেবদেবীর মূর্তি এখনও অমলিন। এছাড়াও সুপুরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বেশ কয়েকটি মন্দির।
তথ্যসূত্র :
স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত এবং সম্পাদিত শ্রী শ্রী চণ্ডী (উদ্বোধন কার্যালয়)
বীরভূম দর্পণ – বিজয় কুমার দাস
সুপুর-রজতপুরের প্রত্ন গুরুত্ব – সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় (রজতপুর ইন্দ্রনারায়ণ বিদ্যাপীঠ থেকে প্রকাশিত প্রবন্ধ)
পায়ে পায়ে বীরভূম – রত্না ভট্টাচার্য, শক্তিপদ ভট্টাচার্য
বীরভূম পরিচিতি – সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়
[ছবিসত্ত্ব – লেখক
কেবলমাত্র ইন্টারনেট আর্কাইভ থেকে প্রাপ্ত গড়জঙ্গলে মেধস ঋষির আশ্রমের বর্তমান ছবি]
রসায়নের ছাত্রী ইন্দিরা আদ্যোপান্ত হোমমেকার। তবে গত এক দশকেরও বেশি সময় যাবৎ সাহিত্যচর্চা করছেন নিয়মিত। প্রথম গল্প দেশ পত্রিকায় এবং প্রথম উপন্যাস সানন্দায় প্রকাশিত হয়। বেশ কিছু বইও প্রকাশিত হয়েছে ইতিমধ্যেই। সব নামীদামি পত্রিকা এবং ই-ম্যাগাজিনে নিয়মিত লেখেন ছোটগল্প, ভ্রমণকাহিনি, রম্যরচনা ও প্রবন্ধ।




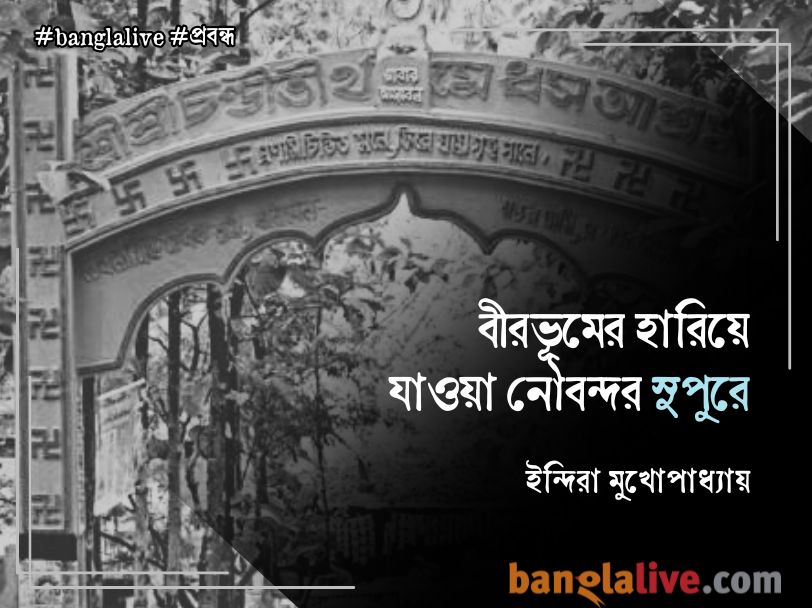





















One Response
আপনার লেখাটি পড়ে সমৃদ্ধ হলাম।
আপনার কলম থেকে আরো কিছু মণিমুক্তার আশায় রইলাম। ধন্যবাদ