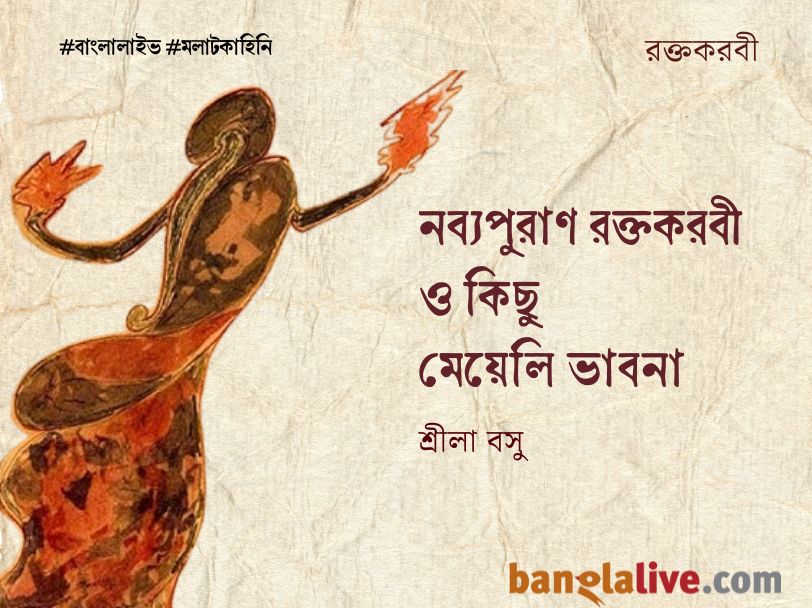(Raktakarabi)
রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন রক্তকরবী নাটকটা হচ্ছে ‘নন্দিনী নামে একটি মানবীর ছবি’। তবে নন্দিনী বা যক্ষপুরী নাম প্রথমে রাখলেও শেষ পর্যন্ত তিনি বেছে নিয়েছিলেন রক্তকরবী নামটি। ব্যক্তিনামের বদলে ফুলটির মধ্যে বিদ্রোহের যে রং এবং বিষের অনুষঙ্গ আছে তাকেই চূড়ান্ত করলেন নাট্যকার। (Raktakarabi)
আরও পড়ুন: রক্তকরবী’: বিগ ব্রাদার— The ‘Terrifying Bigness’
নন্দিনী যক্ষপুরীর মানুষ নয়। সে এসেছে ঈশানী পাড়া থেকে। তার পরনে ধানী রঙের শাড়ি। রবীন্দ্রনাথ এ নাটকের সঙ্গে কর্ষণজীবী এবং আকর্ষণজীবী সভ্যতার দ্বন্দ্বের তুলনা করেছেন। রক্তকরবী নাটকটিকে নব্যরামায়ণ হিসেবে দেখতে পছন্দ করতেন রবীন্দ্রনাথ। রামের নবদূর্বাদল শ্যাম গায়ের রং আর নন্দিনীর ধানী রঙের শাড়ি– এই দুইই কৃষি সভ্যতার প্রতীক। বাইরে দৌরাত্ম্যে কৃষি নষ্ট হয়, আবার ভেতরের কারণেও তার ক্ষয় হয়। রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এ কথা বলেছেন জাভা-যাত্রীর পত্র -এ। রামায়ণে কৃষির প্রতীক সীতা কখনও বাইরের দৌরাত্ম্যে কষ্ট পেয়েছেন কখনও ভেতরের কারণে অর্থাৎ রামের জন্যে। রবীন্দ্রনাথের কাছে রক্তকরবীর রাজা হলেন এক দেহে রাম ও রাবণ ‘সে আপনাকেই আপনি পরাস্ত করে’। (Raktakarabi)
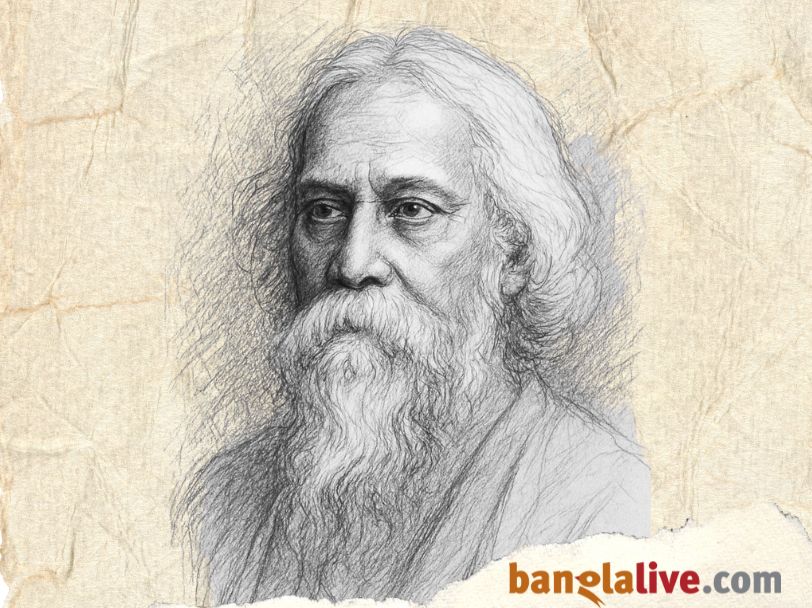
রক্তকরবী সম্পর্কে রামায়ণের যে ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন আপাতত তাকে একটু সরিয়ে রাখি আমরা। রামায়ণের কাহিনির কেন্দ্রে আছেন রাম। মহাকাব্যের সংরূপ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে নবনীতা দেবসেন বলেছিলেন যে মহাকাব্য পুরুষের কথা বলে। বাহুবলের কথা বলে। মহাকাব্যে নারী কখনও কর্তা হয় না, তাকে ঘিরে নানা কর্ম ঘটে। যার ফল হচ্ছে যুদ্ধ বা দ্বন্দ্ব। সীতা-দ্রৌপদী-হেলেন সকলেই এইভাবে পুরুষের বিরোধের, পুরুষের লোভের উপলক্ষ হয়ে উঠেছেন। নবনীতা এও দেখিয়েছেন যে মহাকাব্যে নারীকে সবসময়ই বিপদ বা বিরোধের কারণ হিসেবে দোষারোপ করা হয়। (দ্র. নায়িকা সংবাদ: প্রাচী ও প্রতীচী, চন্দ্র-মল্লিকা এবং প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ, দে’জ পাবলিশিং, ১৪২২) (Raktakarabi)
নারী পুরষ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের একটা স্পষ্ট ভাবনা ছিল। সমাজে সম্পর্কের মধ্যে দু’জনের ভূমিকা আলাদা বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন। মেয়েরা জন্মায় মায়ের পূর্ণতা নিয়ে একথা রাণী চন্দকে বলছেন তিনি (দ্র আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী, ১৯৪৬)। পুরুষ স্বভাবত অসম্পূর্ণ তাদের মধ্যে দূরের প্রতি আকর্ষণ সেইজন্য স্বাভাবিক। স্বেচ্ছাবিহার প্রিয় পুরুষের সঙ্গে অবরুদ্ধ গৃহবাসিনী নারী দুজনের স্বভাবের এই বিপরীতমুখিনতার কথা রবীন্দ্রনাথ বারবার বলছেন। এও এক ধরনের সামাজিক নির্মাণ। মেয়েরা প্রেরণা দেবে, সেবা করবে এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বদ্ধমূল ধারণা ছিল। (Raktakarabi)
“পুরুষের প্রকৃতিতে সৃষ্টিকর্তার তুলি আপন শেষ রেখাটা টানে নি। পুরুষকে অসম্পূর্ণই থাকতে হবে।”
পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারিতে রবীন্দ্রনাথ নাটকটির তাৎপর্য বুঝিয়েছেন এইভাবে। এই নাটকের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নারী পুরষ ভাবনার কথাও এখানে স্পষ্ট। (Raktakarabi)
লক্ষ্মীতে সৌন্দর্য হচ্ছে পরিপূর্ণতার লক্ষণ। সৃষ্টিতে যতক্ষণ দ্বিধা থাকে ততক্ষণ সুন্দর দেখা দেয় না। সামঞ্জস্য যখন সম্পূর্ণ হয় তখনই সুন্দরের আবির্ভাব।…
পুরুষের কর্মপথে এখনো তার সন্ধানচেষ্টার শেষ হয় নি। কোনো কালেই হবে না। অজানার মধ্যে কেবলই সে পথ খনন করছে, কোনো পরিণামের প্রান্তে এসে আজও সে অবকাশ পেলে না। পুরুষের প্রকৃতিতে সৃষ্টিকর্তার তুলি আপন শেষ রেখাটা টানে নি। পুরুষকে অসম্পূর্ণই থাকতে হবে। (Raktakarabi)
…স্থিতির ফুলই হচ্ছে নারীর মাধুর্য, সেই স্থিতির ফলই হচ্ছে নারীর মাঙ্গল্য, সেই স্থিতির সুরই হচ্ছে নারীর শ্রীসৌন্দর্য।
“সেই নারীশক্তির নিগূঢ় প্রবর্তনায় কী করে পুরুষ নিজের রচিত কারাগারকে ভেঙে ফেলে প্রাণের প্রবাহকে বাধামুক্ত করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হল, এই নাটকে তাই বর্ণিত আছে।”
নারীর ভিতর দিয়ে বিচিত্র রসময় প্রাণের প্রবর্তনা যদি পুরুষের উদ্যমের মধ্যে সঞ্চারিত হবার বাধা পায় তা হলেই তার সৃষ্টিতে যন্ত্রের প্রাধান্য ঘটে। তখন মানুষ আপনার সৃষ্ট যন্ত্রের আঘাতে কেবলই পীড়া দেয়, পীড়িত হয়। (Raktakarabi)
এই ভাবটা আমার রক্তকরবী নাটকের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। যক্ষপুরে পুরুষের প্রবল শক্তি মাটির তলা থেকে সোনার সম্পদ ছিন্ন করে করে আনছে। নিষ্ঠুর সংগ্রহের লুব্ধ চেষ্টার তাড়নায় প্রাণের মাধুর্য সেখান থেকে নির্বাসিত। সেখানে জটিলতার জালে আপনাকে আপনি জড়িত করে মানুষ বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই সে ভুলেছে সোনার চেয়ে আনন্দের দাম বেশি; ভুলেছে, প্রতাপের মধ্যে পূর্ণতা নেই, প্রেমের মধ্যেই পূর্ণতা। সেখানে মানুষকে দাস করে রাখবার প্রকাণ্ড আয়োজনে মানুষ নিজেকেই নিজে বন্দী করেছে। (Raktakarabi)
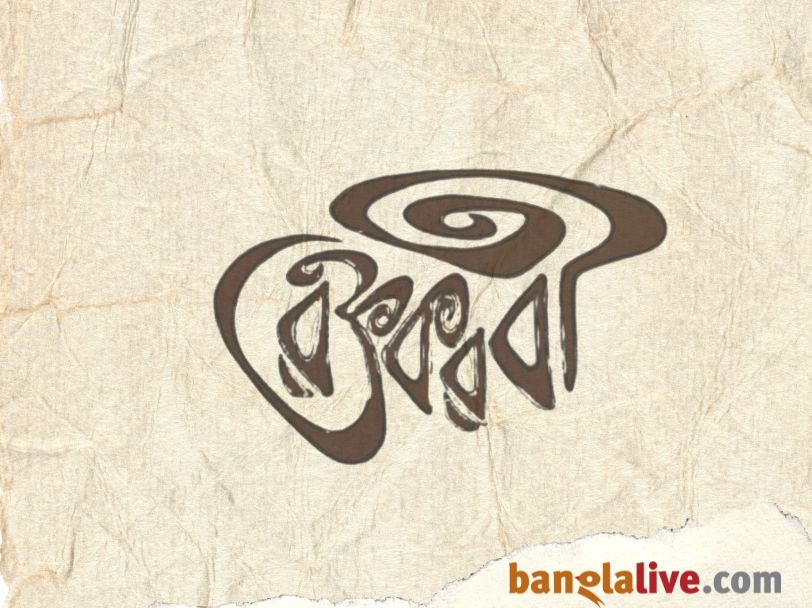
এমন সময়ে সেখানে নারী এল, নন্দিনী এল: প্রাণের বেগ এসে পড়ল যন্ত্রের উপর; প্রেমের আবেগ আঘাত করতে লাগল লুব্ধ দুশ্চেষ্টার বন্ধনজালকে। তখন সেই নারীশক্তির নিগূঢ় প্রবর্তনায় কী করে পুরুষ নিজের রচিত কারাগারকে ভেঙে ফেলে প্রাণের প্রবাহকে বাধামুক্ত করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হল, এই নাটকে তাই বর্ণিত আছে। (Raktakarabi)
“তাঁর অনেক রচনায় দেখছি তারই কথা। মেয়েদের মধ্যে পূর্ণতার কথা, তাঁর ইংরেজি লেখা Personality-র Woman প্রবন্ধেও আছে। কুঁড়ি, ফুল, ফলের পূর্ণতার সঙ্গে মেয়েদের পূর্ণতার তুলনা করেছেন।”
কিছু বাক্যাংশ বাদ দিয়েও উদ্ধৃতিটি দীর্ঘ হল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মন বুঝতে এ অংশটি উদ্ধার করা ছাড়া উপায় ছিল না। রবীন্দ্রনাথের কাছে নারীর ভূমিকা তাহলে পুরোটাই পুরুষ সাপেক্ষ। নারী পরিপূর্ণ তার নিজের জগতে। সে জগত যে সৃষ্টিশীলতার পক্ষে যথেষ্ট নয়, তা ন’দিদি স্বর্ণকুমারী প্রসঙ্গে রাণী চন্দকে বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এসব কথা একবিংশ শতাব্দীতে এমনকি রবীন্দ্রনাথের সমকালেও বেসুর শোনালেও রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল এমনিই। তবে রবীন্দ্রনাথ বিদ্রোহিণী নারীর কথা এই ডায়ারিতে বলেননি। অথচ তাঁর অনেক রচনায় দেখছি তারই কথা। মেয়েদের মধ্যে পূর্ণতার কথা, তাঁর ইংরেজি লেখা Personality-র Woman প্রবন্ধেও আছে। কুঁড়ি, ফুল, ফলের পূর্ণতার সঙ্গে মেয়েদের পূর্ণতার তুলনা করেছেন। (Raktakarabi)
রবীন্দ্রনাথ যক্ষ কুবের বা মকরের কথা এ নাটকে বলেছেন। এরা সবাই পৌরাণিক উপদেবতা বা ডেমি গড। দেবতা আর দানবের মাঝখানে তাদের অবস্থান। এই নাটকটির আবহে পুরাণের পরিবেশ পুরোদস্তুর রয়েছে। কিন্তু এই নব্য পুরাণে নারীকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের অবস্থান একেবারে অন্যরকম। এই নাটকে চরিত্র এবং ঘটনাগুলিকে গতি দিচ্ছে নন্দিনী। প্রথমে কিশোর তারপর একে একে অধ্যাপক রাজা বিশু প্রধানত এই কয়েক জনকে নাড়া দিয়েছে নন্দিনী। প্রত্যেকের সঙ্গে নন্দিনীর আলাপ, রবীন্দ্রনাথ দেখাচ্ছেন, সকলেরই মনে চমক লাগায় সে। সেই চমক অনেকটা নতুনকে, খাপছাড়াকে দেখবার বিস্ময়। শুধুই মুগ্ধতা নয়। ফাগুলাল চন্দ্রা তাকে নিয়ে কৌতূহলী। কিছুটা সন্দিগ্ধও বটে, বিশেষত চন্দ্রা। যক্ষপুরীতে এরা সবাই যখন পুরীর ব্যবস্থার অঙ্গ হিসেবে ছিল নন্দিনী এসে তাদের ব্যবস্থাটা ওলোট পালট করে দিচ্ছে। (Raktakarabi)
রবীন্দ্রনাথের নাটকে অবশ্য এ বিষয়টা একেবারেই নতুন নয়। রুদ্রচন্ড থেকে বাল্মীকি-প্রতিভা, প্রকৃতির প্রতিশোধ থেকে বিসর্জন সব জায়গাতেই একটি মেয়ে প্রচলনকে প্রশ্ন করে ওলোট-পালট করে দিচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের মেয়েরা শুধু সেবা বা প্রেরণা জোগায় না, তারা চরিত্রগুলোর শেকড় পর্যন্ত নাড়িয়ে দিয়েছে। নন্দিনী সম্পর্কে রক্তকরবীতে বারবার বিদ্রোহের কথা এসেছে। যক্ষপুরীর শক্তিকে নন্দিনী তার জাদু দিয়ে ধাক্কা মারতে পেরেছে। নন্দিনীর সুন্দরীপনা নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করেছে চন্দ্রা। তার সাজ তার চলন- বলন সবকিছুই একান্তভাবে ‘মেয়েলি’ অথচ তার চরিত্র বল কিছু কম নয়। (Raktakarabi)
“রবীন্দ্রনাথের এই নব্যপুরাণে নারীর ভূমিকা রয়েছে কেন্দ্রে। সনাতন মহাকাব্যে নারী যেমন কর্তা হন না কখনও, হন কর্ম মাত্র; রবীন্দ্রনাথ তা করেননি। শুধু রক্তকরবীতে নয় রবীন্দ্রনাথের বহু রচনাতেই কেন্দ্রে থাকেন নারী।”
ঠিক এইখানেই মেয়েদের সেবা- মাধুর্য দিয়ে গড়া লক্ষ্মীর আর্কেটাইপ, যা তিনি নিজে তৈরি করেছেন তাকে নিজেই ভাঙছেন তিনি। শুধু প্রেরণা দিয়ে ব্যবস্থাকে প্রশ্ন করা বা ভাঙা যায় না। তার জন্য দরকার বুদ্ধি এবং ব্যক্তিত্বের জোর। রঞ্জনের মৃতদেহ দেখেও নন্দিনী রুখে দাঁড়ায়নি কিন্তু কিশোরকে মরতে দেখে সে রাজার সঙ্গে লড়াই ঘোষণা করল। শুধু প্রেম নয় নন্দিনীর স্নেহ ধাক্কা খেল কিশোরকে দেখে। নন্দিনীর বিদ্রোহের মূলে রয়েছে তার ধাক্কা খাওয়া স্নেহ। (Raktakarabi)
মেয়েরা যে ভাঙতেও পারে শুধু গড়তে নয়, তা রবীন্দ্রনাথই দেখিয়েছেন বিসর্জন-এ গুণবতীর মধ্যে দিয়ে, তাসের দেশ-এ রানির মধ্যে দিয়ে। রাজা ও রানীর রেবতী বা বিসর্জন-এ গুণবতীর ভূমিকাটি নঞর্থক , তাসের দেশ-এর রানি তা নন। মেয়েদের এই সহজাত বুদ্ধি, যার মধ্যে সহজ প্রাণ আছে তাকে রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করেননি। বরং মান দিয়েছেন। বিদ্রোহের মশাল ধরিয়েছেন নন্দিনী বা তাসের রাণীর হাতে। (Raktakarabi)

চন্দ্রা নন্দিনীকে বিশ্বাস করেনি। সে যে সর্বনাশ বহন করে আনবেই এ তার একান্ত ধারণা ছিল। অচলায়তনে গুরু আসবার মতো নন্দিনীর যাত্রা। যে যাত্রায় রাজা থেকে চন্দ্রা সবাই সঙ্গ দেয়। অচলায়তন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠিতে বুঝিয়েছিলেন যে তিনি শুধু ভাঙবার কথাতেই শেষ করেননি গড়ার কথাও আছে। রক্তকরবীতে আবার গড়ার কোনও ইঙ্গিত রবীন্দ্রনাথ দেননি। নবতর যক্ষপুরী নির্মাণের প্রয়োজনও ছিল না। ‘টাইটানিক ওয়েলথ’এর দাপট ধূলিসাৎ করাই রবীন্দ্রনাথের দেখানোর উদ্দেশ্য ছিল। (Raktakarabi)
রবীন্দ্রনাথের এই নব্যপুরাণে নারীর ভূমিকা রয়েছে কেন্দ্রে। সনাতন মহাকাব্যে নারী যেমন কর্তা হন না কখনও, হন কর্ম মাত্র; রবীন্দ্রনাথ তা করেননি। শুধু রক্তকরবীতে নয় রবীন্দ্রনাথের বহু রচনাতেই কেন্দ্রে থাকেন নারী। সেই ঘটনানিয়ন্তা। রবীন্দ্রনাথ রামায়ণ তুলে যত উপমাই ব্যবহার করুন তাঁর এই নব্যরামায়ণটি চরিত্রগতভাবে তাঁর থেকে ঢের দূরের। (Raktakarabi)
আরও পড়ুন: বর্ষামঙ্গল ও রবীন্দ্রনাথ
ব্যক্তিত্বে রবীন্দ্রনাথ এমন এক ভবিষ্যতের আভাস দিয়েছেন যেখানে মেয়েরাই হাল ধরবে জীবনের। প্রাচীন যুগের ম্যমথ ও ডাইনোসরের কথা বলেছেন যারা আকারে শক্তিতে বিপুল হয়েও আপাত ছোট শক্তির কাছে হেরে গিয়ে জগত থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। Personalityতে মেয়েদের feeble বলেও রবীন্দ্রনাথ এভাবে তাদের জোর স্বীকার করছেন ‘In the future civilization and the women, the feebler creatures, feebler at least in their outer aspects,-who are less muscular, and who have been behind hand, always left under the shadow of those huge creatures, the men,-they will have their place, and those bigger creatures will have to give way’। নারীর এই শক্তি রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী নব্যপুরাণের মূল কথা। (Raktakarabi)
মুদ্রিত ও ডিজিটাল মাধ্যমে সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ , বিশ্বভারতী। চর্চার ক্ষেত্র- রবীন্দ্রসাহিত্য ও বাংলার শিল্প।