(১)
‘স্মৃতি যেন ঠিক পুরোনো চড়ুই পাখি
নীল মাঠ থেকে উড়ে আসে জানালায়
খেলা করে ঘরে উঠোনে আলো ছায়ায়…’
বালিগঞ্জ ডাকঘরের ঠিক উলটোদিকের রাস্তায় একটা বহুতল আবাসন। সেখানে পাঁচ তলায় পুব-দক্ষিণ খোলা একটা বিশাল বড় ফ্ল্যাটে ইদানীং একাই থাকে দময়ন্তী। একটি বহুজাতিক সংস্থার যথেষ্ট উঁচু পদে কাজ করে সে। সারা দিনে চারপাশে মানুষজনের অভাব নেই; কিন্তু দিনের শেষে সে একা। প্রথম যৌবনে জীবন ছিল অন্যরকম। পড়াশুনোয় একটু বেশিই ভালো ছিল, জীবনে উচ্চাশাও ছিল নেহাত কম নয়; কিন্তু সেই সঙ্গে আর পাঁচটা সমবয়সী ছেলেমেয়ের মতো সে-ও ভালবাসার জন্য ছটফট করত, বিয়ে-থা করে সংসার করে দেখিয়ে দিতে চাইত মেয়েরা ইচ্ছে করলেই কেমন দশভুজা হতে পারে! কিন্তু বিধি বাম! তীক্ষ্ণ মেধার সঙ্গে ধারালো সৌন্দর্য যখন জুটি বাঁধে, সেদিকে চোখ পড়লে আশঙ্কা থাকে অন্ধ হয়ে যাওয়ার। সেই ভয়েই সম্ভবত বন্ধুত্বের চৌকাঠ পেরিয়ে কেউই তেমনভাবে তার হৃদয়ের ঘরে পা রাখার দুঃসাহস দেখায়নি; একমাত্র ঋজু ছাড়া। ঋজুর কথা মনে পড়তে ঠোঁটের কোণে হালকা হাসির ছাপ পড়ল দময়ন্তীর।
ঋজু। ওর পোশাকি নাম ছিল আনন্দরূপ। মেয়েদের স্কুলে পড়ত দময়ন্তী। মায়ের শ্যেনদৃষ্টি আর বাবার রাশভারী মেজাজের কারণে মাথা নিচু করে স্কুলে যাতায়াত করতে হত। সহপাঠিনীরা যখন চাপা গলায় পাড়ার বা বেপাড়ার দাদাদের কথা আলোচনা করত বা সদ্য-পাওয়া চিরকুট নিয়ে হাসাহাসি করত, তখনও ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকত সে। মাকে মোটেই বিশ্বাস নেই, হয়ত অদৃশ্য অবস্থায় থেকে মেয়ের হাবভাবের ওপরে নজর রাখছেন! তারপর যখন কলেজে ঢুকল, সহশিক্ষার দৌলতে সদ্য গোঁফ-গজানো একজন দু-জন সহপাঠীর সঙ্গে কিছুটা সখ্য জমল তার। তাদেরই একজন আনন্দরূপ। আঠেরো বছর পুরতে পায়ের নীচের জমি কিছুটা শক্তপোক্ত বলে বোধ হল যখন, মাকে লুকিয়ে আর বাবাকে এড়িয়ে একটু একটু করে স্বাধীন জীবনের স্বাদ নিতে শিখেছিল সে। অভিভাবকদের নজরদারি সামান্য শিথিলও হয়েছিল হয়ত; আর সেই ছিদ্রপথে এসেছিল আনন্দরূপ, ওরফে ঋজু। দময়ন্তীই বলেছিল, ‘তোর ভালো নামটা কেমন সিড়িঙ্গে লম্বামতো, তোর ঠিক যেমন তালঢ্যাঙা গড়ন! আমি বাপু তোকে ডাকনামেই ডাকব।’ জবাব উড়ে এসেছিল, ‘আর তোর নিজের নামটা? ওই তো পাঁচ ফুটিয়া টিংটিঙে চেহারা! দেখলেই মনে হয় পিঠে ভারী নামের বস্তা চাপিয়ে কুঁজো হয়ে হাঁটছিস!’ যৌবনের প্রগাঢ় সোনালি আলো সমস্ত শরীরে শুষে নিতে নিতে খিলখিল করে হেসে উঠে দময়ন্তী তখন বলেছিল, ‘একদম কমিয়ে বলবি না! আমি পাক্কা পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি! তুইও বরং আমাকে ডাকনামেই ডাকিস। আমার ডাকনাম মিতুল।’

সেই শুরু! তখন কথায় কথায় ঋজুর ওপরে খুচরো অভিমান হত খুব! ‘খুচরো’ শব্দটা এই মুহূর্তেই মাথায় এল তার, কারণ সত্যিকারের বড়োসড়ো অভিমান করতে সিলমোহর লাগে। সম্পর্কের সিলমোহর। ঋজুর সঙ্গে এক বিচ্ছিরি বেনামী অস্থায়ী সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তার। তাই সব অভিমান শেষ পর্যন্ত খুচরোই থেকে গেল! সেই অভিমানের গুরুত্বও দেয়নি কেউ। রাশি রাশি সম্পর্কের নৌকো ভেসে থাকা অতলান্ত জলে কালচে সবুজ একটুকরো শ্যাওলা হয়ে, সবজেটে ছায়া হয়ে রয়ে গেল ঋজু। আজীবন! যত ভালবাসা আর অভিমান টুকরো টুকরো ছেঁড়া কাগজ জুড়ে একা একাই তৈরি করেছিল দময়ন্তী। আজকাল যখনতখন সেইসব ধুলোবালি মাখা ছবিগুলো একে একে চোখের পাতায় উড়ে এসে জুড়ে বসে, হাতছানি দেয়। ঋজুর সঙ্গে ঝাঁ ঝাঁ দুপুরে মার্বেল প্যালেস দেখতে যাওয়া, হেমন্তের সন্ধেবেলায় সুভাষ সরোবরে জলের পাশে উঁচু ধাপিতে বসে ঘটিগরম খাওয়া, একসঙ্গে ফুচকা খেয়ে ঝালের চোটে হুশহাশ, সিগারেট কিনলে মিঠে পান তো কিনতেই হবে, তারপর বাড়ি ফেরার পথে একসঙ্গে পথবাতিদের ঝুরঝুরে হলুদ রেণু রেণু আলো দেখা… এইসব আর কী! সে একবার আবদার করে একটা ব্যাকক্লিপ চেয়েছিল ঋজুর কাছে। লাল টুকটুকে পলাশ ফুলের রং। বলেছিল, ‘যদি না দিস, তাহলে বুঝব পরশু কফিশপের জানলার বাইরে সেই যে জোড়া শালিখ ছিল বলেছিলি…ছাই! কক্ষনো দুটো শালিখ ছিলই না! একটাই ছিল। অন্যটা স্রেফ পাখিটার ছায়া!’
ঋজু কিনে দেয়নি ব্যাকক্লিপ। সুযোগও পায়নি। এমন কপাল, ওই দিনই ফেরার পথে বাবার গাড়িটা ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে গেল তাদের সামনে। বাবার গম্ভীর গলা এখনও কানে বাজে দময়ন্তীর, ‘মিতুল, গাড়িতে উঠে এসো এক্ষুনি!’ তারপর যা হয় আর কী! বাবা আর মা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া শুরু করে দিয়েছিলেন কার গাফিলতির জন্য মেয়ে জাহান্নমে গেল! অশান্তি এড়াতে কথা দিয়েছিল সে, বলেছিল ঋজুর সঙ্গে কোনও সম্পর্কে জড়াবে না।
নিজের মাথায় অজান্তেই হাত দিল দময়ন্তী। ব্যাকক্লিপের শখ বা প্রয়োজন ফুরিয়েছে বহু বছর। তার চুলে এখন পিক্সি ছাঁট। আর ঋজু? সেভাবে মনে পড়ে না, ঠিক কী করে সম্পর্কটা মরে গেল! হয়ত দময়ন্তীরই বোঝার ভুল! তারা কেউই পরস্পরের সঙ্গে তেমন করে জড়িয়ে পড়েনি; তাই বিচ্ছেদে একটু চিনচিনে কষ্ট থাকলেও আলাদা করে তেমন তীব্র যন্ত্রণার বোধ ছিল না!

দময়ন্তীর পড়াশোনার ব্যাপারে মায়ের যতটা উৎসাহ ছিল, প্রেম-ভালবাসায় ততটাই অনীহা। সত্যি বলতে কী, ঋজুর ঘটনার পরে দময়ন্তী বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মেলামেশাও করত খুব মেপেজুপে। যতটুকু না করলে বন্ধুরা তাকে একঘরে করে দেবে, ঠিক ততটুকুই। সে বুঝে গিয়েছিল, তাকে বাধ্য মেয়ে হতে হবে আর লক্ষ্মী মেয়েও। ঋজুর সঙ্গে দেখা হত কোনও কোনও জমায়েতে, টুকটাক কথাও হত; তবে ওই পর্যন্তই। আর ঋজুও তো সেভাবে ভালবাসার কথা বলে উঠতে পারেনি! এরপর আচমকা একদিন একটা নীল খাম এসেছিল দময়ন্তীর নামে। প্রেরকের নাম ছিল না। ভেতরে ফিকে নীল কাগজে আড়াআড়িভাবে সুন্দর ছবির মতো হাতের লেখায় দুটি ছত্র ছিল শুধু…
‘কানাকানি হোক, আরও বেশি কানাকানি হোক,
তুই আর আমি তো পুষ্পক বিমানে চড়ে অন্য দেশে চলে গেছি…’
ঋজুর হাতের লেখা খুব চেনা! দময়ন্তী ভেবেছিল উত্তর দেবে; পারেনি। অনেকগুলো কাগজ নষ্ট হয়েছিল সেই রাতে। খুব চেষ্টা করেছিল সে, মনের ঘেরাটোপ থেকে যদি অক্ষরগুলোকে মুক্তি দেওয়া যায়! হয়নি।
সব কথা সহজ আর সোজা করে লিখতে সকলে তো পারে না!
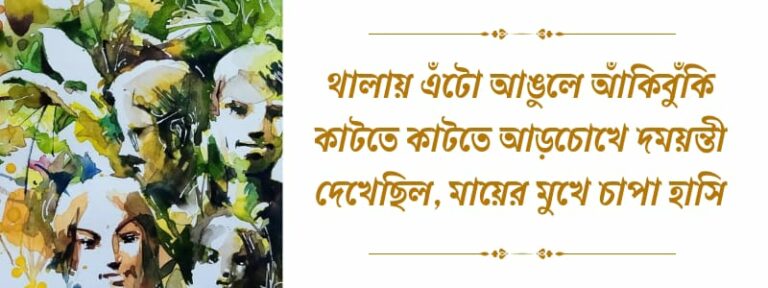
ঋজু মুছে গেল দময়ন্তীর দিনরাত্তির থেকে। লেখাপড়ার পাট মিটল যেদিন, বাবা খাবার টেবিলে ঘোষণা করলেন, ‘এবার মিতুলের বিয়ে দেব আমি।’
থালায় এঁটো আঙুলে আঁকিবুঁকি কাটতে কাটতে আড়চোখে দময়ন্তী দেখেছিল, মায়ের মুখে চাপা হাসি। তার মানে কর্তা-গিন্নি আটঘাট বেঁধেই মাঠে নেমেছেন!
নিরুপমাই কথা শুরু করেছিলেন সেদিন,
‘কই, বলো মিতুলকে, কেমন সম্বন্ধ এসেছে! আর একেবারে যেচে!’
অমলেশ স্ত্রীর কথায় সায় দিলেন, ‘হ্যাঁ মিতুল, আমার অনেক দিনের চেনা বরেনবাবুর ভাগ্নে। ছেলেটি চার্টার্ড অ্যাকাউনট্যান্ট, নিজের ফার্ম এই অল্পবয়সেই। কাজেকর্মে খুব সুনাম। দিল্লির বাসিন্দা ওরা। বাড়িতে বাবা, মা আর দাদা-বউদি। গ্রেটার কৈলাসে নিজেদের বাড়ি, তিনটে গাড়ি, হাসিখুশি আর সম্পন্ন পরিবার। আমার সঙ্গে ওঁরা বরেনের মারফত যোগাযোগ করেছিলেন। তোমার মায়ের সঙ্গেও ফোনে কথা বলেছেন। তুমি রাজি হলে আমরা এক্ষুনি এগোতে পারি।|’
উচ্ছ্বসিত গলায় নিরুপমা বললেন, ‘একেবারে আমাদের পালটি ঘর! ছেলেটি দেখতে শুনতেও দিব্যি! সব দিক থেকেই মনের মতো।’
ক্লান্ত লাগছিল খুব দময়ন্তীর। নিচু গলায় বলল, ‘সব তো নিজেরা ঠিক করেই ফেলেছ তোমরা! তাহলে আর আমার মতামত আসছে কোথা থেকে? শুধু একটাই কথা, আমি কিন্তু চাকরি পেয়ে গেলে সেটা নেব। আমার ওই একটাই ইচ্ছে।’
লাখ কথা চালাচালি হল না। দু-পক্ষই মুখিয়ে ছিল, তাই তড়িঘড়ি বিয়েটা হয়েই গিয়েছিল দময়ন্তীর। দু-বাড়িতে জাঁকজমকও কিছু কম হল না। দময়ন্তীর দাবি মেনে নিয়েছিলেন সকলে। তাই সে যখন নিজের যোগ্যতায় খোদ রাজধানীতেই একটা দারুণ লোভনীয় চাকরি পেয়ে গেল, সকলেই খুশি হয়েছিলেন। দময়ন্তী নিশ্চিন্ত হয়েছিল তার স্বামীর ব্যাপারেও। অনির্বাণকে নিয়ে অভিযোগের জায়গাই ছিল না তেমন। সব দিক থেকেই সব কিছু যেন একটু বেশি বেশিই ভালো! দময়ন্তী ডুবে গিয়েছিল নিজের পেশার জগতে যতটা, সংসারেও ঠিক ততটাই।
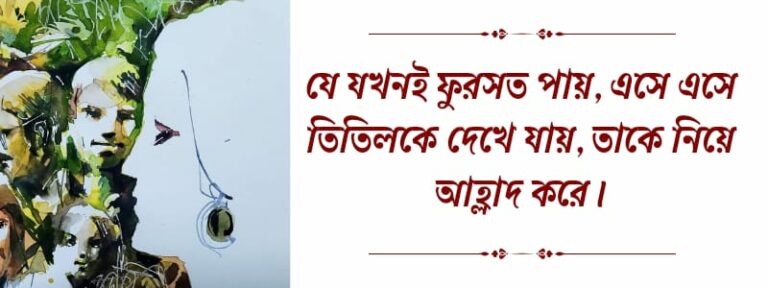
(২)
‘কাজের টেবিলে যার কথা ভুলে থাকি
তার কথা মনে সহসা ছবি সাজায়
স্মৃতি যেন ঠিক পুরোনো চড়ুই পাখি
নীল মাঠ থেকে উড়ে আসে জানালায়…’
যদিও অনেকগুলো বছর আগের কথা, তবুও চোখ বুজলেই মনে হয়, এই তো কিছুদিন আগেই একটা গাবলুগুবলু ফুটফুটে মেয়ে হল তার বড় জায়ের। বাড়িতে কত কাল পরে নতুন শিশু! দময়ন্তী তো যখনই অবসর পায়, টুক করে গিয়ে একটিবার দেখে আসে, কোলে নেওয়ার জন্য ছটফট করে। তবে বড্ড ছোট তো! ভয় পায় তাই। দিদিভাই বলেছিল, দময়ন্তী তো ছোট-মা! তাই নামও যেন ও-ই দেয়| অনেক ভেবেচিন্তে সে তাই নাম রেখেছিল ‘তপস্যা’, আর ডাকনাম ‘তিতিল’। তিতিলের দোলনা-খাটে উঁচু রেলিং, দু-পাশে পাশবালিশ দিয়ে দৃষ্টিসীমা বন্ধ, চোখ তুলে পিটপিট করে তাকায় যখন… শুধু সাদা ফ্যাকফ্যাকে সিলিং। বাড়ির পুরুষমানুষেরা কাজে বেরিয়ে যান, দময়ন্তীও চাকরিতে, তার শাশুড়ি-মা আর বড় জা সংসারে ব্যস্ত, কাজের লোকজনও সময় পায় কম। যে যখনই ফুরসত পায়, এসে এসে তিতিলকে দেখে যায়, তাকে নিয়ে আহ্লাদ করে। তিতিল কালো কাচের মার্বেলের মতো গুলি গুলি চোখ দিয়ে চেনা মুখগুলো খোঁজে, কান পেতে থাকে চেনা স্বর শোনার জন্য, কচি আঙুল দিয়ে আঁকড়ে ধরতে চায় চেনা আদর। একটু পরেই আবার ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা করে। তার সারাক্ষণের সঙ্গী হল দেওয়াল-ঘড়ির টিকটিক, লাল ঝুমঝুমি আর তুলোর কুকুরছানা।

মসৃণভাবেই চলছিল রোজের জীবন। তারপর সেই অন্ধকার দিন আর ছন্দপতন। বড়রা ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন খুব; সকলেই চাইছিলেন দময়ন্তীর সন্তান হোক। চার চারটে বছর তো কেটে গেছে, চাকরি ছাড়ারও দরকার নেই, বাড়িতে লোকজন নেহাত কম নেই, সকলে মিলে ঠিক ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এই তো, দেখতে দেখতে তিতিলও কেমন বড় হয়ে গেল! নিরুপমা আর অমলেশবাবুও ব্যাকুল হয়েছিলেন। দময়ন্তীরও তো অসাধ ছিল না! সে-ও চেয়েছিল তেমনটাই। কিন্তু চাওয়া আর পাওয়ার মধ্যে যে বিস্তর ফারাক, সেটাই বোঝেনি দময়ন্তী। সে বুঝতেই পারেনি, তার শরীরে কত বড় ওলটপালট হয়ে যেতে চলেছে!
কিছুদিন ধরেই খুব ক্লান্ত লাগছিল তার। মাঝেমাঝেই জ্বর আসছিল, পিঠের নীচে আর তলপেটে ঘিনঘিনে ব্যথা, খেতে বসে মনে হত পেটে আর জায়গা নেই, ওজন কমছিল দ্রুত, ঘনঘন বাথরুমে যাওয়ার দরকার পড়ছিল। অনির্বাণ নিয়ে গেল ডাক্তারের কাছে; ধরা পড়ল ডিম্বাশয়ে কর্কট রোগ থাবা বসিয়েছে; ছড়িয়েছে জরায়ুতেও। ডাক্তার কোনোরকম ঝুঁকি নিতে রাজি নন। সব কিছু ফেলে দিতে হল। তারপর কেমোথেরাপি, বিস্তর ওষুধপত্রে অবস্থা সামাল দেওয়া গেল বটে; কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মে মা হওয়ার পথ বন্ধ হয়ে গেল দময়ন্তীর। এমনিতে কর্কটরোগ সামলানো গেছে; তবে নিয়মিত পরীক্ষা করে খেয়াল রাখতে হবে। নিরুপমা আর অমলেশ কপাল চাপড়ালেন, অনির্বাণ গুম হয়ে গেল আর শ্বশুর-শাশুড়ি বেজার হলেন তাঁদের আদরের ছোট ছেলের জীবন খুঁতো হয়ে গেল বলে।
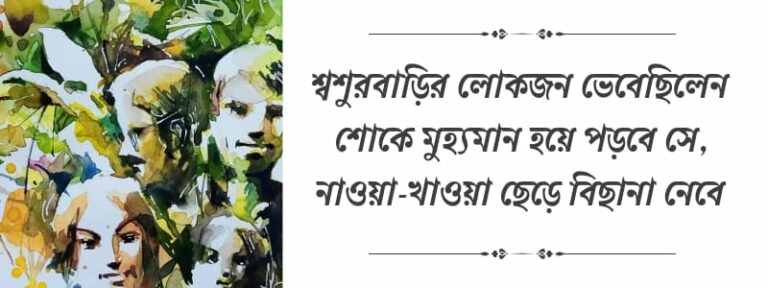
নিরুপমা আর অমলেশকে ডাকা হল দিল্লিতে। বসল গোলটেবিল বৈঠক। একটা কারণেই দময়ন্তী সামান্য হলেও কৃতজ্ঞ ছিল, শুধুমাত্র দু-তরফের বাবা-মায়েরাই তাতে উপস্থিত ছিলেন বলে। কী ভাগ্যিস, পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজনদেরও নেমন্তন্ন করে ডেকে এনে মতামত চাওয়া হয়নি! এমনকি তার ভাশুর আর জা-ও ছিল না সেখানে। অনির্বাণ উপস্থিত ছিল আর আসামির কাঠগড়ায় ছিল দময়ন্তী নিজে। প্রত্যক্ষভাবে দোষারোপ করা না হলেও এত অপরাধী মুখে বসেছিলেন অমলেশ আর নিরুপমা, দময়ন্তীর মনে হচ্ছিল সে নিজে যেমন সন্তানের জন্ম দিতে না পারার ব্যর্থতায় কষ্ট পাচ্ছে, সন্তানের জন্ম দিয়েও তার মা আজ একই রকম অসহায়তার শিকার।
অনির্বাণের মা-ই অবশ্য ছিলেন মুখ্য ভূমিকায়। অজস্র কথার পিঠে কথার মাঝে তাঁর একটি সংলাপ এখনও স্পষ্ট কানে বাজে দময়ন্তীর। ক্ষুব্ধ গলায় ঘোষণা করেছিলেন, ‘আপনাদের জন্য খারাপই লাগে, বুঝলেন বেয়ান! আমাদের তবু তিতিল আছে, হয়ত আরও একটি দুটি ভাই বা বোন আসবে তার। আপনাদের তো… এক তরকারি, দেখুন তো, কেমন নুনে বিষ হয়ে গেল!’
দময়ন্তীর ঠিক কেমন লেগেছিল সেদিন? খুব কষ্ট হয়েছিল! অসুখের ওপরে তো কোনও হাত থাকে না মানুষের; তবু নিজেকে বড় অসহায় মনে হচ্ছিল সেদিন। এই ব্যর্থতার বোঝা সে বয়ে নিয়ে চলতে পারবে তো সমস্ত জীবন? তারপর একটু একটু করে সব অপ্রাপ্তি, সব অসম্মান, সব অসহায়তা ঝেড়েঝুড়ে সামলে নিয়েছিল নিজেকে। ততদিনে চাকরি বদল করে অনেক বেশি টাকায় অনেক উঁচু পদে বসেছে সে; নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছে কাজের মধ্যে। হয়ত শ্বশুরবাড়ির লোকজন ভেবেছিলেন শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়বে সে, নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে বিছানা নেবে; কিন্তু তেমন কিছুই হল না। ছোট ছেলের ঘরের নাতিপুতির জন্য অনির্বাণের মা-বাবার হাহুতাশ শুনতে শুনতে অস্থির হয়ে যেদিন দময়ন্তী বন্ধ ঘরে অনির্বাণের কাছে দত্তক নেওয়ার কথা তুলল, সেদিনই হল বিস্ফোরণ। অনির্বাণ বলেছিল, ‘যার তার বাচ্চাকে নিজের বলে মেনে নিতে পারব না! অত উদার আমি নই, দময়ন্তী। আর আমার বাবা-মা কক্ষনও রাজি হবেন না। আত্মীয়স্বজনের কাছেই বা মুখ দেখাবেন কেমন করে? ওসব চিন্তা ছাড়ো। আমার কপালটাই মন্দ!’
তার পরেও তো দাঁতে দাঁত চেপে চেষ্টা করেছিল দময়ন্তী! বোঝাতে চেষ্টা করেছিল, সমঝোতায় আসতে চেয়েছিল। বড়রা না হয় আগেকার দিনের মানুষ, অনির্বাণ তো তা নয়! সে কি পারত না সকলকে বুঝিয়ে রাজি করাতে? এখন দময়ন্তী বুঝতে পারে, অনির্বাণের মনই উঠে গিয়েছিল দাম্পত্য থেকে! রোজ কথা কাটাকাটি, চাপানউতোর, একটা সময়ে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল দু-জনেরই। বেরিয়ে পড়েছিল নখ-দাঁত। তারপর নিজেরাই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যাতে পথ আলাদা হয়ে যায়।
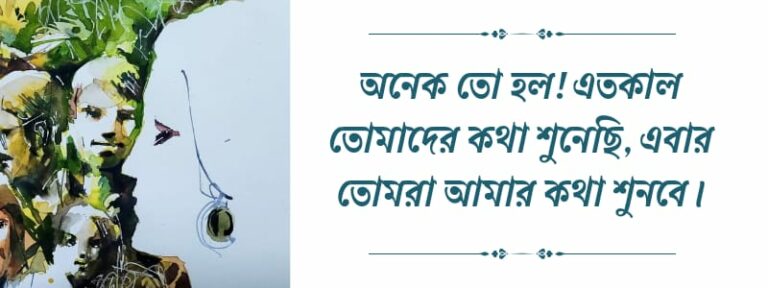
প্রায় সাত বছর বিবাহিত জীবন ছিল তার। তারপর আইনমাফিক সুতো ছিঁড়ল। কলকাতায় ফিরে এল দময়ন্তী, বদলি নিয়ে। সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, এবার থেকে একাই থাকবে। বাবা-মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে, একই শহরে যখন; কিন্তু ওই পর্যন্তই। আর কারও হাতে নিজের জীবনের রাশ ছেড়ে দেবে না। নিরুপমা কান্নাকাটি করেছিলেন, অমলেশও বিস্তর চেঁচামেচি; কিন্তু মেয়েকে বাগে আনতে পারেননি। স্পষ্ট গলায় এই প্রথম দময়ন্তী বলেছিল, ‘অনেক তো হল! এতকাল তোমাদের কথা শুনেছি, এবার তোমরা আমার কথা শুনবে। বাধ্য মেয়ে ছিলাম, এখন থেকে অবাধ্য হলাম। যদি বেশি বাড়াবাড়ি করো, চাকরি নিয়ে অন্য শহরে চলে যাব বা দেশের বাইরে। তখন কিন্তু একেবারেই কোনও যোগাযোগ রাখব না।’
আঙুলের কর গুনে হিসেব করছিল দময়ন্তী। মেঘে মেঘে বেলা হল ঢের। আজন্মের চেনা শহরে একা একা থাকার আট বছর পুরল। অবশ্য বছরে ক-টা দিনই বা কলকাতায় থাকে সে! দৌড়ে বেড়াতে হয় চতুর্দিকে, দেশে বিদেশে। সেইজন্যই প্রবল ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও কোনও শিশুকে দত্তক নিতে পারেনি; বাচ্চাটার প্রতি খুব অবিচার হত তাহলে। মনে মনে সঞ্চয়ের হিসেবও করছিল। অবসর নিয়ে একটা মস্ত বাড়ি বানাবে সে; শহরতলিতে। বাগান, পুকুর আর অনেকটা জায়গা নিয়ে। সেখানে তার আঁচলের তলায় আশ্রয় নেবে অজস্র অনিকেত শিশু। এখনও অনেকটা সঞ্চয় করতে হবে। সেইসঙ্গে বেঁচেও থাকতে হবে আরও বেশ কয়েকটা বছর।

কলকাতায় থাকলে এভাবেই সন্ধের পরে বারান্দায় এসে বসে থাকে সে; নিঝুম একা। টবের গাছে ফুটে থাকা ফুলেরা তাকে অভ্যর্থনা জানায়। লাগোয়া শোবার ঘরে নিয়ম করে নিচু সুরে বেজে যায় নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেতার বা আমজাদ আলি খান সাহেবের সরোদ। বৈঠকখানার কোকিল-ঘড়ি যেই জানান দেয় রাত ন’টা, অমনি তার কলকাতার বাড়ির দিনরাতের পরিচারিকা জানকী এসে দাঁড়ায় দরজার ফ্রেমে, ছবিটি হয়ে; ডাক দেয়, ‘খাবার গরম করি, দিদিজি?’
অবশ্য রোজই একইভাবে চটকা ভেঙে যায় দময়ন্তীর, সে যেখানেই থাকুক না কেন…হোটেলে, অতিথিশালায় বা নিজের বাড়িতে। তার জীবন এখন ঘড়ির কাঁটা ধরে আবর্তিত হয় নিত্যদিন। তার কাছে আগামীকাল মানেই আবার একটা নতুন সকাল, নতুন জীবন, নতুন করে সব কিছু শুরু করা।
রাতে খেতে বসার ডাক আসে যখন, তারপর রোজই হাতে এইভাবেই অবসর থাকে মিনিট কয়েকের। পৃথিবীর যেখানেই থাকুক, রোজই সেই চুরি করে পাওয়া সময়টুকুতে নিজের তলপেটে সন্তর্পণে হাত বোলায় দময়ন্তী। ফিসফিস করে নিজেকে আশ্বাস দেয়, শরীরে মা হয়ে উঠতে না পারলেও সমস্ত মনটুকু দিয়ে একদিন না একদিন সত্যিসত্যিই সে অনেকের মা হয়ে উঠবে।
প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় নিজের অদেখা, অচেনা, অজাত সন্তানের কাছে। একই সঙ্গে নিজের কাছেও। এত অনিশ্চয়তা, এত দুঃখ পার হয়ে এখন মনে হয় অন্ধকার সুড়ঙ্গ পেরিয়ে এভাবেই হয়ত আলোর দিকে এগিয়ে যাওয়া যায়। এইভাবেই হয়ত অহনার আলোয় ফুলের কুঁড়ি একটি একটি করে পাপড়ি মেলে ধরে। এখন আর খাদের পাশে দাঁড়াতে একটুও ভয় পায় না দময়ন্তী। তার পিঠে পাখির ডানা।
উঠে দাঁড়াল দময়ন্তী। দু-চোখ বন্ধ করে নির্ভার মনে হাত বাড়িয়ে দিল তারাভরা আকাশের দিকে। অনন্তের দিকে।
(গল্পের দুটি পর্বের শুরুতে ব্যবহৃত অংশ-কবিতা-ঋণ : পুরোনো চড়ুই/ শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়)
অলঙ্করণ: শুভ্রনীল ঘোষ
ছবি সৌজন্য: Adobe stock, Stockvault
ইলেকট্রনিক্সের ছাত্রী ঈশানী রায়চৌধুরী তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে ভাষান্তরের কাজে যুক্ত। নিজস্ব লেখালেখির মাধ্যম হিসেবে সবচেয়ে পছন্দ রম্য গদ্য আর ছোট গল্প | আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, ফ্রিডা কাহলো, খলিল জিব্রান, আর কে নারায়ণ প্রমুখ লেখকদের কাজ ভাষান্তর করেছেন। 'কৃষ্ণচূড়া আর পুটুস ফুল', 'আবছা অ্য়ালবাম', 'বাবু-টাবুর মা', ওঁর কয়েকটি প্রকাশিত বই।


























4 Responses
খুব বাস্তব জীবনের সাথে মিল۔۔ খুঁজে পেলাম۔۔۔ সব মিলিয়ে ভীষণ মন ছুঁয়ে যাওয়া গল্প۔۔۔
Sesh hoye o roye gelo resh
খুব ভালো লাগলো তবে এর আগে দময়ন্তী প্রতিবাদ করলে ভালো হতো।এত পড়াশোনা করেও তার নুইয়ে থাকাটা মানতে অসুবিধে হচ্ছে।
ঝকঝকে গদ্য। টানটান গল্প।