হাজরা রোডে থাকতে এসে দেখা গেল, আত্মীয়স্বজনরা অনেকেই কাছেপিঠে। তাঁদের অ-পূর্বঘোষিত যাওয়া আসা লেগেই থাকত। আমরাও বেড়িয়ে আসতাম তাঁদের বাড়ি। দরজায় বেল ছিল না। কালচে সবুজ রঙের আমকাঠের দরজায় লাগানো লোহার কড়া। একটু নীচের দিকে বলে কেউ কেউ সেটা ঠাহর করতে না-পেরে দরজায় দুম দুম করাঘাত বা পদাঘাত করত। দরজা পাছে ভেঙে যায়, তাই ছুতোর ডেকে আরও একজোড়া কড়া লাগানো হয়েছিল ওপরের দিকে। কিন্তু লোহার ওপর পালিশ ভাল হয়নি বলে তার আওয়াজ কাঠের উপর ভাল ফুটত না। ফলে তাকে বাজানোই হয়নি বেশি।

আমাদের মতো মধ্যবিত্ত অনেক বাড়িতেই তখন ফোন ছিল না। সিনেমায় দেখা যেত, ভারী কালো অথবা ধাতব স্টাইলিশ ফোন তুলছেন কমল মিত্র বা উত্তমকুমার। আমাদের জীবনে ফোনের কোনও ভূমিকা ছিল না। আগে থেকে না-জানিয়েই লোকজন আসতেন। ‘এই সময়ে কেন এল’ বলে মুখ পাঁচ করার প্রথা বাঙালি জীবনে আরম্ভ হয়েছিল সম্ভবত টেলিভিশন আসার পর। শৈশবে দরজা খোলার দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলাম আমি। লাফাতে লাফাতে গিয়ে দরজা খুলে, ‘মা, দাদু এসেছে’, ‘পিসি এসেছে’, ‘জ্যাঠা এসেছে’ বলে ঘোষণা করতে আমার ভালই লাগত।
[the_ad id=”266918″]
এমনও হয়েছে, দুপুরবেলা থালায় গরম ভাত বেড়ে আমরা খেতে বসছি, এমন সময় কড়া নড়ে উঠল। বেহালা থেকে ছেলেমেয়ে নিয়ে বড়মাসি, কিংবা শিয়ালদহ থেকে ছোটকাকা-কাকিমা। পড়ে রইল ভাত, বেড়ে দেবার অপেক্ষায় ক্ষুধার্ত ছেলে-মেয়ে-স্বামী। মা হেসে হাত ধুয়ে আধঘোমটা টেনে গল্প করতে চলে গেলেন। ‘ওরে তুই খেয়ে নে’, ‘বউদি তোমরা খেয়ে এস না’, ইত্যাদি কথার উত্তরে মা বলতেন, ‘আচ্ছা সে হবে’খন, খাওয়া কি পালিয়ে যাচ্ছে নাকি!’
বাবা আমাদের মাছ-তরকারি বেড়ে তাড়াহুড়ো করে খাইয়ে দিলেন হয়তো। এখন আমাদের পরিমণ্ডলে না-জানিয়ে কেউ বাড়িতে এসেছে, ভাবাই যায় না! একুশ শতকে আমরা এতই সুশীতল, ভদ্র, যে কাউকে সোজাসুজি ফোনও করি না। আগে হোয়্যাটসঅ্যাপ করে সময় জেনে নিই। অতিথি এলেও বাড়ির ছোটরা নিজেদের ঘরে আইপ্যাড, ফোন, ল্যাপটপে ডুবে থাকতে পারে। তাদের কাছ থেকে সামাজিকতার প্রত্যাশা করা হয় না।
[the_ad id=”266919″]
কিন্তু আমাদের সময় আত্মীয়দের আসা মানে অনেকটা সময় পড়াশুনো বন্ধ। বাড়িতে লোকজন আর তুমি বই মুখে বসে আছ, তা-ও আবার হয় নাকি! তাছাড়া ছুট্টে গিয়ে সিঙাড়া মিষ্টি ইত্যাদি নিয়ে আসা, অথবা মায়ের সঙ্গে হাত মিলিয়ে লুচি আলুরদম তৈরি করে প্লেট সাজিয়ে দেওয়া… কেনা মিষ্টি না গরম জলখাবার, সেটা নির্ভর করত অতিথি সপরিবার এসেছেন, না একা। প্রায়ই আসেন, না অনেকদিন পর এসেছেন, তার উপরও। এ নিয়মের একমাত্র ব্যতিক্রম আমার ছোটপিসি, যিনি সপ্তাহে দু’তিনবার আসতেন। পিসি আসতেন যেখান থেকে, আদি শৈশবে সেই জায়গাটাকে বলতাম ‘মই মালদার থীত।’ মহিম হালদার জানতে পারলে তাঁর নামাঙ্কিত রাস্তার এই অবনমন কীভাবে সইতেন জানি না।

কাছেপিঠের আত্মীয়স্বজন সবাই পায়ে হেঁটেই যাওয়া আসা করতেন। বেহালা, শিয়ালদহ, দক্ষিণেশ্বর থেকে হলে বাসে-ট্রামে। গাড়ি-বাহন কেউ আমাদের নিকট বলয়ে ছিলেন না। তা নিয়ে কারও কোনও মাথাব্যথাও দেখিনি। স্বামী, ছোট ছেলে, শ্বশুর-শাশুড়ি-ভাসুর-দেওর-ননদ সবাইকে নিয়ে পিসির ঠাসাঠাসি জীবন। মায়ের সঙ্গে পিসির দারুণ বন্ধুত্ব ছিল। কারণ বিয়ে হয়ে এসে চোদ্দো বছরের বউ পনেরো বছরের ননদকে সঙ্গী হিসেবে পেয়েছিলেন। দু’জনে একসঙ্গে বসলে পিসি একটু আধটু দুখ্খু করতেন শ্বশুরবাড়ি নিয়ে, যেটা বাপের বাড়ি আসা মেয়েরা করেই থাকে। পিসির কাছে মা অবশ্য নিজের শ্বশুরবাড়ির নিন্দে করতে পারতেন না। পিসি এলেই বিকেলে লুচি, সঙ্গে তরকারি বা সুজির পায়েস। তার একটা কারণ, পিসিকে নিমিত্ত করে আমাদের খাওয়াদাওয়া।
মা আর ছোটপিসি গল্পে মশগুল হয়ে গেলেই আমি চুপচাপ রান্নাঘর থেকে খাবার জায়গার মেঝেতে পাতিয়ে রাখব পিতলের স্পিরিট স্টোভ, লোহার কড়াই, লুচি ভাজার চাকি-বেলন, ময়দা, জলের ঘটি, এবং সর্বোপরি, শ্রী ঘৃতর লাল রঙের টিন। পিসি লুচি বেলছেন এবং মা ভাজছেন— এক মনোরম দৃশ্য।
[the_ad id=”270084″]
লুচি ভেজে একফোঁটাও তেল বেশি হত না, মায়ের আন্দাজ ছিল এমনই নিপুণ। বাংলার বাইরে পূর্ব ও উত্তর ভারতে যতবারই ময়দার লুচি খাওয়ার বাসনা প্রকাশ করেছি, ততবারই প্রমাদ গুণেছি। একে তো ময়দা এমন দানবীয় চূর্ণ যে, লেচি যতই বেলে বড় ও গোল করার চেষ্টা কর, সে ছোট ও লম্বাটে হয়ে আসে। তার উপর ভাজার তেলের বহর দেখলে মনে হয় তেলকলের মালিকের বাড়িতে এসেছি। এক দেড় লিটার তেল না কলকলালে এঁরা ভাজার পিঁড়েতে বসতে নারাজ।
ব্যতিক্রম মহারাষ্ট্র। তেল, লবণ থেকে বাক্য, সবতাতেই তাদের যুদ্ধকালীন সংযম। শ্বশুরবাড়িতে প্রথমবার আমার বেগুনভাজার জন্য তেল ঢালার মহড়া দেখে আত্মীয় মহিলারা বিমর্ষ হয়ে পড়ে বলেন, ‘এত তেল? আমাদের বাপু বেগুনভাতেই ভাল।’ আটার লুচি, যা সারা দেশে ‘পুরী’ উপাধি পেয়েছে, মহারাষ্ট্রে তা হল উৎসব ও বিয়েবাড়ির ভোজ। কিন্তু নিত্যকার জীবনে এত তেলের খরচ মারাঠীরা ভাবতেই পারে না। এরা পাতে লবণ দেয় এক চিমটে, (আমাদের মত এক খাবলা নয়!) বলে, ‘লাগলে বোলও, আবার দেব।’
যাইহোক, শৈশবের সেই ছোট্ট কড়াইতে ঘি শেষ হত শেষ লুচিটিতে এসে। নিখুঁত হিসেব। শেষ লুচিটি ছিল সবচেয়ে নির্যাতিত ও পোড় খাওয়া। ঘি কম থাকায় কড়াইয়ের দেওয়ালে তাকে মেরে পিটে ঠেসে রাখা হত। লাল ও মচমচে বলে ওইটা আমি পেতাম, বড় দানার চিনি দিয়ে খাওয়ার জন্য।
[the_ad id=”270085″]
দেখুন, আত্মীয়স্বজন থেকে লুচি ভাজায় চলে এলাম। বাঙালি আর কারে কয়! আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে খুব কাছে থাকতেন মেজ জ্যাঠা আর জ্যেঠিমা। আমাদের উল্টোদিকে যে ময়লাটে হলুদ চারতলা বাড়িটা ছিল, গোড়ায় ওঁরা সেখানেই থাকতেন। ও বাড়ির অন্য পড়শি আর জ্যেঠিমার কাছে ছিল আমার বিকেলবেলার দস্যিপনার জায়গা। ১৯৪৬-এ, দেশভাগ হবার আগের বছরই মেজ জ্যাঠা আর বাবা খুলনা থেকে কলকাতায় চলে এসে বাসা করেছিলেন। পার্টিশনের পর মাস তিনেক খুলনা জেলা ভারতেই অংশ ছিল। তারপর ১৯৪৭-এই বসতবাড়ি, পুকুর, সামান্য জমিজমা ছেড়ে ঠাকুরদা-ঠাকুরমা কলকাতায় চলে আসেন, কনিষ্ঠ পুত্রকন্যাদের নিয়ে। ওই বাসাটুকু না-থাকলে রিফিউজি কলোনিতেই জীবন আরম্ভ করতে হত সবাইকে।
কলকাতায় জমি-বাড়ি কিছুই ছিল না। বাবা-জ্যাঠা দু’জনে সরকারি চাকরিও পেয়ে যান কাছাকাছি সময়ে। সেই চাকরির সূত্রে জ্যাঠা একসময়ে থাকতেন ডোভার লেনের সরকারি কোয়ার্টারে। জ্যাঠার গলা ছিল ল্যারিঞ্জাইটিসের কারণে ফ্যাঁসফেসে, কষ্ট করে শুনতে হত। হাসিটি কাষ্ঠবৎ। তিনি কড়া মানুষ, না ভাল, সেটা বুঝতে পারতাম না। তাই জ্যাঠা এলেই আমি দু’নম্বর ঘরে আলমারির পিছনে লুকিয়ে পড়তাম। বেড়াতে যাওয়া ব্যাপারটা আমাদের ছোটবেলায় একটা স্বাভাবিক আনন্দ ছিল। মাঝেই মাঝেই এ-ওর বাড়ি যাচ্ছে। ছোটদের খুব মান্যিগণ্যি করা হত না, চাইল্ড সাইকোলজির চর্চা তো বহু দূর।
[the_ad id=”270086″]
চাটুজ্জে বাড়ির ছোট জামাই, আমাদের ছোট পিসেমশাই ছিলেন আমুদে প্রকৃতির। বাড়ির ছেলেদের (মেয়েদের কদাপি নয়) জুটিয়ে ফুটবল খেলা দেখাতে নিয়ে যেতেন, চিনাবাদাম খাওয়াতেন, ওপারের ফুটপাথ ধরে বাড়ি যাওয়ার সময় ‘ও সেজবৌদি, কেমন আছেন’ বলে রাস্তা থেকেই একটা হাঁক দিয়ে যেতেন। পিসিমার ভাসুরও মাঝে মাঝে চলে আসতেন। তাঁর ভাষা ছিল ফরিদপুরের, মাঝে মাঝে অট্টহাস্য। কাজ করতেন ডাকঘরে আর টিউশন পড়াতেন। একদিন এসে বললেন, ‘রেডিও খোল দেখি, আজ সুমন গাইবে। আমার ছাত্র।’ গল্পদাদুর আসর ছিল কি সেটা? পনেরো বছর বয়সের সুমন চট্টোপাধ্যায়ের গান শুনলাম, ‘তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী।’ মুগ্ধ হলাম। সে মোহ আজও ছাড়েনি।

ন’কাকুর মেয়ে শুভা আমার খুব বন্ধু ছিল। চেতলা রোডের বাসা বদল করে, হাজরার খুব কাছে সদানন্দ রোডে চলে এলেন ন’কাকু কাকিমা, পূর্ণচন্দ্র ঘোষের মিষ্টির দোকানের উল্টোদিকে। পূর্ণচন্দ্র মায়ের অনুমোদিত আউটলেট, প্রায়ই ওখানে মিষ্টি বা সিঙাড়া আনতে যেতাম। একদিন এক চিল ছোঁ মেরে ছোড়দার হাত থেকে কচুরির ঠোঙা নিয়ে চলে গেল। কাঁদো কাঁদো হয়ে ছোড়দা বাড়ি এল। কাকেদের তুলনায় চিলকে আমরা রহস্যময়, দূর গগনের পাখি বলেই জানতাম। মাঝদুপুরে তার চিল্লি চিল্লি ডাক কতবার আমার শিশুমনকে আকুল করে তুলেছে। হঠাৎ করে সেই চিলের এত কাছে নেমে এসে ডানার ঝাপট ও ঠোঙায় ছোঁ, বেচারা ছোড়দা সামলাতে পারেনি। আমাদের জলখাবার তো মাঠে মারা গেলই, কিন্তু পূর্ণচন্দ্রের কচুরি খেয়ে চিলের কী হয়েছিল জানা যায়নি।
কলকাতায় জন্ম, বড় হওয়া। অর্থনীতির পাঠ প্রেসিডেন্সী কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কবিতা দিয়ে লেখক জীবন আরম্ভ। সূচনা শৈশবেই। কবিতার পাশাপাশি গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী, প্রবন্ধ, ছোটদের জন্য লেখায় অনায়াস সঞ্চরণ। ভারতীয় প্রশাসনিক সেবার সদস্য ছিলেন সাড়ে তিন দশকেরও বেশি সময়। মহুলডিহার দিন, মহানদী, কলকাতার প্রতিমা শিল্পীরা, ব্রেল, কবিতা সমগ্র , দেশের ভিতর দেশ ইত্যাদি চল্লিশটি বই। ইংরাজি সহ নানা ভারতীয় ভাষায়, জার্মান ও সুইডিশে অনূদিত হয়েছে অনিতা অগ্নিহোত্রীর লেখা। শরৎ পুরস্কার, সাহিত্য পরিষৎ সম্মান, প্রতিভা বসু স্মৃতি পুরস্কার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুবন মোহিনী দাসী স্বর্ণপদকে সম্মানিত। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমীর সোমেন চন্দ পুরস্কার ফিরিয়েছেন নন্দীগ্রামে নিরস্ত্র মানুষের হত্যার প্রতিবাদে। ভারতের নানা প্রান্তের প্রান্তিক মানুষের কন্ঠস্বর উন্মোচিত তাঁর লেখায়। ভালোবাসেন গান শুনতে, গ্রামে গঞ্জে ঘুরতে, প্রকৃতির নানা রূপ একমনে দেখতে।











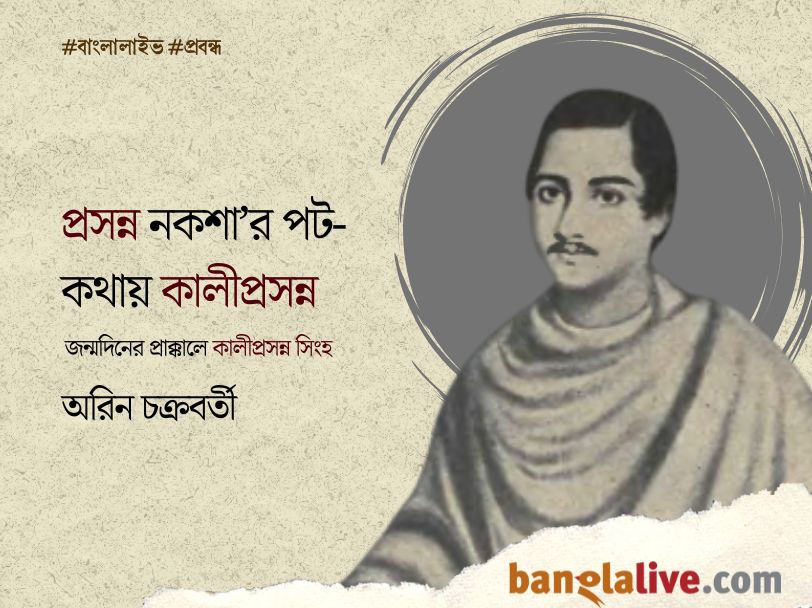













3 Responses
খুবই ভালো লাগছে। সব মিলে গেলে রিলেট করবার সুবিধে হয় বৈকি। আর ভাষা… অনবদ্য, নির্মেদ, প্রাঞ্জল।
এক বিশেষ কারণে ভালো লাগার পরিধিটা সঠিক ব্যাখ্যা করতে পারব না। তবে পড়তে পড়তে মাঝেই মাঝেই শৈশবে হারিয়ে যাচ্ছি।
অসাধারণ