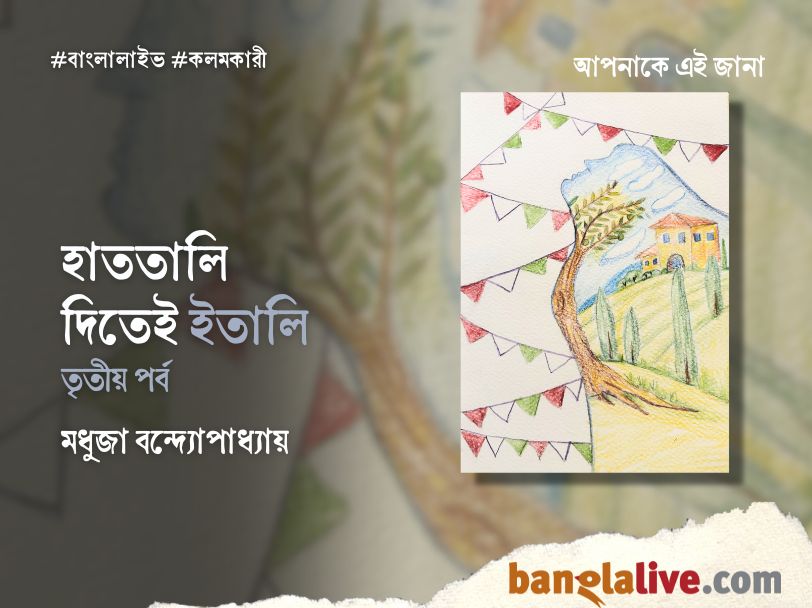(Column)
হলুদ আর সর্ষের তেল দিয়ে ভাজা টাস্কানির নদীর মাছ, সঙ্গে সোনা মুগ ডাল আর মুরগির লাল-লাল ঝোল, গরম ভাতের গ্রাসে মনে হল বাড়ি ফিরে এসেছি যেন। তারপর দলের অনেকেই ঠিক করল ইতালির মাসিমার রান্না না খেয়ে বাংলাদেশী ভাইদের হাতে তৈরি দেশের খাবার খাবেন। (Column)
অল্প আলো আর অনেকটা ছায়ায় এক মায়াবী পরিবেশ তৈরি হয়েছে— আমরা সবাই কেমন একটা ঘোরের মধ্যে চলে গেছিলাম সেদিন। ঘোর ভাঙল দারুণ দারুণ খাবারের গন্ধে।
এক শুক্কুরবার স্প্যাশিওতে পটলাক পার্টি হল। অর্থাৎ প্রত্যেকেই কিছু না কিছু খাবার আনবে আর তা সবাই মিলে ভাগ করে খাওয়া হবে। ওইদিন ইউরোপের নানা দেশ ও আশেপাশের অঞ্চল থেকে বিভিন্ন ধারার শিল্পী আসেন— খাবারের সঙ্গে সঙ্গে ভাগ করে নেন নিজের শিল্পও। এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। আমরা ছাড়াও সেদিন হলঘরে জড়ো হয়েছেন আরও পনেরোটি দেশের শিল্পী। কেউ পিয়ানো বাজাচ্ছেন, সেই তালে কেউ নাচছেন— এই নাচ ঠিক কাউকে দেখানোর বা মন ভোলানোর জন্য নয়, নিজের মনে নাচ, আর একইভাবে কেউ দূরে বসে ছবি এঁকে চলেছেন আপনমনে। আমাদের দলেরও অনেকে সেখানে অংশ নিলেন। আমারও খুব ইচ্ছে করছিল কিন্তু তখনও আমার শরীরে মনে যথেষ্ট জড়তা ছিল— নিজেকে প্রকাশ করার ইচ্ছে ছিল কিন্তু সাহস ছিল না। কিন্তু নিজেকে খুব সৌভাগ্যবান মনে করেছিলাম। আজও আমি অবন্তীর কাছে ঋণী, ওর সঙ্গে না এলে আমি কোনওদিনই এই আশ্চর্য ঘটনার সাক্ষী হতে পারতাম না। সন্ধ্যে থেকে রাত হয়ে আসছে— নাচ ও গানের গতি বেড়েই চলেছে— অল্প আলো আর অনেকটা ছায়ায় এক মায়াবী পরিবেশ তৈরি হয়েছে— আমরা সবাই কেমন একটা ঘোরের মধ্যে চলে গেছিলাম সেদিন। ঘোর ভাঙল দারুণ দারুণ খাবারের গন্ধে। ইউরোপের নানা দেশের খাবার— সেসব বাড়িতে রান্না, সব নামও জানি না, কোনওটা ভাত, মাংস, সব্জি দিয়ে বানানো, কোনওটায় আছে টাটকা অলিভ, চিজ আর আছে নানা রকমের রুটি। আমরা ঠিক করেছিলাম ইউরোপীয়দের পাঁঠার মাংস, ডাল, ভাত খাওয়াব। (Column)

বাংলাদেশীদের আস্তানা থেকে সে খাবার বড় ডেকচিতে পৌঁছে গেল সময়মতন। কিন্তু আমাদের মধ্যে যাদের ভাত ছাড়া চলে না, তাদের কপালে জুটল না সে খাবার। তার আগেই তা চলে গেল ইউরোপীয়দের পাতে। প্রায় হাঁড়ি চেঁচে খাবার মতো নিমেষে শেষ হয়ে গেল বাঙালি খাবার। পড়ে থাকল চিজের টুকরো, কিছু রুটি আর স্যালাড! (Column)
আরও পড়ুন: হাততালি দিতেই ইতালি: প্রথম পর্ব
টাস্কানি বিখ্যাত ভিনিয়ার্ডের জন্য। মালভূমি অঞ্চলে বৃষ্টি হলেও জল দাঁড়ায় না। আঙুরের চাষ দারুণ হয়। স্প্যাশিও থেকে ফেরার পথে এক ক্যাফেতে একলা বসে ওয়াইন খেতে খেতে ছবি এঁকেছিলাম, যা ছিল আমার বহুদিনের ইচ্ছে। সাদা মিষ্টি ওয়াইনে চুমুক দিতে দিতে রঙ পেন্সিলে আঁকিবুকি কেটে চমৎকার কাটল একার সময়— বিপদ হল বিল দিতে গিয়ে। যেখানে বসেছিলাম সেখানে আমার নতুন কেনা সৌখিন হলুদ জ্যাকেট রেখে গেছি ক্যাশ কাউন্টারে। এসে সে জ্যাকেট তুলতে গিয়ে মহা ঝামেলায় পড়লাম। সুবেশা তিন ইতালিয়ান মহিলা ক্যাফে মালিককে আমার দিকে তাকিয়ে কী সব বললেন! ক্যাফে মালিক বললেন জ্যাকেটটা যে আমার তার প্রমাণ কী? কী প্রমাণ আছে যে আমি বাংলাদেশি চোর নই! থতমত খেলাম— রাগ হল, দুঃখও হল। শেষে পাসপোর্ট আর মোবাইলে ওই জ্যাকেটটি পরা আমার ছবি দেখিয়ে মুক্তি পেলাম। জীবনে সেই প্রথম বর্ণবিদ্বেষ অনুভব করলাম। এও এক আত্মানুসন্ধান বইকী! (Column)

এই সব কিছুর পরও মন ভাল থাকত, আবার পরের দিন ওয়ার্কশপে যাব ভেবে। রোজই সেখানে নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করতাম। একদিন বলা হল চোখ বেঁধে হাঁটতে। হাঁটতে হাঁটতে কারের সঙ্গে ধাক্কা লাগলে তাকে হাত ধরে অভিবাদন জানাতে আর জড়িয়ে ধরতে মানে যাকে Hug বলে আর কী। এ হেন প্রস্তাবে আমার প্রথমে বেশ জড়তা ছিল। কিন্তু চোখ বাঁধার পর যেন এক অচেনা জগতে চলে গেলাম। প্রথমে চারিদিকে অন্ধকার। দমবন্ধ পরিস্থিতি তারপর দেখলাম বড় জানলা দিয়ে হলে যে সোনালি রোদ পড়ে তার উত্তাপ বুঝতে পারছি— সেই উত্তাপের অনুভূতির রাস্তা ধরে একটু একটু করে এগোতে থাকলাম, ধাক্কা খেলাম— কেউ হাত ধরেই ছেড়ে দিল, কেউ আবার অনেকক্ষণ হাত ধরে হাগ করল, কেউ বা কেজো হাগ করে চলে গেল— আলোর উত্তাপ পায়ের পাতায় এসে ঠেকছিল। বুঝছিলাম হলের জানলা মানে আলোর দিকে চলে এসেছি। অনেকক্ষণ সেই আলো গায়ে মেখে বসে থাকলাম। আর ভাবলাম একটা হাঁটা যেন সম্পূর্ণ জীবনদর্শন। কত মানুষ আসবে, যাবে, ভালবাসবে, হাত ধরবে, হাত ছাড়বে, কেউ স্বেচ্ছায় চলে যাবে, কেউ বা চলে যেতে হবে বলে এগিয়ে যাবে আর এই এগিয়ে যাওয়াটা যেন নিজেকে জানার, অন্ধকার থেকে আলোয়, অজানা থেকে জানার— মনে পড়ে গেল
ছোটবেলায় স্কুলে শেখা “অসতো মা সৎ গময়ঃ।
তমসো মা জ্যোতির্গময়ঃ॥”
কথালয়া – কথার জন্ম হয় যেখানে : মধুজা বন্দ্যোপাধ্যায়
এই যাত্রা তাই শুধু শরীরে জড়তা মুক্তির যাত্রা নয়, নিজেকে জানার আর জীবনের সত্যকে উপলব্ধি করার যাত্রা।
এর পরে আমাদের শেখানো হয়েছিল ঠিক করে শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া। যে কোনও Creative Workshop-এই আমি দেখেছি শেখানো হয় নানা ভাবে নিঃশ্বাস নেওয়ার পদ্ধতি। কিন্তু জিয়ানির প্রতিটি শেখানোর পিছনে যে কারণ বলতেন সেটা মনে গেঁথে যেত। জানতে পারলাম মানুষের অন্যতম সংবেদনশীল অঙ্গ হল তার পেট। মেয়েদের ক্ষেত্রে এটি আরও গুরুত্বপূর্ণ কারণ সেখানে আরও একটি প্রাণের সৃষ্টি হয়। কিন্তু ইউরোপে বার বার মেয়েদের পেটকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখা হত সৌন্দর্য ও ভদ্রতার নামে। কখনও গাউনের পরতে কখনও বা কর্সেটের দড়ির ফাঁসে। ফলে নাভি থেকে যে শ্বাস উঠে আসে তা কখনই তারা নিতে পারত না। ভাবলাম, তুলনায় আমাদের দেশ অনেক বেশি প্রগতিশীল ছিল। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রাচীনকাল থেকে যে বস্ত্র পরা হয় তাতে পেট ঢাকা থাকে না। কোনও এক জায়গায় শুনেছিলাম, এর এক বৈজ্ঞানিক কারণ হল যাতে নাভি দিয়ে শরীরে সূর্যের উত্তাপ প্রবেশ করে। জিয়ানি শেখালেন কী করে পেট থেকে শ্বাস নিতে হয়। সম্পূর্ণ পাঁজরে সেই শ্বাস ভরে তারপর ছাড়তে হয়। এতে দেখলাম শরীরটা ঝরঝরে লাগল, নির্ভার মনে হল নিজেকে। এভাবে যখন মনের মধ্যেটা ফুরফুরে লাগছে অবন্তী আমাদের নিয়ে গেল এক কঠিন দুঃখের জগতে, যার নাম Gravyard Talk মানে মৃত মানুষের সঙ্গে কথা বলতে হবে। যার সঙ্গে অনেক অশান্তি, না বলা কথা ছিল তা বলে নিজেকে শান্তি দিতে হবে। আমি তখনও জীবনে খুব প্রিয়জনের চলে যাওয়া দেখিনি আমার দিদা বা দিম্মা ছাড়া। দিম্মা প্রায় দশ বছর ডিমেনশিয়ায় ভুগে সম্পূর্ণ এক অচেনা মানুষ হয়ে চলে গেল। কিন্তু যাঁকে আমি চিনতাম, স্মৃতি চলে যাওয়ার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। (Column)

আমি মনে করার চেষ্টা করলাম দিম্মার সঙ্গে এমন কী না বলা কথা ছিল যা আজও আমাকে তাড়িয়ে বেড়ায়? মনে পড়ল, আমার দিম্মা দশ বছর ডিমেনশিয়ায় ভোগার আগের পাঁচ বছর, মূলত সেই সময় আমি কলেজে পড়ি- বার বার বলত অন্তত মাসে একবার তার কাছে যেতে। ফোন করে কৌতূহলে দিম্মা জানতে চাইত কী কী পড়ানো হচ্ছে। কী কী বই নিয়ে আলোচনা হচ্ছে? কোন বিষয়ে সেমিনার চলেছ। নতুন বন্ধুদের আড্ডা-উত্তেজনা ঠেলে হয়তো সে সময় দিম্মার ডাকে সাড়া দিতে পারিনি। মনে মনে দিম্মাকে সে কথাই বলেছিলাম। কিন্তু আমার আর দিম্মার সেই কাল্পনিক কথোপকথনে ছিল শান্তি আর অনেক ভালবাসা। কোথাও একটা ভারমুক্ত লাগছিল নিজেকে। আমাদের দলে বেশিরভাগই পেশাদার অভিনেতা। তাদের কথোপকথন দেখে অভিনয়ই মনে হচ্ছিল— মনে হয়নি মন খুলে তাঁরা হারিয়ে যাওয়া প্রিয় মানুষটির সঙ্গে কথা বলছেন। শুধু একজন ছাড়া। আজও তাঁর কথোপকথন চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে। তিনি প্রতিষ্ঠিত, শিক্ষিত সুন্দরী এককালের প্রথম সারির অভিনেত্রী। কাল্পনিক কথা বললেন মৃত মায়ের সঙ্গে। সে কথায় কী যন্ত্রণা। বারবার ছোট মেয়ের মতো আকুলি-বিকুলি কেঁদে তিনি বলে চলেছেন আমাকে কি একটা দিনের জন্য সুন্দর বলতে পারতে না? ‘একটা দিনও কী আমার কাজের প্রশংসা করতে পারতে না।’ মা আমি তোমায় খুব ভালবাসতাম, তাই মনে মনে তোমার মতো হতে চেয়েছি। কিন্তু বার বার তোমাকে দেখে মনে হত তোমার মতো তো হতে পারলাম না। বাবার মতো করে আমায় একটু ভালবাসলে না কেন মা?’ (Column)
আপনাকে এই জানা : শেকড়ের ডানা আর ডানার শেকড় : মধুজা বন্দ্যোপাধ্যায়
সে অভিনেত্রীর একটা কথাও সেদিন বানানো monologue মনে হয়নি। তাই তাঁর দুঃখে সেদিন সবার চোখই জলে ভিজে গিয়েছিল। তিনিও হয়তো ভারমুক্ত হয়েছিলেন। সেদিন আমায় ভাবিয়েছিল ঘটনাটা —বাবা মা মানেই তাঁরা তাঁদের সবটা দিয়ে ভালবাসবেন তা হয়তো স্বাভাবিক নয়। বাবা-মা অনেক সময়ে নিজের ছাঁচে নিজের মতো করে ছেলেমেয়েদের গড়ে তুলতে গিয়ে বিধিনিষেধের বেড়াজাল বোনেন নিজের অজান্তে। সেই বেড়াজালই কখন এক মজবুত জেলখানা হয়ে যায়—যেখানে ভালোবেসে দুটো হাত একে অপরকে ছুঁতে পারে না। (Column)

এমনই মন ভারি করা এক দিনের পর আমরা ক’জন ঠিক করলাম একবেলার জন্য ফ্লোরেন্স যাব। ট্রেনে চেপে ইতালির গ্রামের মধ্যে দিয়ে সফর করছি ভেবে নিজেরই মন আনন্দে ভরে উঠছিল। টুরিস্টের মতো ঘুরে ঘুরে লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির বাড়ি, ডেভিডের মূর্তি, ফ্লোরেন্স ডুমো ঘুরে ঘুরে এসে দাঁড়ালাম উফিজি মিউজিয়ামের সামনে। ছোটবেলায় মনে পড়ে কেউ হয়তো ইতালি বেড়াতে গিয়ে উফিজি গ্যালারির এক ক্যাটালগ বই আমার মাকে উপহার দিয়েছিলেন। সেই বইয়ের পাতা উল্টেপাল্টে রেনেসাঁ পেন্টিং দেখতে আমার খুব ভাললাগত। ছোটবেলায় জানতাম না সে সব ছবি কোথায় আছে। কারণ বইটি রোমান হরফে লেখা হলেও ইংরেজিতে লেখা নয়। বড় হয়েও ছবিগুলো মনে ছিল কিন্তু উফিজির কথা ভুলে গেছিলাম। সেদিন গ্যালারির সামনে দাঁড়িয়ে মনে হল হয়তো আমি মনে মনে এই গ্যালারিতে আসতে চেয়েছিলাম। তাই জীবন আমাকে আজ তার সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। সে সময় ইন্টারনেটে টিকিট বুক করলে যে মিউজিয়ামের লম্বা লাইন এড়ানো যায় তাও জানতাম না। সামনে বিশাল লাইন আর হাতে সময় মাত্র তিন ঘণ্টা। দলের বাকিরা বলল, তারা ফেরত যেতে চায়। আমার কেমন জেদ চেপে গেল। এত কাছে এসে আমি ফিরে যাব না। একা একা বিদেশ বিভুঁইয়ে সেই প্রথম ঘোরার অভিজ্ঞতা। দেড় ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে সামনে পিছনের নানা বয়সের নানা ভাষার মানুষের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। আর ভয় করল না। (Column)
পনেরোশো শতক, মানে ভারতে সে সময় মুঘল আমল ইতালির টাস্কানি প্রদেশ শাসন করত ‘হাউজ অফ মেদিচি’। সে সময় টাস্কানি প্রদেশের প্রাণকেন্দ্র ছিল ফ্লোরেন্স। তাই সেখানেই শিল্প, সংস্কৃতির চর্চা হত সবচেয়ে বেশি। উফিজি গ্যালারি গড়ে উঠেছিল সেই মেদিচিদের ব্যক্তিগত শিল্প সংগ্রহ নিয়ে। হাতে দেড় ঘণ্টা সময়, তারপর মিউজিয়ামের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। দৌড়ে দৌড়ে যতটা পারা যায় দেখে থমকে গেলাম বত্তিচেলির আঁকা ‘বার্থ অফ ভিনাস’ দেখে। এ ছবি খুব চেনা। কিন্তু কোনওদিন তাকে চাক্ষুস দেখব তা ভাবতে পারিনি। টিশিয়ানের ভিনাস বা রাফায়ালের আঁকা ম্যডোনা দেখেও একই রকম শিহরণ হল। এই ছবিতে রং, রেখা এতটাই পরিপাটি দেখলে মনে হয় ছবি নয়, যেন ফোটোগ্রাফ। রেনেসাঁ পেন্টিং-এর পোর্ট্রেটের আর এক বৈশিষ্ট্য হল মুখের অভিব্যক্তি নেই কোনও মানুষের। তাদের হাত, পা, পোশাক, চুল সব পরিপাটি কিন্তু মুখে কোনও ভাষা নেই। কারণ সে সময় ফোটোগ্রাফি আসেনি। দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা শিল্পীর সামনে বসে থাকা যায় কিন্তু পোট্রেটে মুখের হাসি ধরে রাখা যায় না। এই একটা জায়গাতেই মোনালিসা বিরল! সে সময়ের আশ্চর্য এক প্রতিকৃতি। তাই মোনালিসার হাসি এক বিস্ময়। আর ততটাই বিস্ময়কর তার নির্মাতা লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি। মনে মনে ভাবলাম উফিজির মতোই একদিন হয়তো মোনালিসা দেখতে যাব প্যারিসের ল্যুভেরে। মনে একরাশ ভালোলাগা নিয়ে গ্যালারি থেকে বেরোলাম। সামনেই ফ্লোরেন্সের main market square—নভেম্বর মাসের শেষের দিক। বসেছে ক্রিসমাসের মেলা। তার মধ্যে দেখি একদল ইস্কনের সাহেব খালি গায়ে, নামাবলী পরে হরিবোল ধরেছেন। পাশে আর একজন গিটারে Imagine গাইছে। মনে হল এক বিশ্বগ্রামে চলে এসেছি। এ-পথ সে-পথ ঘুরে হঠাৎই দেখি ঘড়িতে পৌনে নটা। (Column)

আমাকে আবার একা একা পথ চিনে ফিরতে হবে। Google Map তখনও হাতের মুঠোয় আসেনি। আশেপাশের লোককে জিজ্ঞেস করলাম স্টেশন কোথায়? দৌড়াতে দৌড়াতে সেখানে পৌঁছে দেখি তা বাস টার্মিনাস। এখানে বসে টার্মিনাসকেও স্টেশন বলা হয়। খুবই অসহায় লাগল। অর্ধেক মানুষ এখানে ইংরেজি বোঝে না। হঠাৎ পেয়ে গেলাম এক চিনে মহিলাকে। পরিষ্কার ইংরেজিতে আমাকে পথ দেখিয়ে দিলেন। জানতে পারলাম জন্মসূত্রে তিনি চাইনিজ হলেও অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক। তাঁর স্বামীর Vodaphone-এ চাকরি সূত্রে তিনি ফ্লোরেন্সে এসেছেন। তারপর টিকিট কেটে ফাঁকা ট্রেনে যখন অ্যারেজো নামলাম, ঘুটঘুটে অন্ধকার। চারপাশের রাস্তা শুনশান। প্রবল খিদে পেটে কিন্তু রাত দশটায় সব দোকানই বন্ধ। যে ধর্মশালায় থাকতাম সেখানে একটা Food Vending Machine ছিল। সেখানে এক ইউরো ফেলে একটা ক্রঁসো খেয়ে ঘরে গেলাম একরাশ আনন্দ আর একবুক সাহস নিয়ে। সেই আমার প্রথম সত্যি সত্যি একলা ঘোরা। তারপর আর থেমে থাকিনি। (Column)
প্রচ্ছদ – মধুজা বন্দ্যোপাধ্যায়
ছাত্রী ইতিহাসের আর চাকরি গণমাধ্যমে। তাতে কী! নেশা কিন্তু আঁকা এবং লেখা। বিশেষত নকশা। নোটবুক ভর্তি তার প্রতিটি ছবিই গল্প বলে চলে। গুছিয়ে বসে বা দফতরের মিটিংয়ের ফাঁকে - রং কাগজ এবং কলম সবসময় মজুত।