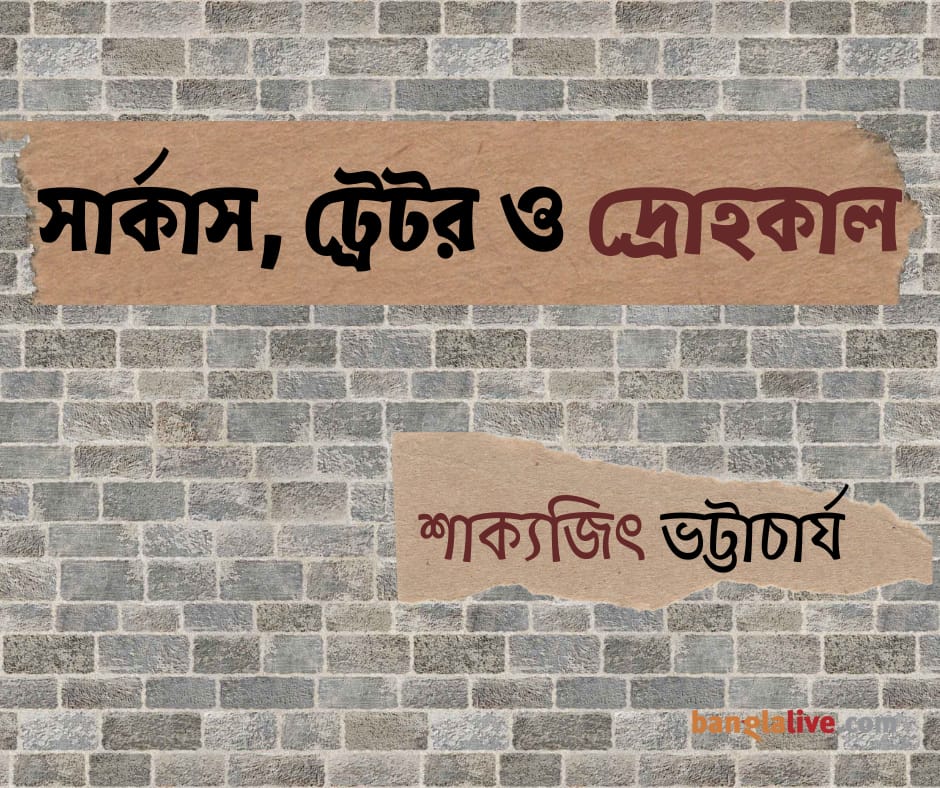আগের পর্ব পড়তে: [১] [২] [৩] [৪] [৫] [৬] [৭] [৮]
গ্লাসনস্তের উঠোন
‘বরং নিজেই তুমি পুষ্পিত হও– দারুব্রহ্ম বললেন, তার
দক্ষিণে প্রকাণ্ড এক দুধপুকুর এখন জলে টৈ-টুম্বুর, আর বামে নিহত
শকুনগাছ, সেখানে রাতে চাঁদের গাড়ি এসে দাঁড়ায়, রোজ
কলমে কর্পূর ভোরে অঙ্ক করি, পিপাসায় গলা শুকিয়ে
কাঠ, সেখানে আজ আর সুর নেই, সুগন্ধ পালিয়ে গেছে অন্য লোকের
বাড়ি, অশ্রু, লজ্জা, অশ্বভয়…’
-সুব্রত সরকার
সহস্রাব্দের শুরুর দিকে আমাদের অনেকেরই কাঁচা লেখালেখিকে প্রশ্রয় দিতেন, সময়ে সময়ে সংশোধন করে অকৃপণ ঔদার্যে নিজেদের কাগজে ছাপাতেন যেসব অগ্রজ সম্পাদক ও সাহিত্যিকরা, তাঁদের দেখে আমরা একপ্রকার আশঙ্কায় ভুগতাম। আশঙ্কা, তাঁরা যদি না থাকেন, অথবা কাগজ যদি বন্ধ হয়, তাহলে আমাদের লেখা কোথায় যাবে? কেউ তো চেনে না, ছাপাবে কে? আমরা দুরুদুরু বুকে পরিষ্কার হাতে লেখা ফুলস্কেপ কাগজের বান্ডিল দিয়ে আসতাম পত্রিকার অফিস অথবা কফি হাউসে, যেখানে তাঁদের আড্ডা ছিল। তাঁরা স্নেহভরে বলতেন ‘বসে যাও, চা খেয়ে যাও’, আর আমরা ইতস্তত কুণ্ঠার সঙ্গে এটা ওটা অজুহাত দিয়ে পালাতাম। তারপর ভুলেও আর যোগাযোগ করতাম না, জানতে চাইতাম না ‘গল্পটা কেমন লাগল’। যদি বলেন যে ‘হয়নি’, মনে হবে পায়ের নীচে মাটি দু’ভাগ হয়ে গেল। আর কোনওদিন সেখানে লেখা পাঠানো যাবে না। রাসবিহারীর বুক স্টলে মাঝে মাঝে গিয়ে তাগাদা দিতাম, নতুন ইস্যু কবে বেরবে? কল্যাণদা, সেই দোকানের মালিক, তিনি নিশ্চয়ই ততদিনে এরকম হাজার হাজার তাগাদায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। মাঝে মাঝে রেগে বলতেন, ‘কাগজের ঠিকানায় খোঁজ নাও না!’ তিনি কিন্তু কোনওদিন ফেরাননি আমাদের। নতুন পুরনো সব সংখ্যা ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে ঘাঁটতে দিয়েছেন, কেনার রেস্ত নেই জেনেই।
লেখা অমনোনীত হলে পত্রিকাগুলো কিছু জানাত না। মনোনীত হলে ফোন করত সাধারণত। হয়ত সম্পাদক বলতেন, ‘একদিন আমাদের সাথে দেখা করুন। আলাপ পরিচয় হবে।’ বুঝতাম, এখানে তার মানে পরেও লেখা পাঠানো যাবে। উৎসাহিত হয়ে চলে যেতাম কোনও দুপুরবেলা। তাঁর বাড়িতে প্রায়ান্ধকার ঘরে একটা টেবিলের ধারে বসে থাকেন সম্পাদক। তাঁকে সর্বশক্তিমান লাগে। তিনি নিজে লেখক হলে তো কথাই নেই। আমার কাছ থেকে জানতে চান টুকটাক, কবে থেকে লিখি, কার লেখা ভাল লাগে, এখন কী লিখছি। ক্রমে ক্রমে এক দুজন এসে পড়েন। বর্ষার বিকেলে মরা আলো নেতিয়ে যায়। যাঁরা আসেন, তাঁরা কেউ কেউ আলাপ করেন যেচে, স্নেহমিশ্রিত উপদেশ দেন। সংকোচের সঙ্গে জানাই, অন্য কাগজে অমুক লেখা লিখেছি। তাঁরা পড়বেন বলে উৎসাহ দেখান। অনুভব করি, একটা বৃত্ত গড়ে উঠছে। পারস্পরিক অসূয়া, নিন্দাবাদ, রেষারেষির পরেও, সার্বিক একটা স্রোতের ভেতর বুদবুদ হয়ে টিকে থাকে যে বৃত্তগুলো, কোথাও গিয়ে সংলগ্নতার বোধ চারিয়ে দেয়।

তখন ছোট ছোট গল্পপাঠের আসর হত এখানে ওখানে, অথবা সাহিত্যসভা। এক একটা গোষ্ঠী নিজেদের বৃত্ত নিয়ে প্রাইমারি স্কুলঘর, ক্লাবঘর বা কারোও বাড়ির বসার ঘরে সেসব সভা করত। আমরা গল্প পড়তে গিয়ে দেখতাম, যাঁরা পড়ছেন তাঁদের সবাইকেই প্রশংসা করা হচ্ছে। কোনও গল্প ভাল লাগছে না, তবু সভাপতি অদ্ভুত ক্ষমতায় সেগুলোর মধ্যে থেকেও পাঠযোগ্যতা ছেনে আনতেন। স্নেহ, ভালবাসা এগুলো কারণ ছিলই। সেই সঙ্গে গোষ্ঠী ধরে রাখার তাগিদও কম নয়। কাউকে সমালোচনা করলে তিনি হয়ত আর আসবেন না। অনেক সময়েই বাড়ির মালিককে সভাপতি করা হত। চা ও নোনতা বিস্কুট যোগাবার দায়িত্ব তাঁর। অবশ্য আর্থিক সামর্থ্যওয়ালা সম্পাদককেও দেখেছি। তিনি খাবারের প্যাকেট রাখতেন। সভা চলাকালীন বেশিরভাগ সময়টাতেই সম্পাদক দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতেন, নাহলে ব্যস্ত মুখে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করতেন। তাঁকে ঘিরে তৈরি হওয়া শীর্ণ লেখালেখির স্রোতকে মেন্টর করা অথবা বুক দিয়ে আগলানোর একপ্রকার দায়িত্বই কাঁধে তুলে নিয়েছেন সবসময়ে।
ছবিটা বদলে গেল ২০১০-এর পরবর্তীকালে, যখন ফেসবুক ঢুকে পড়ল হুড়মুড়িয়ে। তার আগে অর্কুট ছিল, কিন্তু সেখানে সাহিত্য রচনার প্রচেষ্টা এত সংগঠিত আকার নেয়নি। ফেসবুক এসে সাহিত্য-যশঃপ্রার্থীদের দেওয়াল গদ্য কবিতায় ভরিয়ে তুলল, এবং জুটে গেল বন্ধুবৃত্তের তারিফ। এর ফলে দুটো বড় ব্যাপার ঘটল। সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে যে হায়ারার্কি সেটা ভেঙে গেল। আগে অগ্রজ সাহিত্যিক ও সম্পাদকের পিঠ চাপড়ানি যেমন বড় একটা ব্যাপার ছিল, সে জিনিসগুলোই অনেক ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেল। দ্বিতীয়ত, তৈরি হল নতুন নতুন বৃত্ত, যাদের পোশাকি নাম ওয়েবজিন, এমনকি ফেসবুকের লেখা থেকে তৈরি হওয়া পাবলিকেশন হাউসও। বিগ হাউসের কৌলীন্য আমরা দিনে দিনে হতমান হতে দেখলাম, আর একই সঙ্গে দেখলাম ছোট বড় ক্ষমতার বৃত্তগুলো ভাঙতে। এখন ওয়েবজিনে লেখা পাঠাতে গেলে সরাসরি তাদের ইমেল আইডিতে পাঠিয়ে দিলেই হয়, অথবা ফেসবুকে মেসেজ। আগেকার মত ওজনদার নামের সার্টিফিকেট পিঠে ছাপ মেরে পত্রিকার অফিসে কড়া নাড়বার দরকার পড়ে না। বর্ষীয়ান সাহিত্যিক ফেসবুকে কিছু বললে তাঁকে সেখানেই রূঢ় বিরুদ্ধাচরণও সম্ভব হয়ে গেল। কারণ এই অবাধ গণতন্ত্রের দুনিয়াতে সবাই ক্ষমতাহীন, এবং প্রত্যেকে তাই প্রবল ক্ষমতাধর। যে ওয়েবজিন আমার লেখা বাতিল করবে তাদের প্রকাশ্যে গালমন্দ করেও অন্য ওয়েবজিনে পরের মাসেই বার করা যায় লেখাটি। এখানেও বৃত্ত হয়, গোষ্ঠী হয়। একে অন্যের পিঠ চাপড়ায়। যা-ই লিখুক না কেন কেউ, তাকে ভাল বলার কয়েকজন জুটেই যায়। আর সবথেকে বড় কথা, এখানে পাঠক সংখ্যা অনেক বেশি। একটা কাগজ বার করলে তার পাঠক যদি দু’শ হয়, এখানে চেষ্টা করলে কুড়ি হাজার মেলাও সম্ভব। তারা দীক্ষিত পাঠক না অদীক্ষিত, লেখক নিজে সাহিত্যের নির্যাস কতটা আত্মস্থ করেছেন সে প্রশ্নগুলো অবান্তর। কারণ মূল প্রশ্নটা পালটায়নি। আমরা যখন লিখতে এসেছিলাম, সৃজন বা নিরীক্ষার মত ভারী শব্দ ভেবে আসিনি। লেখার জায়গা খুঁজেছিলাম, এবং লিটল ম্যাগাজিন সে জায়গা আমাদের দিয়েছিল। ফেসবুকে যে তরুণ তরুণীরা লিখছেন, তাঁরাও সেটাই চান এবং চটজলদি লেখা বার হবার আকর্ষণে আত্মস্থ হন। সম্পাদনা অথবা গ্রহণ বর্জনের অঙ্ক এখানে কিছু অন্য নিয়মে চলে। আবার এসবের ভেতর দিয়ে ভাল ওয়েবজিনও উঠে আসে। বন্ধুরা মিলে বানায় মননশীল প্রকাশনা। বিগত কয়েক বছরে অন্তত চারজন ভাল লেখক ও কবিকে দেখেছি, যাঁদের লেখার প্রথম জায়গা ছিল ফেসবুক। লিখতে লিখতে অন্যদের নজরে পড়েছেন, লেখা ছাপা হয়েছে ওয়েবজিন ও পত্রিকায়, বই হয়েছে, পুরস্কারও পেয়েছেন। নিজের যোগ্যতাতেই পেয়েছেন।

আর এই পরিবর্তনের সঙ্গেই পালটে গেল প্রতিষ্ঠানবিরোধীতার চিরাচরিত ছক। এখন বাণিজ্যিক কাগজে লেখা ছাপানো তত আকর্ষণীয় নয়। তার বদলে নিজের পেজকে জনপ্রিয় করে সেখানেই হাজার হাজার পাঠকের সংস্পর্শে আসা যায়। পুরো প্রক্রিয়াতে সময় কম, খরচেরও প্রশ্ন নেই। ফলত একদিকে যেমন লাখে লাখে অকবিতা ও অগদ্যের বন্যাস্রোত আমাদের পাঠাভ্যাস ভাসিয়ে দিল, আবার একই সঙ্গে সিরিয়াস অপ্রাতিষ্ঠানিক সাহিত্যিক, যিনি লেখালেখির কমার্শিয়ালাইজেশনের ধারণাটাকে আঘাত করতে চান, তিনিও পরিস্থিতিকে ব্যবহার করতে এগিয়ে এলেন। পিডিএফ করে অথবা নিজস্ব ব্লগে ছড়িয়ে গেল বহু নিরীক্ষামূলক লেখা। সেখান থেকে আবার একাধিক সিরিয়াস সাহিত্যের ব্লগ ও ম্যাগাজিন তৈরি হল। এমনকি অনেক লিটল ম্যাগাজিন আজকাল না ছাপিয়ে পিডিএফ করে গুগল ড্রাইভে তুলে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। তাদের গুণগত মান ঈর্ষণীয়। বহু মনে রাখার মত লেখা ও চমকে দেওয়া নিরীক্ষা এই প্রক্রিয়াতেই আমাদের সামনে চলে আসছে। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সাধ্য ছিল না তার সঙ্গে পাল্লা দেবার। লক্ষ করলে দেখা যাবে কমার্শিয়াল কাগজগুলির গুণগত মানেও অনেকটা অবনতি ঘটেছে, যদি আগের তিরিশ বছরের সঙ্গে তুলনা করা হয়। সেই অবনতির একটা কারণ কিন্তু এটাও।
তার মানেই অবশ্য এই নয় যে এই অল্টারনেটিভ স্পেস সবসময়েই দারুণ সব জিনিস দিয়ে আমাদের ধাঁ করে দিচ্ছে। বরং বাণিজ্যিক কাগজের বাণিজ্যিক লেখক নিরীক্ষার মুখোশ পরে গা ভাসিয়েছেন এখানে, তাঁদের ছদ্ম-অল্টারনেটিভ সাহিত্য প্যারালালের চোলাই করিয়ে দিব্যি চালানো হচ্ছে, এমনটাও ঘটছে। এমন ঘটছে যে বাণিজ্যিক আর প্যারালালের মধ্যে স্পষ্ট ভেদরেখা থাকছে না। এই সপাট ভুবনায়নের খোলা দুনিয়াতে সকলেই এক স্রোতের যাত্রী বলে মনে হচ্ছে। যা সাহিত্য নয় তাকেও ভিড়ের সমর্থনে মহান সাহিত্য বলে চালানো হচ্ছে, যেহেতু লাইক শেয়ার ও ‘আহা কী পড়িলাম’ কমেন্টের শক্তি ভিন্নকণ্ঠকে রুদ্ধ করার জন্য যথেষ্ট। নিজের বইয়ের ফেসবুকে রিভিউ করাবার জন্য একে ওকে ধরা, নিজের প্রকাশিত বইটির প্রচারের জন্য ফেসবুক লাইভ অনুষ্ঠানে নিজেই আমন্ত্রণ জানিয়ে অনুরোধ করা ‘একটু ভাল ভাল কথা বলে দিও’, ইত্যাদি নির্লজ্জতার বহিরঙ্গ পালটালেও মূল চরিত্র সেই কনভেনশনাল লেখালেখির সময় থেকেই অবিকল। আগেও নিজের লেখা বই গিয়ে দিয়ে আসা, প্রবীণ সাহিত্যিককে প্রণাম করতে যাবার অছিলায় বাড়ি গিয়ে তাঁকে এক কপি ধরিয়ে দেওয়া, তাঁর বাড়ির রবিবারের আড্ডায় নিয়মিত হাজিরা, ইত্যাদি ছিল। সেগুলোর রূপ পাল্টেছে, এই মাত্র।

তাহলে এখন কি আগেকার সেই সাহিত্যসভাগুলোর সময় শেষ? অন্ধকার ছোট স্কুলঘরে ঝিমোতে থাকা অনিচ্ছুক শ্রোতাদের সামনে নিজের লেখা গল্প পড়ছে যে যুবক, তার দিন কি তবে ফুরিয়ে এল? সম্ভবত নয়। দুটোই পাশাপাশি রাস্তা হাঁটবে। যে কোনও বদল, আমরা আজ জানি, মহান আদর্শ থেকে হয় না। হয় প্রাত্যহিক দিন চালানোর ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধির সংঘাত থেকে। স্কুলঘর থেকে ফেসবুক লাইভে বদলের ফলে ক্ষমতার হায়ারার্কি ভেঙে যাবার প্রক্রিয়াতে বিপ্লব ছিল না। ছিল, আগেকার মতই, নিজেদের লেখক হিসেবে পরিচিতি পাবার ইচ্ছেটুকু। তাতে ভাঙনের বাস্তবতা মিথ্যে হয় না।
ছবি সৌজন্য : Wikimedia Commons, PixaHive
শাক্যজিৎ ভট্টাচার্যের জন্ম ১৯৮২ সালে কলকাতায়। প্রথম গল্প বেরিয়েছিল পরিকথা পত্রিকায়, ২০০৩ সালে। এ পর্যন্ত লিখেছেন সাতটি উপন্যাস ও প্রায় চল্লিশটি ছোটগল্প। মূলত লিটল ম্যাগাজিনই তাঁর লেখালেখির জায়গা। এ পর্যন্ত পাঁচটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।