এইভাবেই ডাকতাম আমরা বেলতলা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা অপর্ণাদিকে। প্রিন্সিপাল ম্যাম ডাকার প্রশ্নই ছিল না বাংলা স্কুলে, আড়ালে যদিও হেডমিসস্ট্রেস বলা যেত। ভাল পড়াশুনোর জন্য স্কুলের কোনও ভূমিকা আছে, এটা আমার বাবা-মা মনে করতেন না। এখন মনে হয় সেটা আমাদের দূরে না পাঠানোর ছুতো। হস্টেল তো নৈব নৈব চ, ইংরিজি মিডিয়াম স্কুলেও পাঠানোর কথা ভাবা হয়নি। আমিও কাছাকাছির স্কুলে দিব্যি ছিলাম। ন্যূনতম পড়াশুনোয় পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করে।
তবে স্কুলের একটা জাদু ছিল আমার উপর। দিদিমণিরা যা বলবেন, তা করতেই হবে। খাতাবই বছরের গোড়ায় কিনে ব্রাউন পেপারে মলাট দিয়ে নামের লেবেল লাগানো থেকে ড্রইং পেনসিলের ব্র্যান্ড স্কুল যেমন বলেছে তেমনটিই চাই, যেদিন বলেছেন, সেদিনই চাই। অফিস থেকে ফিরে এই সব দুর্লভ বস্তুর মৃগয়ায় আবার বেরিয়ে পড়া বাবার জন্য কত কঠিন হত, তা আমি বুঝতেও চাইতাম না। ঠোঁট ফুলিয়ে বসে থাকতাম, যতক্ষণ না জিনিসটা হাতে আসে।
একদিন মা রাগ করে বললেন, যাও তুমি স্কুলেই থাক এখন থেকে, দিদিমণিরা যখন বেশি আপন আমাদের থেকে। বাড়ি এবং স্কুল দুটো সমান্তরাল প্রতিষ্ঠান আমাকে দু’ভাবে টানে বুঝতে পারতাম। বাড়ি আমার আপন, স্কুলেরও ছিল এক নিজস্ব মায়া। চৌকো খোপ কাটা খাতায় একক দশক শতকের অঙ্ক করতে প্রথম দিন যা একটু অসুবিধে হয়েছিল, তারপর সব সামলে নিলাম। যেটাকে আমি সহস্র বলে জানি, তাকে স্কুল বলে হাজার, এটা আমি মন থেকে মেনে নিতে পারিনি।
যাইহোক, এই আনন্দময় জীবনের মাঝে একদিন আমি বড়দিদিমণির নজরে পড়ে গেলাম। তারিখটা মনে আছে। ২৭ শে মে, ১৯৬৪। পণ্ডিত নেহরুর মৃত্যুদিবস। স্কুলের সবচেয়ে বড় হলঘর, কবি নিকেতনে, প্রাইমারি থেকে ক্লাস টুয়েলভের মেয়েদের নিয়ে শোকসভা হচ্ছে। বড়দিদিমণি সেখানে নেহরুর জীবন ও অন্যান্য কীর্তি নিয়ে বলছেন। সভার শেষে শোকপ্রস্তাব তৈরি করে দিল্লি পাঠানো হবে। আমাদের পাঠানো এইসব প্রস্তাব কেউ পড়ত কিনা জানা নেই, কিন্তু এসব যথেষ্ট উদ্যমের সঙ্গে করা হত।
প্রচণ্ড গরম, দাঁড়িয়ে থাকার ক্লান্তি, হঠাৎ আমার চারপাশে পৃথিবী দুলে উঠল, আমাকে ঘিরে চিৎকার চেঁচামিচির মধ্যেই আমি জ্ঞান হারালাম। যখন চেতনা এল, তখন বুঝলাম, আমি একটা কাঠির বেঞ্চিতে শোওয়া, আমার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বড়দিদিমণি। উৎসাহী কেউ চোখেমুখে জল ছিটিয়েছে, ইউনিফর্ম ভেজা। ক্লাসটিচার বড়দিদিমণিকে বলছেন, এ-ই হল ক্লাস থ্রির ফার্স্ট গার্ল। এত রোগা! শরীরে কেবল হাড়! ভীষণ দুর্বল তো! সেদিন আমি কেবল নিজের নাম বলতে পেরেছিলাম।
তবে স্কুলের একটা জাদু ছিল আমার উপর। দিদিমণিরা যা বলবেন, তা করতেই হবে। খাতাবই বছরের গোড়ায় কিনে ব্রাউন পেপারে মলাট দিয়ে নামের লেবেল লাগানো থেকে ড্রইং পেনসিলের ব্র্যান্ড স্কুল যেমন বলেছে তেমনটিই চাই, যেদিন বলেছেন, সেদিনই চাই।
কেউ কি বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল আমাকে? হয়তো মোক্ষদাদিদির মতো সহায়িকা কেউ। মনে নেই। বাবা-মা সামনে কোনও উদ্বেগ না দেখালেও, ‘শরীরে কেবল হাড়’ মন্তব্য নিয়ে একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কাজু বাদাম মহার্ঘ্য। মধ্যবিত্তের বাজেটের বাইরে। কারও পরামর্শে আমাকে কাঁচা চিনেবাদাম খাওয়ানো হত একমুঠো করে। সেই হাড় সর্বস্বতার ধারাপথ বেয়ে একদিন আমি যে অতিকায় হয়ে উঠব, তা আমার স্কুল ও বাড়ির অভিভাবকবৃন্দ কেউই ভাবতে পারেননি।
যাই হোক, বড়দিদিমণি যে আমাকে মনে রেখেছেন, তা বুঝলাম সেকেন্ডারি সেকশনে উঠে। ক্লাস ফাইভ থেকে বড়সড় অর্ধগোলাকার লাল বাড়িতে ক্লাস। ওই বাড়ির একতলায় সিঁড়ি দিয়ে উঠে প্রথম ঘরটাই বড়দিদিমণির। বিশাল ঘরখানা, অন্তত স্কুলবেলায় সেই রকমই মনে হত। পিছন দিকে একটা গোল টেবিলে ছোটখাটো মিটিং হত। অভিভাবকদের ডাকলে তাঁরাও ওই ঘরে আসতেন।
সামনের দিকে একটা বড় স্ট্যান্ডে রাখা থাকত ভূগোলের নানা ম্যাপ। ভূগোলের ক্লাসের আগে ম্যাপ নিতে এসে মনিটর কয়েক লহমার জন্য ওই ঘরের ভিতরটা দেখতে পেত। কেবল কাজের সময়টুকু ওই ঘরে বসতেন বড়দিদিমণি, বাকি সময়টা তিনি স্কুলের নানা ক্লাসরুমে ঢুকে খোঁজ খবর নিতেন। বিরাট লম্বা অর্ধগোলাকার করিডরের একপ্রান্তে তিনি দাঁড়ালেই স্তব্ধতা নেমে আসত অন্য প্রান্তে। টিফিন ব্রেকে তিনি নিজের ঘরের সামনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতেন খেলার মাঠের দিকে। মেয়েরা হুটোপাটি করে খেলছে, পা দুলিয়ে টিফিন খাচ্ছে সিমেন্টের স্টেজের উপর, এই সব দেখতে তাঁর ভাল লাগত। সম্পূর্ণ স্থির, ঋজু, তাঁর দিকে না চেয়েও বুঝতে পারতাম নি:শব্দে তিনি কত কিছু দেখছেন। ব্যক্তিত্ব বুঝি একেই বলে।
চুল উল্টে আঁচড়ে পিছনে হাতখোঁপা, কোনও প্রসাধন নেই। শাসন কেবল চোখের দৃষ্টিতে। ক্লাস ফাইভে চিকেন পক্সে দীর্ঘদিন ভুগে, মাথার একরাশ চুল খুইয়ে সিল্কের রুমাল বেঁধে আমার ক্লাসে ফেরা। দুর্বল হয়ে গেছি, ছুটে খেলতে পারতাম না। একদিন টিফিন টাইমে বড়দিদিমণি আবার ডাকলেন হাতছানি দিয়ে। বললেন, ইস শীতকালে সোয়েটার পরে থাকতিস, তখন ভেবেছিলাম একটু মোটা সোটা হলি বুঝি। এখন দেখছি, বড্ড রোগা রে! আমার সব কার্যকলাপে তাঁর চোখ থাকত। স্কুল ম্যাগাজ়িনে কী লেখা যাবে, কবিতা না গদ্য, তা-ও বলে দিতেন।
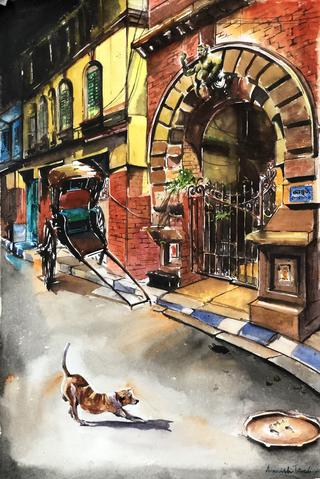
ক্লাস সেভেনে বললেন, ইংরেজি কবিতার অনুবাদ কর তো দেখি। সেই আমার প্রথম ছন্দ মিলিয়ে ইংরেজি কবিতার অনুবাদ। স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে আমাকে বললেন প্রবন্ধ লিখে, তার থেকে ভাষণ দিতে। ভাষণ দিতে দিব্যি অভ্যস্ত হয়ে গেলাম। প্রেয়ারে গানের লিড যারা দিত তাদের মধ্যেও আমি। মন্দ গাইতাম না অবশ্য সে বয়সে। প্রেয়ার শেষ করে ক্লাসে ছোটার আগের মুহূর্তে সব মেয়েদের গানের কথাগুলি বুঝিয়ে দিতেন অপর্ণাদি। মানে না বুঝে গান গাওয়া ছিল তাঁর দুচক্ষের বিষ।”ব্যথা মোর উঠবে জ্বলে ঊর্দ্ধপানে, প্রাণে নয়, বুঝেছ? এ জীবন পুণ্য করো। দহন দানে জীবন পূর্ণ হয় না, পুণ্য হয়।”
মায়ের মতন তিনিও আমাকে গড়েপিটে কোনও আদর্শে পরিণত করতে চাইছেন, সেটা মনের গহনে বুঝতাম। নইলে ফার্স্ট গার্ল তো সব ক্লাসেই একজন করে ছিল। ক্লাস সেভেন। রবিবার কোনও বিয়েবাড়ি ছিল। সোমবার স্কুল গেছি। লিপস্টিকের বালাই নেই, কম্প্যাক্ট পাউডার ও কাজলের রেখাই ছিল চোখে। প্রেয়ারের সময়েই তীক্ষ্ণ চোখ আমাকে দেখে নিয়েছেন, কারণ ডাক পড়ল ক্লাসে যাবার আগেই। এবার আর উপদেশ নয়। ডায়রেক্ট অ্যাকশন। মাড় দেওয়া ধবধবে সাদা শাড়ির আঁচল দিয়ে ঘষে আমার কাজল তোলা হল, ছাইরঙের পাউডারের পোঁচ মোছা হল। শেষে একটি ছোট নিশ্বাস। ‘তুমি যদি এই কর আমি অন্য মেয়েদের কী বলব?’
নিজের অজান্তে যে ক্রস বহন করতে লেগেছি, তা কেবল ক্লাসে প্রথম হওয়া মেয়ের ছিল না। ক্লাস এইটে একবার আমাদের সেকশনে এলেন। ইংরেজী ও অংকের পড়া ধরলেন। আমি তো সবেতেই হাত তুলি। আমাকে বলতেই দিলেন না, চোখ ছিল শেষ বেঞ্চগুলির দিকে। পরে নিজের ঘরে ডেকে বলেছিলেন, ক্লাসে ফার্স্ট তো যে কেউ হতে পারে। অঙ্কে আর ইংরেজিতে ক্লাসে যারা পিছিয়ে আছে, তুমি তাদের দায়িত্ব নাও। বছরের শেষে আমি দেখতে চাই তাদের নম্বর ভাল হয়েছে, সাবজেক্টগুলো ভাল করে বুঝতে পারছে।
সামনের দিকে একটা বড় স্ট্যান্ডে রাখা থাকত ভূগোলের নানা ম্যাপ। ভূগোলের ক্লাসের আগে ম্যাপ নিতে এসে মনিটর কয়েক লহমার জন্য ওই ঘরের ভিতরটা দেখতে পেত। কেবল কাজের সময়টুকু ওই ঘরে বসতেন বড়দিদিমণি, বাকি সময়টা তিনি স্কুলের নানা ক্লাসরুমে ঢুকে খোঁজ খবর নিতেন।
পরবর্তী জীবনে ইনস্টিটিউশন বিল্ডিং কথাটা অনেক শুনেছি। কিন্তু একজন মানুষ অতি অল্প সরকারি সাহায্যে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মেয়েদের একটি স্কুলকে কীভাবে নিজের ধ্যানজ্ঞান চেতনায় পরিণত করে তুলেছিলেন, নিজের চোখে দেখতাম। উচ্চশিক্ষিতা ব্রাহ্ম মহিলা, বিয়ে করেননি। স্কুলই ছিল সবকিছু। আর্থিক সামর্থ্য যথেষ্ট ছিল না, শিক্ষকদের শূন্য পদ সময়ে পূরণ হত না, তারই মধ্যে চেষ্টা চলত সাধ পূরণের। ড্রইং স্যার প্রাইজের বই কিনতেন। তিনি জানতে চাইলেন, আমি কী বই চাই। ক্লাস ফাইভে সবে পড়ে শেষ করেছি বিভূতিভূষণের ‘অপরাজিত’। ছোড়দার স্কুল লাইব্রেরির বই। ফেরত দেওয়া হয়ে গেছে। বইটার দাম সাত টাকা। আমার জন্য বরাদ্দ পাঁচ টাকা। হল না। ক্লাস সেভেনে আবার চেষ্টা। এবার বাজেট সাত টাকা। বইয়ের দাম ন টাকা। তৃতীয়বারের চেষ্টায় ক্লাস এইটে অপরাজিত পেলাম।
এখনকার হিসেবে হাস্যকর, যে কোনও খুব সাধারণ স্কুলেও। কিন্তু ‘অপরাজিত’ আমার লেখক জীবনের ভূপৃষ্ঠ। বাড়ির বইয়ের তাকে এসেছিল স্কুলের হাত ধরে। এই যে এক ছাত্রীর কাছে জানতে চাওয়া, সে কী বই চায়, তার হাতে প্লাস্টিকের ফুলদানি কিংবা একডজন বল পেন না ধরিয়ে দিয়ে, এবং পছন্দের বইটি দেবার জন্য একটানা চেষ্টা করে যাওয়া, এটাই বোধহয় বাড়িতে মা-বাবা আর স্কুলে অপর্ণাদিকে মিলিয়ে দিয়েছিল।
লাইব্রেরিতে অসুবিধে হচ্ছিল। আমি দ্রুত পড়ি। একসঙ্গে দু’ তিনটে বই পাশাপাশি। লাইব্রেরি আওয়ারে একটি বই পড়া হলে দ্বিতীয়টি পাওয়া যাবে, এই সব বাধানিষেধ আমার পছন্দ ছিল না। খবরটা অপর্ণাদির কাছে পৌঁছনোর পর আমার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা হল, অনেকটা লাইব্রেরির বিশেষ নাগরিকত্বের মত। লাইব্রেরির চাবির গোছা আমার নাগালেই থাকবে, আমি যে কোনও আলমারি যখন খুশি খুলতে পারব। পুরোনো সোনার জলে লেখা বইগুলি আমার দিকে তাকিয়ে থাকত পুরনো কাচের ভিতর থেকে। আমি মনের আনন্দে কালীদাস, অলিভার গোল্ডস্মিথ, ওয়াল্টার স্কট পড়তে থাকলাম। লাইব্রেরিয়ানের কাছে কোনও জবাবদিহি না করে। অর্থে নয় হৃদয়ের গুণে আমাকে টেনে রাখল আমার স্কুল।
অঙ্ক, ইংরিজির শিক্ষিকার পদ খালি। তারই মধ্যে উচ্চমাধ্যমিক। সবাই ধরে নিয়েছিল, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় স্কুলের মুখ উজ্জ্বল করার মতো আমি কিছু করব। মুখে কিছু না বলেও অপর্ণা দিদিমণি সেই দিকেই চেয়েছিলেন। কিছু বুদ্ধিদাতা সমাজের সব স্তরে থাকে। সহপাঠীদের একদল আমাকে বলতে লাগল, তুই একটা ভাল স্কুলে ভর্তি হয়ে যা। এখানে থাকলে রেজাল্ট ভাল হবে না। আমাকে ক্লাস টেনে নিতে যে কোনও ভাল বাংলা স্কুল উদ্গ্রীব হবে, জানতাম। আমিও চাইছিলাম অন্য কোথাও যেতে। বাদ সাধলেন আমার স্বল্পবাক বাবা। বললেন, যে স্কুল তোমাকে শৈশব থেকে লালন করেছে, কেবল ভাল রেজাল্টের জন্যে তাকে ছেড়ে যাবে? এখানে থেকে যা হবে হোক। তাই হয়েছিল। সাফল্যের চেয়েও প্রিন্সিপল বড়, সারাজীবনই তা অনুভব করতে করতে এগিয়েছি। লেখকজীবনেও।
কলকাতায় জন্ম, বড় হওয়া। অর্থনীতির পাঠ প্রেসিডেন্সী কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কবিতা দিয়ে লেখক জীবন আরম্ভ। সূচনা শৈশবেই। কবিতার পাশাপাশি গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী, প্রবন্ধ, ছোটদের জন্য লেখায় অনায়াস সঞ্চরণ। ভারতীয় প্রশাসনিক সেবার সদস্য ছিলেন সাড়ে তিন দশকেরও বেশি সময়। মহুলডিহার দিন, মহানদী, কলকাতার প্রতিমা শিল্পীরা, ব্রেল, কবিতা সমগ্র , দেশের ভিতর দেশ ইত্যাদি চল্লিশটি বই। ইংরাজি সহ নানা ভারতীয় ভাষায়, জার্মান ও সুইডিশে অনূদিত হয়েছে অনিতা অগ্নিহোত্রীর লেখা। শরৎ পুরস্কার, সাহিত্য পরিষৎ সম্মান, প্রতিভা বসু স্মৃতি পুরস্কার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুবন মোহিনী দাসী স্বর্ণপদকে সম্মানিত। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমীর সোমেন চন্দ পুরস্কার ফিরিয়েছেন নন্দীগ্রামে নিরস্ত্র মানুষের হত্যার প্রতিবাদে। ভারতের নানা প্রান্তের প্রান্তিক মানুষের কন্ঠস্বর উন্মোচিত তাঁর লেখায়। ভালোবাসেন গান শুনতে, গ্রামে গঞ্জে ঘুরতে, প্রকৃতির নানা রূপ একমনে দেখতে।


























3 Responses
ক্লাস টুয়েলভ নয়। ইলেভেন হবে। ১৯৬৪তে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা এগারো ক্লাসের পরে হত।
টুয়েলভ নয়। ইলেভেন হবে। ১৯৬৪তে এগারো ক্লাসের পরে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা হত।
পড়ছি, খুব ভালো লাগছে……