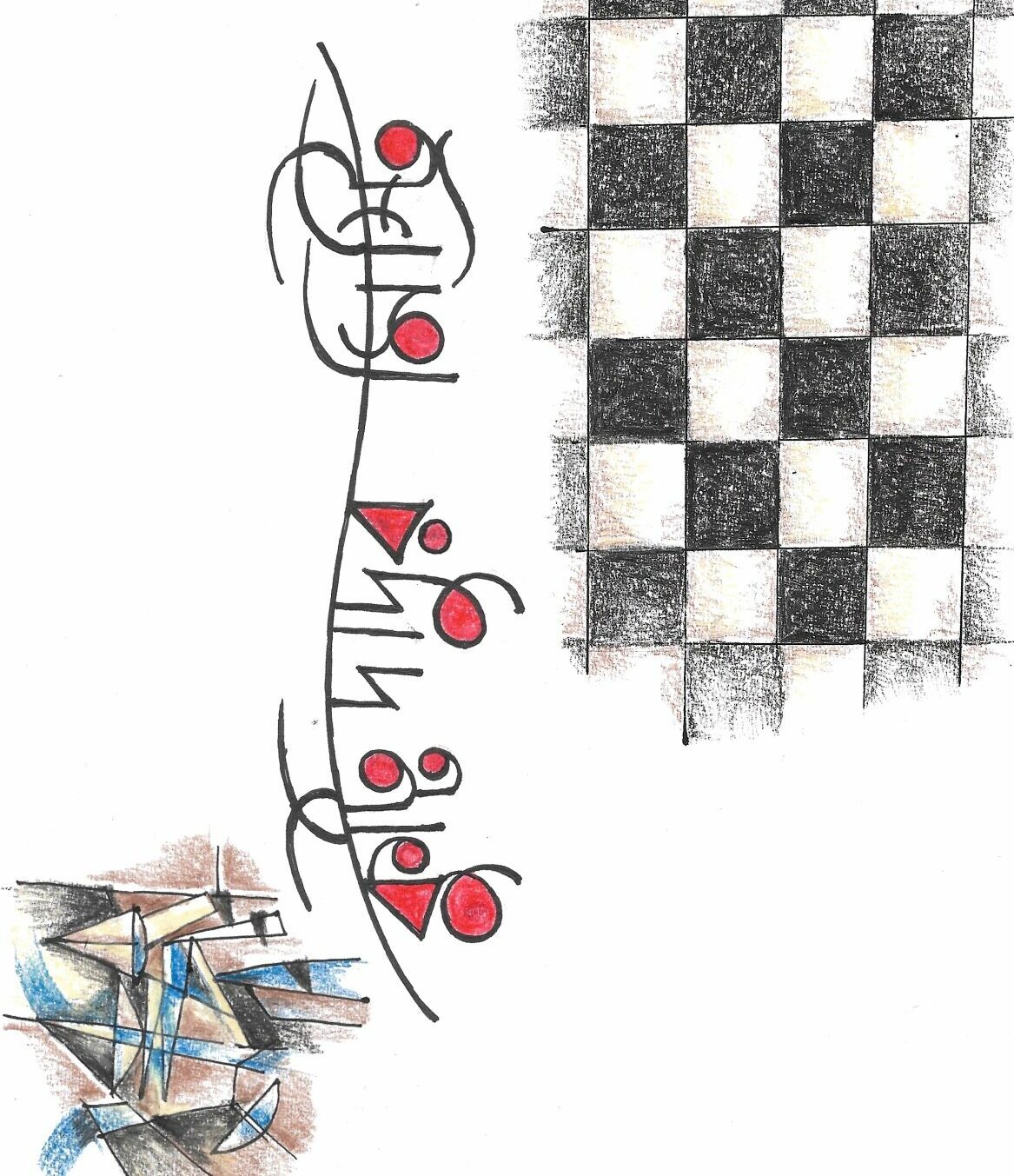ঋতজা মাঝেমধ্যেই বাঁশবেড়িয়ায় ওর পিসির বাড়ি যেতে বলে। গঙ্গার পাড়েই বাড়ি। খুব সুন্দর নাকি জায়গাটা। ওর পিসিও বলেছেন, আর ঋতজারও ভীষণ ইচ্ছে একবার পিকুদের সবাইকে নিয়ে ঘুরে আসে পিসির বাড়ি থেকে। সেইমতো এক শনিবার ওরা এসে পৌঁছলো বাঁশবেড়িয়া। বাঁশবেড়িয়ায় একেবারে গঙ্গার পারেই ঋতজার বড় পিসির বাড়ি। ঋতজার দুই পিসি। ছোট পিসি বেহালায় পর্ণশ্রীতে থাকেন, কলকাতায় এলে যার কাছে ঋতজা থাকে। আর বাঁশবেড়িয়ার পিসি হলেন বড় পিসি, ওর বাবার থেকেও বড়।
গেট দিয়ে ঢুকে ছোট্ট একটা বাগান। দেখেই বোঝা যায় একসময় কেউ যত্ন করে বাগানটা করেছিলেন। বাগান পেরিয়ে বাড়িতে ঢোকার মুখে দুপাশে একঝাঁক নয়নতারা গাছ, তাতে ভরে ফুল ফুটে আছে। একটা বেশ বড় পেয়ারা গাছও আছে বাড়ির বাঁ-দিকের কোনায়। পিকুদের দেখে ঋতজার পিসির প্রথম প্রশ্ন “শৌন আসেনি?” মেঘনা একটু মিচকি হেসে পিকুর দিকে তাকালো। ঋতজা বলল, “না ও তো শান্তিনিকেতনেই আছে!”
আরও পড়ুন- গল্প: ১৩বি হরি ঘোষ স্ট্রিট
পিকুরা তিনজনে ভেতরে গিয়ে বসল। খুব আলো হাওয়া বাড়িটাতে। একটা মন ভালো করে দেওয়া ব্যাপার আছে। ঋতজা সবাইকে নিয়ে বাড়ি দেখালো। বাড়ির পিছনেই গঙ্গা। ঠিক হল, দুপুরে খাওয়ার পর যাওয়া হবে গঙ্গার পাড়ে। বাড়ি দেখাতে দেখাতে ঋতজা বলল, “জানিস, আমার পিসির যে শ্বশুর, জিতেন লাহিড়ী, মানে আমাদের কুট্টিদাদু খুব নামকরা শিল্পী। ছবি আঁকেন। তখনকার দিনে আর্ট কলেজ থেকে পাশ করে বেশ কিছুদিন প্যারিসে ছিলেন। ওখানে থাকাকালীন উনি বেশ কিছু বিখ্যাত শিল্পীর সান্নিধ্যে আসেন। পিসি বলে, ওঁর কাছে নাকি কোনও এক বিখ্যাত ফরাসি শিল্পীর অরিজিনাল ছবি আছে, যার দাম আজকে আকাশছোঁয়া হবে। কুট্টিদাদুর তিনটে নেশা— ছবি আঁকা, বই পড়া আর দাবা খেলা। চল দাদুর সাথে দেখা করে আসি।
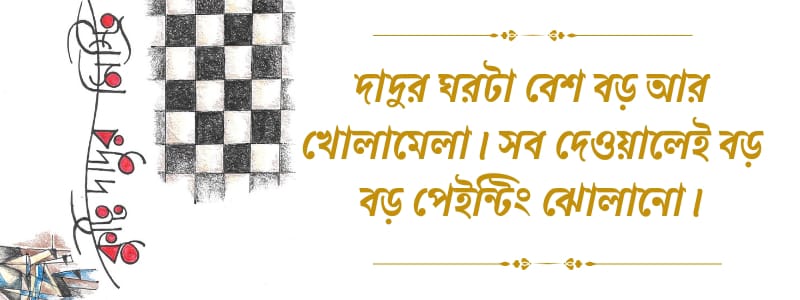
ঋতজা চেঁচিয়ে বলল, “পিসি আমরা ওপরে দাদুর সাথে দেখা করতে যাচ্ছি।”
“দাঁড়া চা আনছি, চা খেয়ে তারপর যা।” পিসি বলে উঠলেন।
গরম সিঙাড়া, রসগোল্লা আর চা খেয়ে পিকুরা ওপরে গেল। কুট্টিদাদু খাটে বসে ছবি আঁকছিলেন। ঋতজাদের দেখে বললেন “এসো এসো দাদুভাইরা…”
কুট্টি দাদুর ঘরটা বাড়ির পিছন দিকে। ঘরে ঢুকলেই উল্টোদিকের জানালা দিয়ে দূরে গঙ্গা দেখা যাচ্ছে, দু’একটা পালতোলা নৌকা ভেসে আছে। মেঘের ছায়া পড়ে নদীর জলও যেন আকাশের রঙে মেতে উঠেছে। কোথাও উজ্জ্বল, কোথাও বা ঘোলাটে। গোটাটা যেন একটা বহমান ক্যানভাস। দাদুর ঘরটা বেশ বড় আর খোলামেলা। সব দেওয়ালেই বড় বড় পেইন্টিং ঝোলানো। অধিকাংশই অয়েল পেইন্টিং। নানান ধরনের ছবি। একটা দেওয়ালে হুবহু একরকম কিউবিজমের স্টাইলে পাঁচটা ছবি পাশাপাশি টাঙানো। আর খাটের দুপাশে দুটো ঘুঁটি সাজানো দাবার বোর্ড। দেখে মনে হচ্ছে কেউ খেলতে খেলতে হঠাৎ উঠে গেছে। একটা বোর্ডে বেশ ধুলো পড়া, আর অন্যটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে রেগুলার খেলা হয়। তাছাড়া ঘরে একটা কাঠের আলমারি আর একটা টেবিল চেয়ার ছাড়া বিশেষ কিছু নেই।
দাদু কী ছবি আঁকছেন পিকু একটু দেখার চেষ্টা করতেই কুট্টিদাদু ক্যানভাসটা পিকুর দিকে ঘুরিয়ে দিলেন।
“বলো তো দাদুভাই এটা কিসের ছবি?”
ছবিটার নীচে লেখা তৎ ত্বম্ অসি। পিকু কিছুক্ষণ ভালো করে দেখে বলল, “যা লেখা আছে তাতে তো মানে দাঁড়ায় তুমিই সব!” দাদু বলে উঠলেন “এক্স্যাক্টলি!” সঙ্গে সঙ্গে ঋতজা বলে উঠল “জানো দাদু, ও অনেক কিছু জানে! যেরকম ভালো পড়াশোনায় তেমনি ভালো গোয়েন্দা। ও জানো কত কঠিন কঠিন সব মিস্ট্রি সলভ করেছে!”
পিকু বললে উঠল, “না না ও সব কিছু না। ও একটু বেশি কথা বলে তাই বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলছে।”
দাদু বললেন “উরেব্বাস! সেসব গল্প তো তাহলে শুনতেই হবে দাদুভাই! তবে জানো তো, আমার এই ঘরেও একটা মিস্ট্রি আছে। এখন কিছু বলব না, পরে সুযোগ মতো বলা যাবে‘খন।”
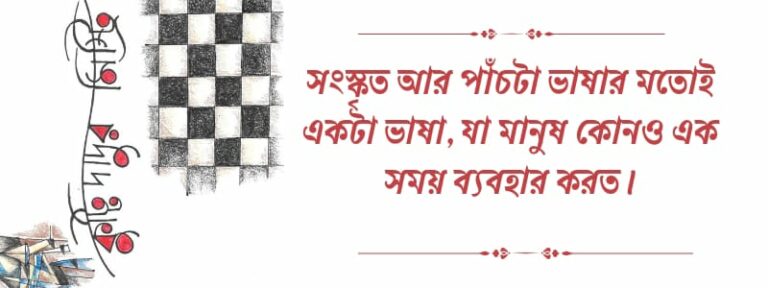
পিকু বলল,”দাদু, যদি কিছু মনে না কর তাহলে একটা প্রশ্ন করতে পারি? “অবশ্যই!” দাদু বললেন। “আচ্ছা, তুমি যে এই ছবিটা আঁকছ এর মানে কী? আসলে যে কোনও সৃষ্টির মধ্যেই তো একটা বক্তব্য থাকে, তাই আমার প্রশ্ন এই ছবিতে তোমার কী বক্তব্য, যদি একটু বুঝিয়ে বল!” পিকু জিজ্ঞাসা করল।
“অবশ্যই এর একটা মানে আছে। তবে সেটা বোঝাতে গেলে তো দাদুভাই অনেক কথা বলতে হয়। তোমাদের কি আর সে সব শুনতে ভালো লাগবে!”
সবাই মিলে ইনসিস্ট করাতে কুট্টিদাদু শুরু করলেন, “তোমরা কেউ অদ্বৈত বেদান্তের কথা শুনেছো? পিকুরা বলল, শব্দটা শুনেছে কিন্তু কোনও পরিষ্কার ধারণা নেই। “তাহলে তো তোমাদের একটু বিশদেই বলতে হয়।” কুট্টিদাদু বলতে শুরু করলেন।
“আমাদের মুনি ঋষিরা যে বেদ উপনিষদ লিখে গেছেন তার ব্যাপ্তি বিশাল। কেউ কেউ বলে, আদি শঙ্করাচার্য বা তারও আগে কেউ বেদ উপনিষদের থেকে জিস্ট করে অদ্বৈত বেদান্তের সৃষ্টি করেন। বেদ উপনিষদের যে মূল বক্তব্য তা এই বেদান্তেই বলা আছে। এদের মধ্যে দুএকটা যেমন দৃক দৃশ্য বিবেক বা বিবেক চূড়ামণি ইত্যাদি।
দৃক দৃশ্য বিবেক মানুষকে বলার চেষ্টা করে তুমি কে? আর বিবেক চূড়ামণি জীবন মুক্তি নিয়ে আলোচনা করে, বোঝানোর চেষ্টা করে তুমি এবং জীবন ভিন্ন। তোমার থেকে জীবনকে মুক্ত করতে পারলেই তুমি স্বতন্ত্র, তুমি মুক্ত।সবচাইতে ইন্টারেস্টিং হচ্ছে এই পুরো বক্তব্যের মধ্যে কোথাও ভগবান, স্বর্গ বা ওই ধরনের কোনও ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে আলোচনা নেই। তোমরা কেউ ভগবানে বিশ্বাস কর?” কুট্টিদাদু জিজ্ঞাসা করলেন। মেঘনা একটু হ্যাঁ বলার চেষ্টা করলেও বাকিদের সমবেত “না”তে সে চুপ করে গেল। দাদু আবার শুরু করলেন, “তবে গোড়াতে একটা কথা বলি, সংস্কৃত শুনে ভেবো না এর কোনও অলৌকিক মাহাত্ম্য আছে! ব্যাপারটা আদৌ তা নয়। সংস্কৃত আর পাঁচটা ভাষার মতোই একটা ভাষা, যা মানুষ কোনও এক সময় ব্যবহার করত। ব্যাস, এর বাইরে আর কিছু নয়।
ছান্দ্যোগ্য উপনিষদের একটা গল্প বলি শোনো, উদ্দালক তার ছেলে শ্বেতকেতুকে বারো বছরের শিক্ষা গ্রহণের পর জিজ্ঞাসা করলেন, “আচ্ছা বল তো, কী সেই প্রশ্ন যার উত্তর জানলে সবকিছুই জানা হয়ে যায়?” শ্বেতকেতু অনেক চেষ্টা করেও যখন উত্তর দিতে পারল না, তখন উদ্দালক বললেন— “তৎ ত্বম্ অসি । অর্থাৎ, তুমি যদি নিজেকে জানতে পারো তাহলেই সব জানা হয়ে যায়। অতএব নিজেকে জানাটাই জীবনের সবচেয়ে বড় কাজ। যদি নিজেকে জানতে পারো, তাহলে জানবে তোমার আর কিছুই জানার বাকি নেই। বড় কঠিন কাজ। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন– “আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না!”
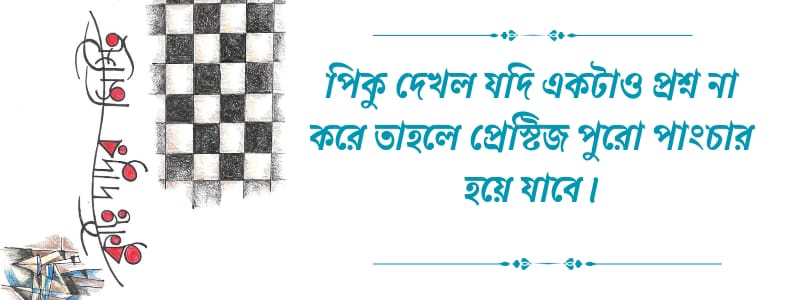
এইসব বলে কুট্টিদাদু একটু থেমে বললেন, “তোমরা নিশ্চয়ই খুব বোর হলে! তবে হ্যাঁ, আমি এক বাক্যে স্বীকার করছি, তোমরা খুব ভালো শ্রোতা। তোমাদের কোনও প্রশ্ন নেই?”
সবাই কীরকম ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। পিকু দেখল যদি একটাও প্রশ্ন না করে তাহলে প্রেস্টিজ পুরো পাংচার হয়ে যাবে। তাই জিজ্ঞাসা করল, “আচ্ছা দাদু, শুনেছি গীতার মূল বক্তব্য বেদ আর উপনিষদ থেকেই নেওয়া। তাহলে গীতায় শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে বারে বারে ভগবান বলে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করলেনই বা কেন, আর তা প্রমাণ করতে অর্জুনকে নিজের বিশ্বরূপই বা দেখালেন কেন?”
“হুম। ইন্টেরেস্টিং! আসলে কী জানো, সবটাই স্বার্থসিদ্ধির জন্যে। অর্জুন যখন কিছুতেই যুদ্ধ করতে রাজি হচ্ছিল না নিজের আত্মীয় পরিজনের বিরুদ্ধে, তখন শ্রীকৃষ্ণ ওইসব করতে শুরু করেন। এমনকি এই লোভও দেখান যে, অর্জুন যুদ্ধে মারা গেলে স্বর্গে স্থান পাবে আর জীবিত অবস্থায় জিতে গেলে রাজার সুখ উপভোগ করবে। দুটোই লোভনীয়। অথচ এই কৃষ্ণই বলছে কর্ম কর, কিন্তু কর্মের ফল নিয়ে কিছু আশা কোরো না। তাই আমি উপনিষদে বিশ্বাস করি, যেখানে ভগবান, স্বর্গ এই সবকিছুর থেকেও নিজেকে চেনা বা জানার ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে।”কুট্টিদাদু কথাগুলো একনাগাড়ে বলে গেলেন।
এইসব কথাবার্তার ফাঁকে ঋতজা নীচ থেকে ঘুরে এসে বলল, “চলো দাদু, পিসি সবাইকে খেতে ডাকছে।” নীচে এসে ওরা দ্যাখে বিশাল আয়োজন। ভাত, মুগের ডাল, বেগুনভাজা, আলু ফুলকপির ডালনা, দেশি পাবদার ঝোল, পাঁঠার মাংস, আমসত্ত্ব খেজুরের চাটনি আর শেষ পাতে মিষ্টি দই। খেতে বসে পিকুদের সঙ্গে ঋতজার পিসেমশাইয়ের আলাপ হল। ভীষণ শান্ত প্রকৃতির লোক। একদমই দাদুর মতন নয়।
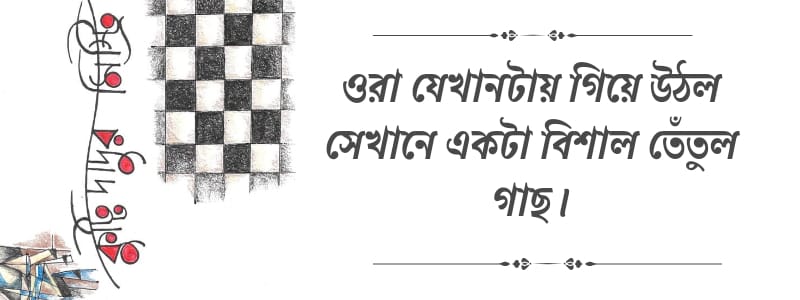
খাওয়ার জায়গা থেকেই দেখা যাচ্ছিল বাড়ির পিছন দিকে বেশ খানিকটা ঘেরা জায়গা আছে, আর তাতে আম, জামরুল, কাঁঠাল এইসব গাছের সারি। গাছের ফাঁক দিয়ে দূরে একটু গঙ্গাও দেখা যাচ্ছে।
খাওয়াদাওয়ার শেষে ঋতজা পিকুদের নিয়ে গঙ্গার পাড়ে ঘুরতে গেল। বাড়ির পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে দেড় দুশো মিটার গেলেই গঙ্গা। ভারী সুন্দর গঙ্গার পাড়টা। ওরা যেখানটায় গিয়ে উঠল সেখানে একটা বিশাল তেঁতুল গাছ। তারপরেই গঙ্গার পলির কাদা। পিকুরা তেঁতুল গাছটার তলায় গিয়ে বসল। চারিদিক নিস্তব্ধ, হালকা একটা ফুরফুরে হাওয়া বইছে, মাঝগঙ্গা দিয়ে দুএকটা সাদা পালতোলা নৌকা ভেসে যাচ্ছে, রোদ পড়ে গঙ্গার জল গলানো রুপোর মতো লাগছে— পাড়ে গঙ্গার ঢেউয়ের ধাক্কা খাওয়ার ছলাৎ ছলাৎ আওয়াজ। একটা দারুণ শান্ত পরিবেশ। কারুর মুখে কোনও কথা নেই। পিকু ঋতজাকে বলল, “এইরকম একটা অপূর্ব এনভায়রনমেন্ট আর একটা গান গাইবি না!”
ঋতজা গাইতে শুরু করল—
অমল ধবল পালে লেগেছে
মন্দ মধুর হাওয়া
দেখি নাই কভু দেখি নাই
এমন তরণী–বাওয়া!
দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে চলল। নদীর আশপাশ, এপার ওপার সব যেন কেমন ক্লান্তিতে ভরা। কোথাও কোনও তাড়া নেই। একটা নির্ধারিত ছন্দ মেনে সব ঘটে চলেছে, নদী তার মতো বয়ে চলেছে, দুটো নৌকা পাল ফেলে ওপারে ঘাটে নোঙর ফেলেছে, হাওয়াও কেমন যেন অনিচ্ছায় বয়ে চলেছে। মেঘনা ঘড়ি দেখে বলল চারটে বাজে, এবারে ওঠ।

বাড়িতে পৌঁছে সবাই একবার দাদুর সঙ্গে দেখা করতে গেলো। পিকুর মাথায় তখনও দাদুর ঘরের মিস্ট্রির কথা ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে এবার কুট্টিদাদুকে মিস্ট্রির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেই ফেলল।
দাদু বললেন “এখন তো বলা যাবে না দাদুভাই। তবে কথা দিচ্ছি, ঠিক সময় মতো তুমি আমার ঘরের মিস্ট্রি সলভ করার ডাক পাবে।”
পিকু কোনও উত্তর দিলো না, শুধু বেরোনোর সময় জিজ্ঞাসা করল, “দাদু আমি কি দুটো প্রশ্ন করতে পারি?”
“নিশ্চয়ই”! দাদু বললেন।
“প্রথম প্রশ্ন, কিউবিজম স্টাইলে আঁকা হুবহু একই রকম পাঁচটা ছবি কেন? আর দুটো দাবার বোর্ড সাজানো কেন?” পিকু জিজ্ঞাসা করল। “ওই যে বললাম, সবটাই তুমি সময় মতো নিজেই জানতে পারবে। আই প্রমিস।” দাদু হেসে বললেন।
পিকুরা ফেরার সময় ঋতজা আর ওদের সঙ্গে ফিরল না। ও পরেরদিন সকালে পিসির বাড়ি থেকেই শান্তিনিকেতনে ফিরে যাবে। সেদিন রাত্রে মিতু মানে ঋতজা, কুট্টিদাদু, পিসি, পিসেমশাই সবাইকে পিকুর গোয়েন্দাগিরির গল্প শোনাচ্ছিল। জয়সলমির আর রণথম্ভোরের ঘটনাগুলো তো বললোই, সঙ্গে আর যেগুলো ও জানে সেগুলোও বললো। দাদু শুনে শুধু বললেন “ছেলেটিকে দেখলেই বোঝা যায় খুব ইন্টেলিজেন্ট।”

সোমবার থেকে পিকুদের জীবন তথৈবচ। কোনও বৈচিত্র্য নেই। তবে মাঝেমধ্যেই পিকুর মাথায় কুট্টিদাদুর মিস্ট্রিটা ঘোরে। মাঝে একদিন পিকু মেঘনাকে নিয়ে সল্টলেক গিয়েছিল। ভালো খাওয়াদাওয়া হল। মেঘনার তো যত বয়স্কাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। ওদিকে দিদা আর বাড়িতে ঠাকুমা। দিদা বহু কষ্টে মেঘনা নামটা উচ্চারণ করতে পারলেও ঠাকুমা এতদিনেও ম্যাঘনার থেকে মেঘনাতে পৌঁছতে পারেননি। পিকু অনেক বুঝিয়েছে, কিন্তু ঠাকুমা মেঘনাকে দেখলেই ফোকলা দাঁতে হেসে ম্যাঘনা ম্যাঘনা করতে করতে ওকে জড়িয়ে ধরবেন।
এরই মধ্যে একদিন হঠাৎ ঋতজা মেঘনাকে ফোন করে জানালো কুট্টিদাদু নাকি খুব অসুস্থ, ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক হয়েছে, হাসপাতালে ভর্তি। তিনদিন হয়ে গেছে এখনও জ্ঞান ফেরেনি। ভেন্টিলেশনে আছেন। শুনে পিকুর মন খারাপ হয়ে গেল। খুব ইচ্ছে করছিল দাদুকে একবার দেখতে যেতে, মেঘনাই বারণ করল। বলল ঋতজার অনুপস্থিতিতে যাওয়াটা বোধহয় ঠিক হবে না। অবাক লাগল পিকুর। “আচ্ছা দাদুকে তো আমার ভালো লাগে, তার সঙ্গে ঋতজার উপস্থিতির কী প্রয়োজন!” পিকু বলল।
সেদিন রাত্রেই কুট্টিদাদু মারা গেলেন। দুদিন পরে ঋতজা ফোন করে মেঘনাকে দাদুর মৃত্যুসংবাদ দিল। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, দাদু নাকি কিছুদিন আগে ঋতজার বড় পিসিকে একটা খাম দিয়ে বলেছিলেন খামটা যেন উনি মারা গেলে তবেই খোলা হয়। এখন পিসি খাম খুলে দেখে তাতে লেখা—
“আমার মৃত্যুর পর আমার ঘরের কোনও কিছুতে হাত না দিয়ে মিতুর বন্ধু পিকুকে খবর দিও। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ও চেষ্টা করলে আমার ঘরের মিস্ট্রি সলভ করতে পারবে এবং তোমরা তাতে লাভবান হবে। আমার ঘরের একরকম করে আঁকা ছবিগুলোর মধ্যে একটা ছবি বিখ্যাত এক ফরাসি শিল্পীর আঁকা। সে ছবির এখন অনেক দাম হতে পারে। কাজেই আসল ছবিটা খুঁজে বের করতে পারলে তোমাদেরও অনেক লাভ হবে।”
শুনে তো পিকুর মাথায় হাত। “এটা দাদু কী করল! আমাকে শেষে ফাঁসিয়ে দিয়ে গেল!”

যাইহোক, পরদিন সকালেই ওরা চারজন বাঁশবেড়িয়া পৌঁছে গেল। শৌনও কলকাতাতেই, তাই সেও গেল সঙ্গে। ওরা বাড়িতে বলে গেল, যদি রাত্রে দেরি হয় ঋতজার পিসির বাড়িতেই থেকে যাবে।
কুট্টিদাদুর ঘরে ঢুকে পিকুর কীরকম মনে হল দাদু বুঝি এক্ষুনি এসে দাঁড়াবেন। ঘরের মধ্যে সেইসব গোছানো বা অগোছালো ভাব দুটোই আছে যা যেকোনও একটা দৈনন্দিন ব্যবহৃত ঘরে থাকে।
পিকুর দুটো জিনিসের ওপর প্রথম থেকেই নজর। দাবা আর কিউবিজম ছবিগুলো। পিকু দেখল সেই প্রথম দিনের মতোই একটা দাবার বোর্ড ইনট্যাক্ট সাজানো রয়েছে, কিন্তু অন্যটা দেখে মনে হচ্ছে কেউ খেলতে খেলতে উঠে গেছে। ঋতজার পিসেমশাই পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন “কিছু বুঝতে পারছ? বাবার কাছে আর মিতুর কাছে তোমার বুদ্ধির অনেক গল্প শুনেছি। বাবা তো বলেই গেছেন পারলে তুমিই পারবে। তবে তুমি না পারলে আমি এই ঘর এইভাবেই রেখে দেব। অন্য কাউকে আর হাত দিতে দেব না।”
“কথা দিতে পারছি না পিসেমশাই, তবে দাদু যখন বলে গেছেন একটা আপ্রাণ চেষ্টা তো আমি করবই। দেখা যাক। পারলে দুএকদিনের মধ্যেই বুঝতে পারব। আপনাদের কি কিছু মনে হচ্ছে?” পিকু বললো।
“নাহ, আমরা তো কিছুই বুঝতে পারছি না। তবে উনি ওই পাঁচটা ছবি নিয়ে খুব গর্বিত ছিলেন। বলতেন এরকম কেউ আঁকতে পারবে না। কিন্তু উনি যে কেন পাঁচটা হুবহু একই ছবি এঁকেছিলেন সেটা বলতে পারব না। তবে এখন তো দেখছি পাঁচটা নয়, চারটে আঁকা ওঁর, আর পঞ্চমটা কোনও এক বিখ্যাত ফরাসি শিল্পীর।”
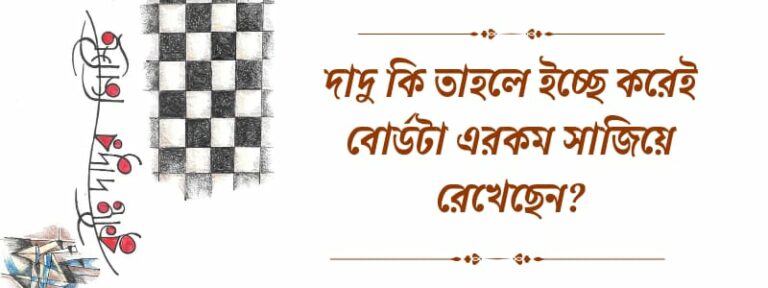
পিকু ভালো করে কুট্টিদাদুর ঘরটা দেখল, আর কোথাও কিছু অস্বাভাবিক আছে কিনা বোঝার জন্যে। তারপর একটা টুল টেনে নিয়ে তাতে উঠে ছবি পাঁচটা খুব ভালো করে কাছ থেকে দেখল। কোথাও কোনও তফাৎ নেই। হুবহু এক। হঠাৎ মনে পড়ল দাদুকে পিকু যখন এই ছবিগুলো আর দাবার কথা জিজ্ঞাসা করেছিল, দাদু এড়িয়ে গিয়েছিলেন। টুল থেকে নেমে পিকু অর্ধেক খেলা দাবার বোর্ডটা ভালো করে বোঝার চেষ্টা করল। সাদা ঘুঁটিগুলো খুব অল্প মারতে পেরেছে কালোরা। সাদার মোটামুটি অধিকাংশ ঘুঁটি বেঁচে আছে। আর কালোর অবস্থা বেশ শোচনীয়। রাজা একা দাঁড়িয়ে আছে, দূরে একটা ঘোড়া আর একটা গজ পড়ে আছে, আর সঙ্গে সর্বসাকুল্যে দুটি বোরে। তাদের কেউই কোনও ভালো পজিশনে নেই।
পিকু যতটুকু দাবা খেলা বোঝে তাতে এরকম সিচুয়েশন হওয়া প্রায় অসম্ভব। সবথেকে আশ্চর্য ব্যাপার হল, কালো মন্ত্রী প্রায় সাদা রাজার পাশেই বহাল তবিয়তে দাঁড়িয়ে আছে। নর্মাল খেলায় মন্ত্রী ওইভাবে বিপক্ষের শিবিরে ঢুকতে পারে না। খুব ভালো করে ভেবে দেখলে এ তো অলমোস্ট কিস্তিমাৎ। তাহলে দাদু এইভাবে বোর্ডটা ফেলে রাখলেন কেন?
আপাতদৃষ্টিতে পুরো বোর্ডটা দেখলে যেন মনে হচ্ছে কালো রাজা সবকিছু হারিয়ে কেমন অসহায় অবস্থায় একলা দাঁড়িয়ে আছে, আর সাদারা পূর্ণ শক্তি নিয়ে কালোর রাজত্ব দখল করতে চলেছে।
কিন্তু কালো মন্ত্রী! সে কী করে সাদাদের অত কাছে? তাকে অনায়াসে মেরে ফেলা যায়, অথচ সাদারা মারছে না। পিকুর মনে একটু খটকা লাগল। দাদু কি তাহলে ইচ্ছে করেই বোর্ডটা এরকম সাজিয়ে রেখেছেন? এটা কি কিছু ইঙ্গিত করছে? কালো মন্ত্রীর জায়গাটা সত্যিই খুব বিস্ময়কর। সাধারণ খেলাতে মন্ত্রীর ওইখানে পৌঁছে যাওয়াটা অস্বাভাবিক। তার মানে এটা দাবা খেলা নয়! দাদু নিজেই ঘুঁটিগুলো এইভাবে সাজিয়ে রেখেছেন। কিছু বলার চেষ্টা করেছেন। অপনেন্টের ঘরে কালো মন্ত্রী এইভাবে তখনই পৌঁছে যেতে পারবে যখন সে সাদাদেরই একজন। তার মানে মন্ত্রী কালো হয়েও সাদাদেরই সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে। আর রাজা অসহায়, কারণ মন্ত্রী বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। পুরোটাই এবার পিকুর কাছে পরিষ্কার হ’তে থাকল। তার মানে, এখানে ঘুঁটির রং আর পজিশন দুটোই ভীষণ ইমপর্টেন্ট, দাবা খেলাটা নয়। কুট্টিদাদু এখানে একটা বাস্তব সিচুয়েশন বোঝাতে চেয়েছে। সাদা ঘুঁটি রিপ্রেজেন্ট করছে বিদেশি শক্তি আর কালো ঘুঁটি মানে আমরা নেটিভ ইন্ডিয়ান্স। আর বিদেশিদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রী।
পিকু একটু জোরেই বলে উঠল সিরাজদৌলা-মীরজাফর। অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধ।
“কিন্তু এর সঙ্গে পাঁচটা ছবির কী সম্পর্ক?” পিকু পিছনে ফিরে দ্যাখে দরজায় পিসেমশাই দাঁড়িয়ে আছেন।
“সেটাই তো বুঝতে পারছি না।” উত্তর দিল পিকু।
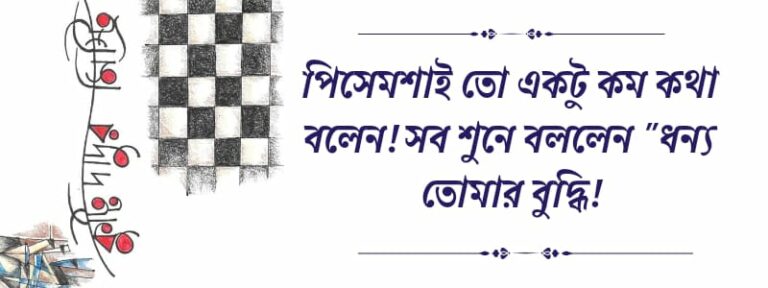
একটু পরেই ঋতজা এসে নীচে ডেকে নিয়ে গেল, পিসি খেতে ডাকছে। পিকু যখন কুট্টিদাদুর ঘরে ছিল, তখন ঋতজারা তিনজনে গঙ্গার পার থেকে ঘুরেও এসেছে। পিকু অবশ্য এতে কিছু মনেও করল না। পিকুর মাথায় তখন পলাশীর যুদ্ধ ঘুরছে। খাওয়া সেরে পিকু ওপরে গিয়ে আবার ভালো করে দাবার বোর্ডটা দেখতে লাগল। কোথাও বুঝতে কোনও গণ্ডগোল হচ্ছে না তো! দাবার ছকের ব্যাপারটা মোটামুটি কন্ফার্ম হ’য়ে পিকু বোঝার চেষ্টা করল এর সঙ্গে ছবির যদি কোনও যোগাযোগ পাওয়া যায়।
টুলে উঠে ছবিগুলোর উপর মোবাইলের টর্চের আলো ফেলে ভালো করে বোঝার চেষ্টা করল কোনও সাংকেতিক ইঙ্গিত পাওয়া যায় কি না। পিকুর ধৈর্যও আছে। অনেকক্ষণ ছবিগুলো দেখার পর পিকুর মনে হল প্রত্যেকটা ছবির কোনায় যেন একটা করে দুই ডিজিটের সংখ্যা লেখা আছে। এমনভাবে লেখা যে সংখ্যাটা পুরো ছবির অংশই মনে হচ্ছে। খুব কনফিউজিং।
পিকু আবার ভালো করে দেখল। একটা ছবিতে যেন মনে হচ্ছে ২৩ লেখা। আবার আরেকটা ছবি ভালো করে দেখল ২২, এইভাবে পাঁচটা ছবিতে ১৯ থেকে ২৩ অবধি সংখ্যা পেল। পিকু বোঝার চেষ্টা করল এই সংখ্যাগুলো কীসের ইঙ্গিত। ওদিকে পলাশীর যুদ্ধ, এদিকে ১৯ থেকে ২৩ অবধি সংখ্যা! কোনও কি লিংক আছে, নাকি পুরোটাই পিকুর মনের ভুল! সব কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে।
নীচে তখন ঋতজারা চুটিয়ে আড্ডা মারছে আর পিকু এদিকে খেটে মরছে। মেঘনাটাও ওদের দলে গিয়ে ভিড়েছে। পিকু একটু হতাশই হল। ঘরে আর কেউই নেই, পিকু একা। পিকু জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ালো। দূরে গঙ্গা দেখা যাচ্ছে। একটা স্টিমার যাচ্ছে। সত্যিই ভারী সুন্দর জায়গাটা। পিকু তো এখানে একাই সাতদিন কাটিয়ে দিতে পারে।
পিকু বোঝার চেষ্টা করল, দাবা আর ছবির মধ্যে সম্পর্কটা কোথায়। পিকু বিড়বিড় করে বলে উঠল, “ইফ মাই থিঙ্কিং ইজ রাইট, তাহলে ছবির গায়ে লেখা সংখ্যার সাথে পলাশীর যুদ্ধের একটা সম্পর্ক থাকতেই হবে।”

পিকু আবার ফিরে গেল দাবা আর ছবিগুলোর কাছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হ’য়ে গেল। ও দৌড়ে নীচে নেমে এসে ঋতজাকে বলল, “শোন, বোধহয় পেয়ে গেছি। আগে একটু ভালো করে চা খাওয়া দেখি!”
মেঘনা বলল “কী জানলি আমায় বলবি না?”
“কেন তুই তো আড্ডা মারতেই ব্যস্ত, তোর আর এসব জেনে কী হবে?” পিকুর গলায় অভিমানের স্বর। মেঘনা বুঝতে পারল কেস গণ্ডগোলের।
এর মধ্যে ঋতজা পিসির সঙ্গে মিলে চা নিয়ে এল। পিসি আর পিসেমশাইও এসে বসলেন।
চা খেতে খেতে পিকু ওদের পুরো ব্যাপারটা বলল। পিসেমশাই সব শুনে বললেন “সব বুঝলাম, কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের সঙ্গে ছবির কী সম্পর্ক?”
পিকু বলল, “আসলে ওই পাঁচটা ছবির মধ্যে চারটে ছবি দাদুর নিজের আঁকা আর একটা ছবি অরিজিনাল ফরাসি শিল্পীর আঁকা, যার দাম হয়তো আজকের বাজারে কোটি ছাড়িয়ে যেতেও পারে। চুরির হাত থেকে বাঁচাতেই দাদু এই পন্থা নিয়েছিলেন। এবারে বলি, কোনটা অরিজিনাল ফরাসি শিল্পীর আঁকা বুঝলাম কী করে!
পলাশীর যুদ্ধ হয়েছিল ১৭৫৭-তে। এই চারটে সংখ্যা যোগ করলে, ১+৭+৫+৭ = ২০ হয়। যে ছবিতে ২০ সংখ্যাটা আছে, সেটাই অরিজিনাল, বাকি সবগুলোই দাদুর আঁকা।”
পিসেমশাই তো একটু কম কথা বলেন! সব শুনে বললেন “ধন্য তোমার বুদ্ধি! বাবা ঠিকই বলে গিয়েছেন, পারলে তুমিই পারবে!”
পিসি পিকুর পিঠে হাত রেখে জিজ্ঞাসা করলেন “তুমি কী চাও বল!”
পিকু আর মেঘনা একসাথে বলে উঠল, “লুচি, বেগুনভাজা, পাঁঠার মাংস আর মিহিদানা।” সবাই মেঘনার দিকে তাকিয়ে হো হো করে হেসে উঠল।
— “কেন! পিকু তো এগুলো খেতেই ভালোবাসে তাই আমি বলে দিলাম!”
“না না তাতে কী হয়েছে, কিন্তু তাহলে তো রাত্রে থাকতে হবে! সকলে বাড়িতে বলে দাও, কাল সকালে বাড়ি যাবে!” পিসি বললেন।
ডিনারের পর ওরা চারজন মিলে ওপরে দাদুর পাশের ঘরে বসে সারা রাত আড্ডা মারল। সাথে ঋতজার গান আর শৌনর বাঁশি, আর দূরে চাঁদের আলোয় গঙ্গা দর্শন। দারুণ কাটল রাতটা।
অলংকরণ: পারমিতা দাশগুপ্ত
ছবি সৌজন্য: Needpix
পড়াশোনা করেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেডিয়ো ফিজিক্স বিভাগে। পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন তথ্য প্রযুক্তিকে। প্রায় এগারো বছর নানা বহুজাতিক সংস্থার সাথে যুক্ত থাকার পর উনিশশো সাতানব্বইতে তৈরি করেন নিজের তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা। বর্তমানেও যুক্ত রয়েছেন সেই সংস্থার পরিচালনার দায়িত্বে। কাজের জগতের ব্যস্ততার ফাঁকে ভালবাসেন গান-বাজনা শুনতে এবং নানা বিষয়ে পড়াশোনা করতে। সুযোগ পেলেই বেড়াতে বেরিয়ে পড়েন আর সেই অভিজ্ঞতা ধরে রাখেন ক্যামেরায়।