শেষপর্যন্ত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএ পড়া ভালোভাবেই শেষ করতে পেরেছিলাম। ১৯৭৮ সালের মাঝামাঝি কোনও এক সময় অনুভূমিক চেহারার কোষ্ঠীর মতো লম্বা মার্কশিট হাতে পেলাম। হবে না? ষোলো প্লাস এক সতেরোখানা পেপার যে! ৭০ শতাংশের কাছে নম্বর, প্রথম শ্রেণী এবং প্রতিটি পেপারেই ফার্স্ট ক্লাস। বাড়িতে মা-বাবা ভয়ে কাঁটা হয়ে ছিলেন। ভদ্রভাবে পাশ করে যাই, এইটুকুনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁদের চাওয়া। প্রথম হয়েছিল শর্মিলা বন্দ্যোপাধ্যায়, পরে অর্থনীতির যশস্বী অধ্যাপিকা। বয়স্কদের সেবা ও কল্যাণের জন্য প্রভূত কাজ ও করেছে। দ্বিতীয় হয়েছিল প্রেসিডেন্সির বিএ অনার্সে প্রথম স্থান পাওয়া অনিন্দ্য সেন। আইআইএম কলকাতার অধ্যাপক, আইআইএম রাঁচির ডায়রেক্টর, এখনও অধ্যাপনায় নিযুক্ত।
আরও উজ্জ্বল রত্ন সব আমাদের সহপাঠী ছিল। তাদের কথা পরে বলব। একহাজার ফুল মার্ক্সে ১ শতাংশ নম্বরের ব্যবধানে প্রথম থেকে তৃতীয়। মোটের উপর মন্দ নয় রেজাল্ট। তারওপর সোজাসুজি সহ-অধ্যাপক পদে নিযুক্তির সুযোগ। কিন্তু ততদিনে আমার মন পুরোপুরি অন্য দিকে চলে গেছে। পরিবারের উৎপাত আর শিক্ষা পরিমণ্ডলের নিস্পৃহ উদাসীনতায় এমএ-র পড়াশুনোর প্রকরণটি উপভোগ করতে পারিনি। তাছাড়া কলকাতার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে অধ্যাপনার কথাও তখন ভাবছি না আর। ১৯৭৭ আর ’৭৮-এর মধ্যে এমন সব ঘটনা ঘটেছে যা জীবনকে বেলাইন করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছি, যদিও ক্ষতবিক্ষত অবস্থায়।
এর বছর বারো পরে ভারত সরকারের সবেতন সাবাটিক্যালে ইংল্যান্ডের ইস্ট অ্যাংগলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ডেভেলপমেন্ট ইকনমিক্সে মাস্টার্স করতে গিয়ে দেখলাম, কলকাতার পড়াশুনো বিশেষ ভুলিনি। ইন্টারন্যাশনাল ইকনমিক্স আর থিয়োরি অব গ্রোথ ভালোই মনে আছে। পাবলিক সেক্টর ও প্রাইভেট সেক্টরের এফিশিয়েন্সির তুলনামূলক স্টাডি করে আমার লেখা থিসিস যথেষ্ট প্রশংসিত হল। ডিস্টিংশন পেয়ে এমএ ডিগ্রি পেলাম। প্রেসিডেন্সির দিনগুলি আবার মনে এল। এখানে পড়ায় নিখাদ আনন্দ। বিশাল লাইব্রেরি, অজস্র বই নেওয়া যায়, যথাসময়ে ফেরত দিতে ভুলে গেলে ফাইন অবশ্য বিকট। বই নিতে না চাইলে অনেক রাত পর্যন্ত লাইব্রেরিতে বসে পড়তে কোনও বাধা নেই।
একটা ঘটনা আমাকে অবাক করেছিল। ৭০ পার্সেন্ট পেলে ডিস্টিংশন পাওয়া যায়। আমি রেজাল্ট পেয়েছিলাম বিদেশেই, দেশে ফিরে মার্কশিট ডাকে পেয়ে দেখি আমার নম্বর ৬৮ পার্সেন্ট। অর্থাৎ প্রয়োজনের চেয়ে দু’ পারসেন্ট কম। ভাবলাম, নিশ্চয়ই ভুলে ডিসটিংকশন দেওয়া হয়েছে। বিবেকের দংশন। মহার্ঘ্য ইন্টারন্যাশনাল কল বুক করে ধরলাম কোর্সের হোতা ডক্টর রিজ় জেনকিনসকে। রিজ় হাসতে হাসতে বললেন, ভুল হবে কেন? তোমার থিসিসটা এত ভালো হয়েছিল যে, কমিটির সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, নম্বর একটু কম হলেও স্পেশাল কেস হিসেবে তোমাকে ডিসটিংকশন দেওয়া যায়। খুব অবাক হলাম। খুশিও। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবিচারের গ্লানি মন থেকে মুছে গেল অনেকটাই।

বিএ-র রেজাল্ট খারাপ হওয়ার পর বাড়ির সকলে আমাকে নিয়ে বিশেষ উদ্বেগে থাকতেন। পাছে হতাশায় আমি কোনও অঘটন ঘটিয়ে ফেলি। একদিন কাঁটাকল স্টপেজে বাসে উঠে দেখি, ছোড়দা। মায়ের নির্দেশে আমার গতিবিধি ফলো করছে। না, এই কারণে জীবন বিসর্জন দেবার পাত্রী আমি নই। যতই লিকলিকে রোগা হই, ইস্পাতে নির্মিত হৃদয়। যদিও ঐ সময় কিছু সহপাঠীর রেজাল্ট নিয়ে অযাচিত মন্তব্য খুব পীড়া দিত। তবে তা তো যে কোনও কলেজেই হয়ে থাকে। আমি টিঁকে আছি দেখে মা আবার উঠেপড়ে লাগলেন বিবাহ নামক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আয়োজনে। তিনি নাকি আগেই জানতেন, আমি জেদ করে ভালো সম্বন্ধ পায়ে ঠেলার পরিণতি কী হবে। যা আশংকা ছিল, তাই হয়েছে। খারাপ রেজাল্ট ও শিক্ষাবিদ পরিবারের সঙ্গে শত্রুতার সম্পর্ক। বাবার রিটায়ারমেন্টের সময় এগিয়ে আসছে এবং তিনি আমার চাকরির জন্য কারও কাছে সুপারিশ করতে পারবেন না। কেনই বা করবেন, আমি তো এসব চাই না। সবই মায়ের মস্তিষ্ক-উদ্ভূত। কাজেই এবার সরাসরি চ্যালেঞ্জ— হয় চাকরি নয় বিয়ে, যে কোনও একটা বাছতে হবে এবং দ্রুত।
আমি তখন এমএ-র তৃতীয় সেমেস্টারে। তাতে কী? পড়াশুনো তো চলতেই থাকে। তার জন্য তো জীবনকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না! বিবাহযোগ্য কেউ ধারে কাছে চোখে পড়ল না। অতএব, চাকরির জন্যই রাজি হলাম। কোথায় চাকরি? তখনও বছর বছর অল বেঙ্গল ক্লার্কশিপ পরীক্ষা হত। অশ্রুপাত করতে করতে তাতে বসে নিখিল বাংলায় দুই বা তিন নম্বর জায়গা হাসিল করে (কিই বা লাভ?) রাইটার্স বিল্ডিংয়ে জুনিয়র ক্লার্ক হয়ে জয়েন করলাম। মাইনে ৪৮৮ টাকা। পুরোটাই মার হাতে তুলে দিতে হত। অনেক নতুন দশ আর একটাকার নোট থাকত, মনে আছে।
তারকবাবু নামের একজন অতি দয়াবান ভদ্র অফিস-হেডকে মনে আছে। হায়ার সেকেন্ডারিতে প্রথম হয়ে, বাড়িতে কোনও অস্বাচ্ছন্দ্য না থাকা সত্ত্বেও আমাকে জুনিয়র ক্লার্কের চাকরি করতে রাইটার্সে আসতে হচ্ছে, তাও এমএ-র পড়াশুনো চলার সময়, এই ব্যাপারটা তাঁকে খুব বিচলিত করত। যাঁর বিচলিত হওয়ার কথা, সেই মাতৃদেবী ছিলেন সিদ্ধান্তে অবিচল। বস্তুত, এই প্রাত্যহিক নির্যাতনের কোনওই অর্থ ছিল না আমাকে পদদলিত করা ছাড়া। এবং একইসঙ্গে চাপে রাখা, যাতে আমি আরও সফল হয়ে পরিবারের মুখ উজ্জ্বল করতে পারি।
তৃতীয় ও চতুর্থ সেমেস্টারের মাঝে কয়েকমাস ছুটি থাকে, যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস হয় না। সেই অবকাশটা বোধহয় আমার চাকরিতে আত্মবলিদান দেওয়ার জন্য তৈরি হয়েছিল। ছুটি ফুরোলে শেষ সেমেস্টার ও একটি ইন্টেগ্রেটেড পেপারের পরীক্ষা, যাতে বাকি সব পেপার থেকে প্রশ্ন থাকবে। কাজেই পড়াশুনোর প্রস্তুতি খুব ধারালো রাখতে হবে। ট্রামে করে ডালহৌসি গিয়ে আর বাড়ি ফিরে সব শক্তি নিঃশেষ হয়ে যেত। অফিসে ইচ্ছে থাকলেও পড়ার সুযোগ ছিল না। আর একজন সেকশন অফিসার ছিলেন, মানুষের খ্যাঁকশিয়াল সংস্করণ। তিনি হাতে বই দেখলেই তেড়ে আসতেন, সিট ছেড়ে নীচে লাইব্রেরিতে গিয়ে দেরি করলেও একই ব্যাপার। নিজের পরিবার যার বৈরী, তাকে অনাত্মীয় অপিরিচিত সেকশন অফিসার রেয়াৎ করবে কেন?
চারদশকের কিছু বেশি আগের এইসব ঘটনা। আরো পরে লিখলে হত, তবু এখনই লিখে রাখছি, পরে স্মৃতি যদি প্রতারণা করে। কিন্তু মাঝেমাঝেই মনে হচ্ছে, এ সব কি সত্যিই আমার জীবন? সত্যিই কি এক শিক্ষিত বাঙালি পরিবারে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম হওয়া, কবিতায় দীক্ষিত একটি মেয়েকে এইভাবে ভেঙেচুরে দেওয়ার নিরন্তর চেষ্টা হতে পারে? আসলে ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন পরিবার, সরকার, সমাজ, সর্বত্র একই পরিণতি আনে। পরিবারের বাইরের বাস্তব, ভবিষ্যতের ছবি দেখতে না পাওয়ার যে সীমাবদ্ধতা মায়ের ছিল, সেটা তাঁর জেদ আর নিয়ন্ত্রণ করার প্রবণতার সঙ্গে মিশে তৈরি করেছিল এক মারণ-ককটেল।

নিজে যে সব ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন, সেগুলি আমাকে দিয়েও করানো এবং একইসঙ্গে তিনি যা পারেননি, তা আমার মধ্যে দিয়ে সম্ভব করে তোলার পরস্পরবিরোধী ব্রত নিয়ে মা স্বৈরাচারী হয়ে উঠেছিলেন। হয় তাঁর মতে মত দেওয়া, নয় বিরোধিতা করা, এছাড়া অন্যদেরও পথ ছিল না। বাবা নিঃশব্দে আত্মসমর্পণ করেছিলেন, অশান্তি এড়ানোর জন্য। কিন্তু আমার জন্য তাঁর মন থেকে নিয়ত রক্তপাত হত। এত অন্যায়ের কোনও বৈপ্লবিক প্রতিবাদ আমি করতে পারিনি। দুটো কারণ ছিল। এক, কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। দুই, বাবা। আমার করা বিদ্রাহে মায়ের ইন্ধন আছে একথা সন্দেহ করে মা তাঁর উপর অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে তুলবেন।
তখন বাম সরকার সদ্য ক্ষমতায় এসেছে। কাঁটাকলে আমাদের থিয়োরি পড়াতেন অধ্যাপক অসীম দাশগুপ্ত। আমার কোনও ধারণাই ছিল না, তিনি কিছুদিন পরেই বামসরকারের অর্থমন্ত্রী হবেন। অসীমদা আমাকে স্নেহ করতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল বিল্ডিংয়ে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক নিয়ে এক সেমিনার আয়োজন করা হয়েছিল। তাতে তিনি আমাকে পাঠিয়েছিলেন। অপর বক্তাদের মধ্যে ছিলেন সইফুদ্দিন চৌধুরী। মনে পড়ে, অসীমদা আমার এই রাইটার্স পর্বকে ‘ছাত্রজীবন চলাকালীন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য অনিতার চেষ্টা’ বলে অন্য এক সতীর্থের কাছে উল্লেখ করেছিলেন প্রশংসাসূচকভাবে। তাতে অবশ্য আমার কষ্ট লাঘব হয়নি।
*ছবি সৌজন্য: Facebook, RTF
কলকাতায় জন্ম, বড় হওয়া। অর্থনীতির পাঠ প্রেসিডেন্সী কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কবিতা দিয়ে লেখক জীবন আরম্ভ। সূচনা শৈশবেই। কবিতার পাশাপাশি গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী, প্রবন্ধ, ছোটদের জন্য লেখায় অনায়াস সঞ্চরণ। ভারতীয় প্রশাসনিক সেবার সদস্য ছিলেন সাড়ে তিন দশকেরও বেশি সময়। মহুলডিহার দিন, মহানদী, কলকাতার প্রতিমা শিল্পীরা, ব্রেল, কবিতা সমগ্র , দেশের ভিতর দেশ ইত্যাদি চল্লিশটি বই। ইংরাজি সহ নানা ভারতীয় ভাষায়, জার্মান ও সুইডিশে অনূদিত হয়েছে অনিতা অগ্নিহোত্রীর লেখা। শরৎ পুরস্কার, সাহিত্য পরিষৎ সম্মান, প্রতিভা বসু স্মৃতি পুরস্কার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুবন মোহিনী দাসী স্বর্ণপদকে সম্মানিত। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমীর সোমেন চন্দ পুরস্কার ফিরিয়েছেন নন্দীগ্রামে নিরস্ত্র মানুষের হত্যার প্রতিবাদে। ভারতের নানা প্রান্তের প্রান্তিক মানুষের কন্ঠস্বর উন্মোচিত তাঁর লেখায়। ভালোবাসেন গান শুনতে, গ্রামে গঞ্জে ঘুরতে, প্রকৃতির নানা রূপ একমনে দেখতে।











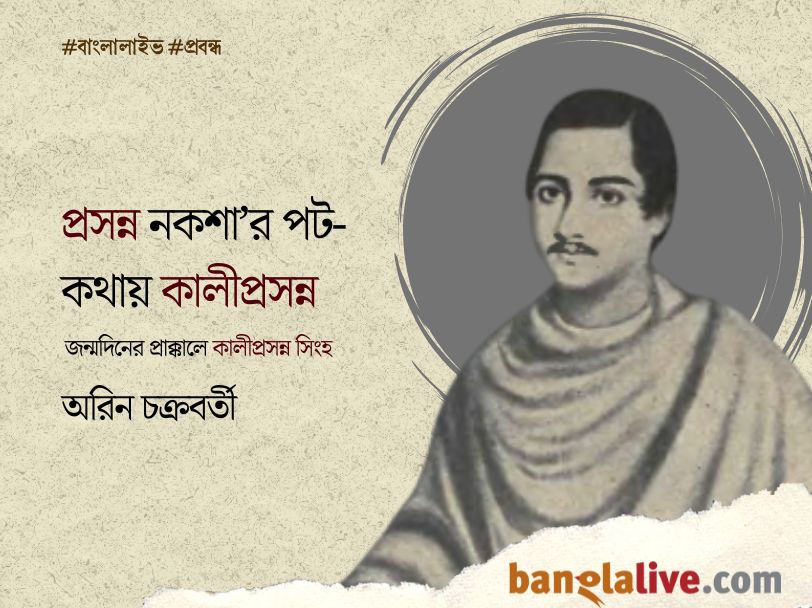






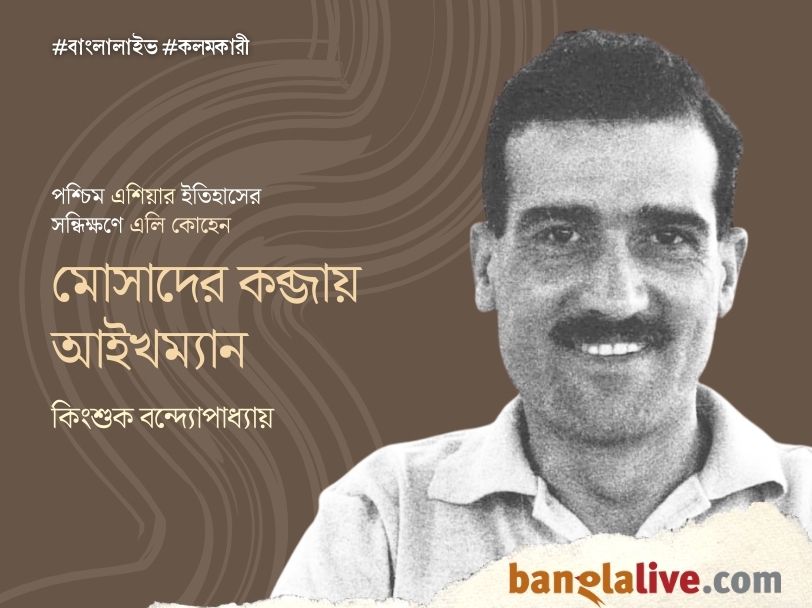







3 Responses
ভাল লাগছে আর কষ্ট হচ্ছে একইসঙ্গে।
তবে সবটা বলার নয়। মনের মধ্যে জমছে বেশিটাই।
ভালই লেখেন আপনি । অফিসার হিসেবেও সৎ, সাহসী ছিলেন। কিন্তু মায়ের এমন আচরণ !
শর্মিলা দি আমারও দিদিমনি ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম কম, এম বি এ ক্লাসে ৮২ থেকে ৮৬। মহুয়া দিও ছিলেন একই সংগে ।