সব সময়ই মনে হয়, এমন কোনও নবীন কবি কি কোথাও রয়ে গেছেন, যাঁর কবিতা আমাকে মুগ্ধ করবে, অথচ যাঁর একটি লেখাও আমি এখনও পড়িনি? এই সন্দেহ যে সত্যি সে কথা আবারও বুঝতে পারলাম– না, কোনও কাব্যগ্রন্থ পড়ে নয়– লিটল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত কবিতা খুঁজতে খুঁজতে। কোনও কোনও নবীন কবি নিশ্চয়ই আছেন, যাঁরা লেখা শুরু করামাত্রই পরপর কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করে চলেছেন– তাঁদের বইও পড়ি। কিছু ভালো লেখা সেখানেও পাই। কিন্তু কাব্যগ্রন্থে নিজেকে প্রকাশ করার সঙ্কোচ এখনও দূর করতে পারেননি এমন কোনও কবি কি নেই, যাঁকে খুঁজে পেতে হবে লিটল ম্যাগাজিনের পৃষ্ঠা থেকে? তেমনই একজনকে হঠাৎ পেয়ে গেলাম একটি ক্ষুদ্র পত্রিকার মধ্যে।
দেখে যুগপৎ বিস্মিত ও হতচকিত হলাম। এমন সব কবিতা এই সম্পূর্ণ অচেনা কবি লিখে রেখেছেন, অথচ আমি তা জানতে পারিনি! নিজের উপর ধিক্কার জন্মালো। কলেজ স্ট্রিটের সর্বাপেক্ষা পরিচিত লিটল ম্যাগ স্টল ‘ধ্যানবিন্দু’ তো বটেই, সেই সঙ্গে ইতিকথা, বইয়ের ঠেক, পাতিরাম, এসব স্টলে খোঁজ নিতে পাঠালাম এই কবির কোনও কাব্যগ্রন্থ পাওয়া যায় কিনা জানতে। না, পাওয়া গেল না। স্টলে যাঁরা বসেন তাঁদের সহায়তায় অনেক নতুন কবির সন্ধান পাই। কিন্তু এই বিশেষ কবির ক্ষেত্রে আমার কাছে মাত্রই পত্রিকায় ছাপা কয়েকটি কবিতার উপর নির্ভর করতে হল। নতুন কবির খোঁজ পেলে মন আনন্দে পূর্ণ হয়ে ওঠে। পাঠককে এই অচেনা কবির কয়েকটি কবিতা তাহলে পড়তে দিই, কেমন?
কবিতা মায়ের
অস্থির দুপুর এই কবিতা মায়ের
অস্থির দুপুর মা’র নীল গ্রামে বাস
অস্থির দুপুর মাঠে ছুটোছুটি রোদ
শৈশবের মাটি আর দুঃখ লাগা ঘাস
সেই ঘাস থেকে সেই মাটি থেকে আমি
জন্মেছি কখন? এই কবিতা অস্থির
তোমাকে কীভাবে দেব শান্তির বাগান?
অন্নজল দুপুরের পাখি
চার লাইনের দুটি স্তবক। একদম নির্ভুল অক্ষরবৃত্ত ছন্দে বাঁধা। এক মাত্রাও বেশি-কম নেই কোথাও। কিন্তু ছন্দে বাঁধা বললাম তো এক্ষুনি? অথচ কবিতাটি বাইরের দিকে ছন্দের বন্ধন স্বীকার করে নিলেও ভেতরে ভেতরে মুক্তির দিকে ধাবমান। শেষ লাইনের পরে কোনও যতিচিহ্ন নেই। অর্থাৎ কবিতাটি চলছে, তখনও।
প্রথমেই যা বুকে তোলপাড় তোলে তা হল এই কবিতার নামকরণ। কবিতার নাম: ‘কবিতা মায়ের’। অর্থাৎ মায়ের জন্য লিখিত কবিতা। মা-কে নিয়ে বাংলায় অনেক স্মরণীয় কবিতা লেখা হয়েছে। যেমন শঙ্খ ঘোষ লিখেছিলেন তাঁর প্রথম বইয়ে একটি নাতিদীর্ঘ দু’পৃষ্ঠার কবিতা। যে লেখার এমন দুটি লাইন বহু পাঠকই মনে করতে পারবেন– ‘মাগো, আমার মা–/ তুমি আমার এ ঘর ছেড়ে কোথাও যেয়ো না।’ মধ্যবয়সে পৌঁছে এই শঙ্খ ঘোষই আবার লেখেন তাঁর বাবরের প্রার্থণা গ্রন্থে ‘কালযমুনা’ নামক কবিতায় এমন চারটি লাইন: ‘বেচিস না মা বেচিস না/ বেচিস না আমায়/ ওরাও ছিঁড়ে খাবে, না হয়/ তুই আমাকে খা…।’ তারও আগে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন: ‘মা বলে ডেকেছি তোকে, ভাষা!’ আর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় লেখেন তাঁর ‘উনিশশো একাত্তর’ নামের অবিস্মরণীয় কবিতা: ‘মা, তোমার কিশোরী কন্যাটি আজ নিরুদ্দেশ/ মা, আমার পিঠোপিঠি ছোট ভাইটি নেই/ নভেম্বরে দারুণ দুর্দিনে তাকে শেষ দেখি/ ঘোর অন্ধকারে একা ছুটে গেল রাইফেল উদ্যত।’ সেই কবিতায় ছিল ভাইকে খুঁজে বেড়ানোর এইরকম মর্মঘাতী লাইন: ‘মশাল জ্বালিয়ে আমি ভাগাড়ের হাড়মুন্ডে চিনব কি তাকে?’

নবীন পাঠকরা হয়তো মনে করতে পারবেন না, তাই অনেকেরই অত্যন্ত জানা একটি তথ্যের পুনরুক্তি করছি। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ ঢাকায় একটি ভয়ানক গণহত্যা সংঘটিত হয়। যে ঘটনার পরেই আল মাহমুদ, শামসুর রহমানের মতো সর্বজনমান্য কবিদের গোপন পথে চলে আসতে হয় কলকাতায়, নিজেদের প্রাণটুকু রক্ষা করতে। কারণ ওই গণহত্যার বলি কেবল সাধারণ নাগরিকরাই ছিলেন না– নিহতদের মধ্যে লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজিবীরাও ছিলেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের এই কবিতাটি লেখার আগের দশকে সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন ‘কাল মধুমাস’ নামক তাঁর দীর্ঘ কবিতা– যেখানে কবি তাঁর নিজের জন্মমুহূর্তে মায়ের বেদনাপ্রহর স্মরণ করেছেন শেষ লাইনটিতে পৌঁছে। সেই লাইন বলেছিল: ‘মা তখন আমায় নিয়ে যন্ত্রণায় নীল।’ সন্তানকে জন্ম দিচ্ছেন যে মা তিনি তো যন্ত্রণায় নীল হবেনই! চল্লিশ দশকের আরেক কবি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় লিখে গেছেন তাঁর বিখ্যাত কবিতা, যার নামই ‘জননী যন্ত্রণা’। সেই কবিতা সম্পূর্ণ হচ্ছে এই উচ্চারণে: ‘ক্ষুদিরামের মা আমার/ কানাইলালের মা/ জননী যন্ত্রণা আমার/ জননী যন্ত্রণা।’ আর শক্তি চট্টোপাধ্যায় তাঁর ‘হে প্রেম হে নৈঃশব্দ’ নামক প্রথম বইয়ে স্থান দিয়েছিলেন ‘জরাসন্ধ’ নামক এক কবিতাকে। যে কবিতা বলে: ‘আমাকে তুই আনলি কেন, ফিরিয়ে নে।’ আবার সত্তর দশকের প্রারম্ভে কবি তুষার চৌধুরির একটি কবিতায় ছিল এই রকম দুটি লাইন: ‘মা তুমি আবার বুনো ফুল হলে আমি শূন্য শুঁড়িখানা ছেড়ে/ পরাগরেণুতে নেমে যাব, আমি এরকম কাল কাটাবো না।’ অর্থাৎ বাংলা কবিতায় মা-কে বিষয়কেন্দ্রে রেখে অনেক স্মরণীয় কবিতাই লেখা হয়েছে– সামান্য দু-চারটি টুকরো লাইন আমি বললাম এখানে।
অথচ সম্পূর্ণ অচেনা এই নতুন কবির লেখায় ওই সব শ্রুতকীর্তি কবিদের মা-বিষয়ক লেখার কোনও ছায়াই পড়েনি। এমনকি কবিতাটির নামকরণ থেকেই এ-লেখাকে স্বতন্ত্র করে নিয়েছেন এই নবীন কবি। ‘কবিতা মায়ের’। অর্থাৎ এই পত্রিকায় নবীন কবিটির যে কবিতাগুচ্ছ ছাপা হয়েছে, তার সমস্ত কবিতাই মায়ের। এই বক্তব্য কত সংহত ভাষ্যে প্রকাশ পেল! ‘কবিতা মায়ের’। ছন্দ জানা থাকলে কবিতার মধ্যে অতিরিক্ত কথা প্রবেশ করার অবকাশ পায় না, যদি না ছন্দকে অভ্যাসে পরিণত করে কোনও কবি ছন্দ ও মিলের নানারকম খেলা দেখানোতেই মনোযোগী হয়ে পড়েন। যে কারণে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মতো কবিও শেষ পর্যন্ত কোনও মহৎ কাব্য-উচ্চারনে নিজের লেখাকে পৌঁছে দিতে পারেননি। অনেক সময় অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তও ছন্দ মিলের অতিরিক্ত ঝোঁক দ্বারা অনেক কবিতাকেই কৌশল-প্রধান করে তুলেছিলেন। যদিও উৎকৃষ্ট কবিতাও আমরা অলোকরঞ্জনের কাছে কম পাইনি।
আমরা যাঁর কবিতা নিয়ে এখন কথা বলছি সেই কবি নতুন। তিনি ছন্দের ক্রীতদাস হবেন কি হবেন না, সেই পরীক্ষা তাঁর জন্য অপেক্ষা করে আছে। আমরা তাকিয়ে থাকব তাঁর কবিতার যাত্রাপথের চরিত্রের দিকে। আপাতত আমরা দেখছি একটি অস্থির দুপুর, যার কবিতা আর কারো নয়– কেবল মায়ের। সে-মায়ের বাস কোথায়? এক নীল গ্রামে। প্রায় স্বপ্নের মতো এই নীল গ্রাম শব্দটির মধ্যে মায়ের অবস্থান। যে-গ্রামের ঘাসে দুঃখ লেগে আছে। সেই ঘাস, সেই মাটি থেকে এই সন্তান জন্ম নিয়েছে যেন– যে এই কবিতার কথক। সেই সূত্রে মা এখানে মৃত্তিকা ও ঘাসেও রূপান্তরিতা হলেন। তাহলে কি সেই কবিকথক মাতৃজঠর থেকে জন্ম নেননি? সে-কথক কেবল জানেন তাঁর কবিতা অস্থির। দেখুন পাঠক, কী অবলীলায় ‘অস্থির দুপুর’ বদলে গেল ‘কবিতা অস্থির’ এই শব্দে! কখন এই বদল দেখতে পাচ্ছি আমরা? দ্বিতীয় স্তবকের দ্বিতীয় লাইনের শেষে। প্রথম স্তবকের প্রথম লাইনে ছিল ‘অস্থির দুপুর এই কবিতা মায়ের’। আর দ্বিতীয় স্তবকের দ্বিতীয় লাইনে তার রূপ কি দাঁড়াল? ‘জন্মেছি কখন? এই কবিতা অস্থির।’ কেন কবিতা অস্থির হয়ে উঠল? কারণ তোমাকে, অর্থাৎ মাকে, কীভাবে এই কবিকথক দিতে পারবেন শান্তির বাগান, দিতে পারবেন ‘অন্নজল দুপুরের পাখি’– এই চিন্তার তাড়না কবিতাকে অস্থির করে তুলেছে। প্রকৃতপক্ষে শেষ লাইনটিতে ‘অন্নজল’ শব্দের পরেই ‘দুপুরের পাখি’ এসে ‘অন্নজল’-কে কেবল গ্রাসাচ্ছাদনের সীমায় আটকে না রেখে তাকে উড়িয়ে নিয়ে গেল। কোথায়? কোনও শান্তির বাগানে কি?
সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন ‘কাল মধুমাস’ নামক তাঁর দীর্ঘ কবিতা– যেখানে কবি তাঁর নিজের জন্মমুহূর্তে মায়ের বেদনাপ্রহর স্মরণ করেছেন শেষ লাইনটিতে পৌঁছে। সেই লাইন বলেছিল: ‘মা তখন আমায় নিয়ে যন্ত্রণায় নীল।’ সন্তানকে জন্ম দিচ্ছেন যে মা তিনি তো যন্ত্রণায় নীল হবেনই! চল্লিশ দশকের আরেক কবি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় লিখে গেছেন তাঁর বিখ্যাত কবিতা, যার নামই ‘জননী যন্ত্রণা’। সেই কবিতা সম্পূর্ণ হচ্ছে এই উচ্চারণে: ‘ক্ষুদিরামের মা আমার/ কানাইলালের মা/ জননী যন্ত্রণা আমার/ জননী যন্ত্রণা।’ আর শক্তি চট্টোপাধ্যায় তাঁর ‘হে প্রেম হে নৈঃশব্দ’ নামক প্রথম বইয়ে স্থান দিয়েছিলেন ‘জরাসন্ধ’ নামক এক কবিতাকে। যে কবিতা বলে: ‘আমাকে তুই আনলি কেন, ফিরিয়ে নে।’
পুরো কবিতাটি চার লাইন স্পেস চার লাইনে লেখা একটি অকটেভ। প্রথাগত ছন্দশিক্ষা এই জন্যে প্রয়োজন যে, সেই শিক্ষা সাহায্য করে কবিতাকে সংহত রূপে প্রতিষ্ঠা দিতে। ‘অস্থির দুপুর এই’– এইরকম ছিল কবিতাটির সূচনার আটমাত্রা। আর দ্বিতীয় স্তবকের দ্বিতীয় লাইনে সেই আটমাত্রা একটু অন্যভাবে এল, যখন লেখাটি বলল– ‘এই কবিতা অস্থির’। আগে দুই, পরে ছয়– এই হল মাত্রা সমাবেশ। প্রথম স্তবকের প্রথম লাইনে ‘অস্থির দুপুর এই’ দিয়ে কবিতা ছুটতে শুরু করেছিল। দ্বিতীয় স্তবকের দ্বিতীয় লাইনে সে-কবিতা যেন একটু বিরাম নিতে দাঁড়াল। তাই আগে দুই, পরে ছয় মাত্রা স্থাপিত এখানে। কেন যে এই কবিতা অস্থির, তা তো এইমাত্র বললাম– কারণ এই কবিকথক তাঁর মাকে শান্তির বাগান দিতে চান। কিন্তু কীভাবে দেবেন সে উপায় তাঁর ধারণায় নেই।
শান্তির বাগান লাভ করা কি মায়ের একান্ত দরকার? কীভাবে সেকথা বুঝবেন পাঠক? বুঝবেন যদি ‘কবিতা মায়ের’ পরে এই কবিতাগুচ্ছটির মধ্যে অন্য একটি কবিতায় পাঠকের চোখ পড়ে। সে-কবিতার নাম কী? কী বলছে সেই লেখা? পাঠকের সামনে তাহলে দ্বিতীয় কবিতাটি উপস্থিত করি:
দুটি ঘাসফুল
সকালে ঘরের কত কাজ
সারারাত স্বামীর প্রহার
মাথা থেকে রোজ রক্তপাত
মা ভাবে, এটাই তো সংসার
সহ্য করি, যেমন নিশ্চুপে
বজ্রপাত সহ্য করে দীঘি
কেননা ছেলেরা আজও ছোট
সহ্য করা উচিত আমার
তারপর ভোরবেলা, জল
মা’র বুকে দুটি ঘাসফুল
কী সবুজ আমি আর ভাই
ঘুমোচ্ছি তখন –
মা ডাকছে, এক্ষুনি উঠে পড়
কোথাও পালিয়ে যাই, চল!
এই কবিতাটি পড়তে পড়তে আমি বিস্ময়ে আকুল হয়ে ভাবি, এই অজানা নবীন কবি কীভাবে তাঁর কবিতায় এক এক স্তবকে এক এক রকম ‘আমি’-র ব্যবহার প্রয়োগ করেছেন। এই জন্য নিরুপিত ছন্দে স্তবকবন্ধ শিক্ষা করা কবিতালেখকের পক্ষে জরুরি। ধাপে ধাপে, স্তবকের পর স্তবক এসে কবিতাকে তার গন্তব্যে পৌঁছে দেয়। এই কবিতাটি বড় অপূর্ব এক বেদনাময় স্বাধীনতার গন্তব্যে পৌঁছেছে। কিন্তু সে-প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে বলা দরকার প্রথম স্তবকে আমরা কী পাচ্ছি। পাচ্ছি এক অল্পবয়সিনী জননীর কথা, যাঁর জীবনে স্বামীর প্রহার এক নিয়মিত ঘটনা। প্রথম স্তবকে কবিকথক তাঁর জননীকে দেখছেন যেন একটি দূরবর্তী স্থানাঙ্ক থেকে। ‘মা ভাবে, এটাই তো সংসার’। এই যে মা কী ভাবছে– সেই ভাবনাকে দেখে যাচ্ছে বড় ছেলে। বড় ছেলে কেন বললাম? কারণ শেষ স্তবকের আগের স্তবকে পাব এই লাইন– ‘কী সবুজ আমি আর ভাই’। দ্বিতীয় স্তবকে যে ‘আমি’-র ব্যবহার, তা ওই জননীর ‘আমি’। যে-জননী ভাবেন ‘সহ্য করা উচিত আমার’। কেন সহ্য করা উচিত? কারণ একটাই। ‘ছেলেরা আজও ছোট’।
এর পরের স্তবকে জননীর ‘আমি’ রূপান্তরিত হল কবিকথকের ‘আমি’-র পর্যবেক্ষণ শক্তির মধ্যে। ‘মা’র বুকে দুটি ঘাসফুল’– এই লাইনটি তুলনাহীন! কারণ দুটি ঘাসফুল একদিকে ‘আমি আর ভাই’– যারা ঘুমোচ্ছে তখন। অন্যদিকে সদ্যোজাত অবস্থা থেকে মায়ের স্তন্যপান করে তারা বালকবয়সে পৌঁছেছে। ‘মা’র বুকে দুটি ঘাসফুল’ নারীর স্তনকেও বোঝায়। দুদিকেই অর্থস্তর সংকেত পাঠাল ‘দুটি ঘাসফুল’ শব্দের অসামান্য প্রয়োগ। শেষ স্তবকটি মাত্র দু’লাইনের। ‘মা ডাকছে, এক্ষুনি উঠে পড়/ কোথাও পালিয়ে যাই, চল!’ স্বামীর অত্যাচার আর সহ্য করতে না পেরে নাবালক দুটি সন্তানকে নিয়ে যেদিকে দু’চোখ যায় সেদিকে চলে যেতে চাইছে এই মা। দেখা যাচ্ছে কবির ‘আমি’ যেভাবে নিজেকে প্রকাশ করেছিল, সেই ‘আমি’-কেই আবার নিয়ে আসছে শেষ স্তবকটিও। এইভাবে কবিতাটিতে একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ হচ্ছে।
এক্ষুনি বললাম, শেষ স্তবক। কথাটা ভুল বললাম কি? এই প্রশ্ন উঠতেই পারে। কেউ বলতেই পারেন, এই কবিতা তো এগিয়েছে, ধাপে ধাপে, চার লাইনের স্তবক-নিয়ম অনুসরণ করে। ওদিকে, শেষে তো রয়েছে মাত্র দুটি লাইন। তাহলে? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই চার লাইনের স্তবকপ্রথা স্বীকার করেই এই কবিতা অগ্রসর হয়ে এসেছে। কিন্তু চারের অর্ধেক কী? দুই। অর্থাৎ দুই লাইনের একক মান্য করে চলেছে এ কবিতা প্রথম থেকেই। বললামই তো দুই আর দুইয়ে চার। শেষ স্তবকটি এল উপসংহারের মতো। তাই এককের ক্ষুদ্রতম রূপটি আশ্রয় করা হল। দুই লাইনেই বলা হল স্বামীর নিত্য প্রহারে জর্জরিত মা তাঁর সন্তান দুটিকে নিয়ে পালিয়ে যেতে চাইছেন স্বামীর ঘর ফেলে।
এ কবিতা অক্ষরবৃত্তের দশ মাত্রা বজায় রেখে চলেছে প্রায় পুরোটাই। প্রায় বললাম কেন? কারণ পুরো কবিতাটির মধ্যে একটি লাইন আছে যেখানে দশ মাত্রার চেয়ে চার মাত্রা কম রাখা হয়েছে। কোথায়? তৃতীয় স্তবকের শেষ লাইনে। ‘ঘুমোচ্ছি তখন–’। ‘ঘুমোচ্ছি তখন’ কথাটির পরে একটি ড্যাশ আছে, চার মাত্রার স্বল্পতা পূরণ করতে চাইছে যেন ওই ড্যাশ। এইভাবে যতিচিহ্নও কখনও কখনও শব্দের বিকল্প হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হল, ‘ঘুমোচ্ছি তখন’ লাইনটিকে দশ মাত্রা পর্যন্ত না নিয়ে গিয়ে, চারমাত্রা কম রেখে ছেড়ে দিলেন কেন কবি?

এইখানেই বোঝা যায় তিনি ছন্দের দাসত্ব করছেন না। তাঁর বিষয়ের পক্ষে যতটুকু প্রয়োজন, কেবল ততটুকুই ব্যবহারে আনছেন ছন্দের নিয়মকে। ‘ঘুমোচ্ছি তখন’– অর্থাৎ যেহেতু ঘুমন্ত আছি সেই কারণেই তো আমি পুরো ব্যাপারটা দেখতে পাচ্ছি না! এই কবিতার বাকি সব কথা কিন্তু জাগ্রত ও সচেতন ‘আমি’র স্বরে উচ্চারিত। কখনও কবিকথকের ‘আমি’-র স্বর। কখনও জননীর ‘আমি’-র কণ্ঠ। কিন্তু যখন কেউ ঘুমন্ত, সবটুকু সে দেখবে কী উপায়ে? দেখতে তো পাচ্ছে না– তাই চার মাত্রা কম রাখা হল। অতুলনীয় এই সংযম ও ছন্দশাসন। পাঠকের মনে পড়তে পারে আগের কবিতাটির কথা, যা দুটি চার লাইনের স্তবকে রচিত। যেখানে সাতটি লাইনই চোদ্দো মাত্রায় সম্পূর্ণ হচ্ছে। কেবল শেষ লাইনটিতে আসছে দশ মাত্রা। চার মাত্রা কম এখানেও। কেন? কারন, ‘অন্নজল দুপুরের পাখি’– এই অন্নজল পর্যন্ত এসেই ‘দুপুরের পাখি’ শব্দ দুটির প্রয়োগ ‘অন্নজল’ কথাটিকে কল্পনাতীতের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। পাঠকের ভাবনা ওই দুপুরের পাখির পিছনে উড়ে যাক! কবি আর কেন লিখবেন? চার মাত্রা কম হবে? হোক। পাঠকের কল্পনাশক্তির উপর যথেষ্ট ভরসা আছে এই কবির। সবটুকু তিনি কবিতায় গোল গোল করে বলে দিতে চান না। যে বোঝার সে বুঝবে, কিন্তু আমি কবিতায় অতিরিক্ত সরলতা আনব না– কারণ অধিকতর পাঠক পাওয়ার লোভ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে হবে আমার মনকে।
সংকেতধর্মে এই নবীন কবির আস্থা আছে। তা নইলে তৃতীয় স্তবকের প্রথম লাইনে তিনি কেন লিখবেন: ‘তারপর ভোরবেলা, জল’? পাঠককে ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি, সঙ্গে সঙ্গে আমিও ভেবে চলেছি, ‘জল’ শব্দটি কেন এল এখানে? একটা সোজা উত্তর অবশ্য পাওয়া যায় যে কবিতার শেষ লাইনটি বলছে: ‘কোথাও পালিয়ে যাই চল!’ ‘চল’-এর সঙ্গে ‘জল’-এর একটি দূরাগত অন্ত্যমিল দেখা দিচ্ছে– সেই কারণেই কি এই নবীন কবি, ‘তারপর ভোরবেলা’ লেখার পর একটি কমার বিরাম নিয়ে ‘জল’ শব্দটি রাখলেন? মনে হয় না কেবল অন্ত্যমিল দেওয়ার লোভের বশবর্তী হয়েছেন এই কবি। সেই রকমই যদি তাঁর প্রবণতা হত, তাহলে ঘনঘন অন্ত্যমিলকে আসতে দেখতাম আমরা এই কবিতাগুচ্ছের মধ্যে। বরং এই কবি যখন অন্ত্যমিল রাখছেন, তখন সেই সব মিত্রাক্ষর এত দূরে দূরে সরানো থাকছে, যে প্রথম পাঠে ধরাই পড়ছে না। গোপন একটি ধ্বনিসাম্য শুধু শ্রুতির ভিতর পৌঁছে যাচ্ছে কবিতা পাঠের শেষে।
যে কথা বলছিলাম, ‘তারপর ভোরবেলা’ লিখে, একটি কমা দিয়ে এই কবি বসাচ্ছেন ‘জল’ শব্দটি। এই একটি শব্দের প্রয়োগ পূর্ণমাত্রায় সংকেতধর্মী। মনে রাখছি, ঠিক এর আগের স্তবকে রয়েছে একটি দীঘি। ‘যেমন নিশ্চুপে/ বজ্রপাত সহ্য করে দীঘি’। রয়েছে তো? রাত্রে মা ভাবছেন: ‘সহ্য করি’। ভাবছেন: ‘সহ্য করা উচিত আমার’। তারপর ভোরবেলা, অর্থাৎ রাত্রের এই ভাবনার পরে আসছে ভোর। বাড়ির কাছে কি একটি দীঘি আছে? তারই জল? সেই দিকে কি চলেছে সংকেত? অথবা, যখন তোলপাড় করে বন্যা আসে তখন বসতি জমি ঘরবাড়ি ডুবে যায় সেই তোলপাড়ে। কিন্তু বন্যা হয়ে যাওয়ার পর কী দেখা যায়? চতুর্দিকে শান্ত হয়ে আছে জল। মধ্যে মধ্যে জেগে আছে এক একটি বাড়ির মাথা। জেগে আছে গাছ ইতস্তত। কিন্তু জল তখন বেগহারা, স্থির।
জননীর জীবনে স্বামীর প্রহার ও অত্যাচার যেন ওই তোলপাড়– যা নির্ঘুম রাত্রে জননীর স্মৃতির মধ্যে হানা দেয়, অথচ রাত্রি পেরিয়ে যখন ভোরবেলা এল, তখন সব শান্ত। বালক দুটি ঘুমন্ত। মায়ের মনে ফিরে আসছে সাহস। সন্তানদের ঘুমন্ত মুখও কি দীঘির জলের মতো শান্ত ও স্থির নয়? ওই সন্তানরাই তো এই জননীর একমাত্র অবলম্বন। সেই জন্যই তাদের নিয়ে কোথাও পালিয়ে যাওয়া। আমি, ব্যক্তিগতভাবে, জল শব্দটির ব্যবহার কেন হল তার কোনও একটিই বিশেষ অর্থ ধরতে পারিনি। কিন্তু ‘তারপর ভোরবেলা, জল’– এই লাইনটির শেষে জল শব্দটি একটি প্রসারণ এনে আমাকে অভিভূত করেছে। এলিয়টের প্রবন্ধের এই বাক্য তো সকলেই জানেন যে, ‘জেনুইন পোয়েট্রি ক্যান কমিউনিকেট বিফোর ইট ইজ আন্ডারস্টুড’। ‘তারপর ভোরবেলা, জল’ লাইনটি তার প্রমাণ।
এই কবিতাগুচ্ছের পরের কবিতাটির নাম: ‘মাঝরাত্রে মা’। কবিতাটি বলি এইবার:
মাঝরাত্রে মা
এখন সেসব কথা রোজ
মাঝরাত্রে মনে পড়ে মা’র
রাঙা-ফিতে বিনুনি বিকেল
ছায়া-লুকোচুরি আর
পাড়ায় পাড়ায় ধুলোখেলা
এই শরীরেই ছিল তার
বিকেল গড়ানো ছোটবেলা?
এমন কবিতা পড়লে এক অনুপম মাধুর্যে মন ভরে ওঠে। মায়ের বালিকা থাকার সময়টি এসেছে এই কবিতার বিষয়কেন্দ্র হয়ে– যে বালিকা-সময় মায়ের মনে পড়ছে মাঝরাত্রে। ‘মাঝরাত্রে’ শব্দটি মূল কবিতার শরীরে কোথাও নেই। তাহলে কোথায় পাচ্ছি আমরা ‘মাঝরাত্রে’ শব্দটিকে? পাচ্ছি নামকরণে। একটি কবিতা রচিত হয়ে যাওয়ার পরেও কবিতালেখকের সামনে লেখাটির মধ্যে অধিকতর অর্থ যোগ করবার একটি সুযোগ থাকে। সেটি হল কবিতার নামকরণ। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের ‘একটি কথার মৃত্যুবার্ষিকীতে’ অথবা শঙ্খ ঘোষের ‘নিহত ছেলের মা’ এবং বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘আমার’ এইরকম তিনটি অসাধারণ নামকরণের দৃষ্টান্ত, যেসব ক্ষেত্রে কবিতার নামকরণই হয়ে উঠেছে যেন কবিতার আর একটি লাইন। যদি অলোকরঞ্জনের কবিতার নামকরণটিকে সরাসরি এইরকম না-ও বলা যায়, কিন্তু শঙ্খ ঘোষ ও বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা দুটির ক্ষেত্রে এটি অবধারিতভাবে বলা যায়।
সংকেতধর্মে এই নবীন কবির আস্থা আছে। তা নইলে তৃতীয় স্তবকের প্রথম লাইনে তিনি কেন লিখবেন: ‘তারপর ভোরবেলা, জল’? পাঠককে ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি, সঙ্গে সঙ্গে আমিও ভেবে চলেছি, ‘জল’ শব্দটি কেন এল এখানে? একটা সোজা উত্তর অবশ্য পাওয়া যায় যে কবিতার শেষ লাইনটি বলছে: ‘কোথাও পালিয়ে যাই চল!’ ‘চল’-এর সঙ্গে ‘জল’-এর একটি দূরাগত অন্ত্যমিল দেখা দিচ্ছে– সেই কারণেই কি এই নবীন কবি, ‘তারপর ভোরবেলা’ লেখার পর একটি কমার বিরাম নিয়ে ‘জল’ শব্দটি রাখলেন? মনে হয় না কেবল অন্ত্যমিল দেওয়ার লোভের বশবর্তী হয়েছেন এই কবি। সেই রকমই যদি তাঁর প্রবণতা হত, তাহলে ঘনঘন অন্ত্যমিলকে আসতে দেখতাম আমরা এই কবিতাগুচ্ছের মধ্যে।
এই নবীন কবিও তাঁর কবিতাটির শিরোনামে রাখলেন ‘মাঝরাত্রে মা’ শব্দ দুটি। অথচ কবিতার মধ্যে কোথাও রাত্রি এলো না। এ এক দুর্দান্ত প্রয়োগচিন্তা। কবিতার প্রতিটি শব্দই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেকথা ইতিমধ্যেই এই নবীন কবি বুঝে নিয়েছেন– অথচ তাঁর কোনও পরিচিতি এখনও তৈরি হয়নি আমাদের কবিতাসংসারে। যে জননী প্রত্যেক দিন স্বামীর প্রহার সহ্য করেন, তিনিই মাঝরাত্রে যখন জেগে থাকেন, পাশে দুটি সন্তান ঘুমোয়– তখন তিনি কী ভাবেন? যা ভাবতে পারেন কবির মা, সেই সব স্মৃতির টুকরো লিখে রেখেছেন এই কবিকথক। মা ভাবেন: ‘রাঙা-ফিতে বিনুনি বিকেল’। ভাবেন: ‘ছায়া-লুকোচুরি আর/ পাড়ায় পাড়ায় ধুলোখেলা’। এমনকী এই কথাও যেন ভাবেন: ‘এই শরীরেই ছিল তার/ বিকেল গড়ানো ছোটবেলা?’
আগেই বলেছি, কবিতাটির কোথাও রাত্রি নেই। কবিতার মধ্যে তাহলে কী আছে? আছে একটি বালিকার বিকেলবেলার খেলা। ‘রাঙা-ফিতে বিনুনি বিকেল’– অক্ষরবৃত্তের দশ মাত্রার এই ছোট্ট লাইনটি জননীর বাল্যসময় ফুটিয়ে তুলেছে নিখুঁত গতিময় চলচ্চিত্রের মতো। শেষ স্তবকে পৌঁছে আমাদের বুক মুচড়ে ওঠে যখন আমরা দেখি, মা যেন আজ এই স্বামীর প্রহার-জর্জরিত জীবনে পৌঁছে আর বিশ্বাসই করতে পারছেন না, তাঁর জীবনেও একটি ছোটবেলা ছিল! এই শরীরই সেই বাল্যসময় ধরে রেখেছিল একদিন!
এ লেখায় মাত্র সাতটি লাইন আছে। তার মধ্যে ছ’টি লাইনই দশ মাত্রার অক্ষরবৃত্তকে নির্ভুলভাবে অনুসরণ করে এসেছে। কেবল দ্বিতীয় স্তবকের দ্বিতীয় লাইনটি দু’মাত্রা কম রেখে আট মাত্রায় ছেড়ে দিচ্ছে নিজেকে– কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, আট মাত্রার লাইনটির শেষে কোনও যতিচিহ্ন নেই। এখানে এটাও বলে নেওয়া দরকার, পুরো কবিতাটির কোথাও কোনও যতি চিহ্ন রাখা হয়নি। কেবল শেষ লাইনে একটি জিজ্ঞাসাচিহ্ন আছে। ওই জিজ্ঞাসাচিহ্নে এসে পাঠকের মর্মে ধাক্কা লাগে– কারণ মা তো বিশ্বাসই করতে পারছেন না তাঁর জীবনে কোনও বালিকাসময় ছিল! দ্বিতীয় স্তবকের দ্বিতীয় লাইনটি আট মাত্রায় ছেড়ে দেওয়ার ফলে ওই জায়গায় কবিতাটির মধ্যে একটি দ্রুত গতিবেগ উৎপন্ন হয়েছে। শ্বাস-গতিবেগ। যেহেতু সব লাইনগুলি দশ মাত্রায় বাঁধা আছে, সেখানে হঠাৎ একটি লাইনে দু’মাত্রা কম পাওয়ায় আমরা অজান্তেই পরবর্তী লাইনের দশ মাত্রাকে ওই আট মাত্রার সঙ্গে যুক্ত করে নিই। অর্থাৎ যাঁরা কিছুমাত্র ছন্দ জানেন, তাঁরা ওই লাইনে দু’মাত্রা কম পেয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই পরবর্তী লাইনটিতে পৌঁছে ওই না-পাওয়া দু’মাত্রা সন্ধান করবেন। তার ফলে কী ঘটবে? দুটি লাইন যুক্ত হয়ে এক লাইনে পর্যবসিত হয়ে আঠেরো মাত্রার অক্ষরবৃত্তের মাপে ছুটে যাবে। অর্থাৎ অকস্মাৎ গতিবৃদ্ধি পাবে কবিতাটির।
কেন এখানে এরকম প্রয়োগ ঘটালেন কবি? কারণ, মা তাঁর সন্তানদের নিয়ে এই সময় যে-জীবনে বাস করছেন তা বদ্ধ, অত্যাচারিত। ঘরে ঘরে, এরকম অসহায় জননীদের আজও খুঁজে পাওয়া যাবে এই বাংলায়, যাঁরা মার খেতে খেতে স্বামীর ঘরে পড়ে আছেন। মধ্যরাত্রে তাঁদের কি মনে পড়ে না ‘রাঙা-ফিতে বিনুনি বিকেল’? পড়েই তো! মনে পড়ে লুকোচুরি খেলার সময় পাড়ায় পাড়ায় ছুটে বেড়ানো। ওই দৌড়ে যাওয়ার গতিকে ধরার জন্যই একটি লাইনে আচমকা দু’মাত্রা কম রেখে দুটি লাইনকে আঠেরো মাত্রার একটি লম্বা লাইনে রূপান্তরিত করে আমাদের শ্বাস নিতে বাধ্য করলেন কবি।
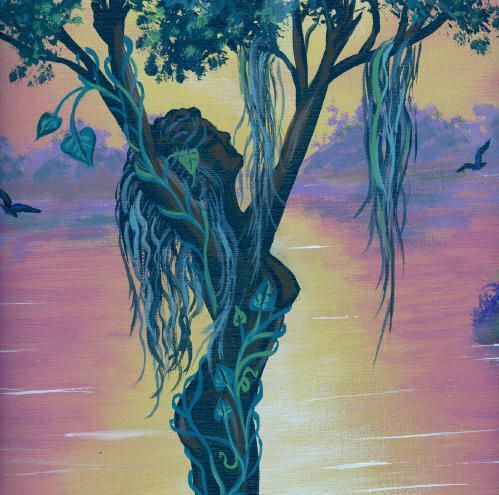
হ্যাঁ, ছন্দকে নিয়ন্ত্রণ করে শ্বাস। ছন্দ বা ‘রিদম’ কী? তার উত্তরে কবি এজরা পাউন্ড যা বলেছিলেন সেকথা পাওয়া যাবে ‘মডার্ন পোয়েটস অন মডার্ন পোয়েট্রি’ গ্রন্থে। পাউন্ড বলেছিলেন এই কথা, যে রিদম হচ্ছে ‘ওয়ার্ডস কাট ইনটু টাইম’। অর্থাৎ ছন্দবিজ্ঞানের মধ্যে যেমন মানুষের শ্বাস নেওয়া যুক্ত, তেমনই সময়যতিও যুক্ত। ‘ছায়া-লুকোচুরি আর পাড়ায় পাড়ায় ধুলোখেলা’– এই হঠাৎ দীর্ঘ হয়ে যাওয়া লাইনটি এক বালিকার পাড়ায় পাড়ায় ছুটে বেড়ানোর গতিকে ধরে রাখল। সার্থক সেই ছন্দ, যা কবিতার বিষয়বস্তুকে প্রকাশ করতে সাহায্য করে কোনও প্রকাশ্য কৌশল না দেখিয়ে, কিছুটা নির্লিপ্তভাবে। এখানে সেই কৌশলহীন নির্লিপ্তির পরিচয় রয়েছে। মাকে কি এই কবি ভালোবাসেন না? নিশ্চয়ই ভালোবাসেন। কিন্তু ছন্দপ্রকরণ তাঁর আয়ত্তে থাকায় তিনি একটি নির্লিপ্তির মধ্য দিয়ে ‘ছায়া-লুকোচুরি’ খেলার ওই দৌড় পাঠকের উচ্চারণে এনে দিলেন, কেবল একটি লাইনে প্রার্থিত দু’মাত্রা কম রেখে।
অবশ্য যাঁরা ছন্দ জানেন না, তাঁদের পক্ষে এই কবিতার সৌন্দর্য পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হবে না, তাতে সন্দেহ নেই। লুকোচুরি শব্দটির আগে ছায়া কথাটিকে হাইফেন দিয়ে যুক্ত করা হয়েছে কেন? আমার অনুমান, দুটি কারণ থাকতে পারে তার। প্রথমত লুকোচুরি খেলা তো নিজেকে আড়াল করার খেলা। সেই সূত্রে যেন এক অন্তরাল বা ছায়ায় ঢুকে পড়া। দ্বিতীয় কারণ হতে পারে, এতদিন পরে মাঝরাত্রে মা যখন সেই লুকোচুরি খেলার কথা ভাবছেন তখন মায়ের মনে হচ্ছে ওই লুকোচুরি খেলা, ওই পাড়ায় পাড়ায় দৌড়ে বেড়ানো– সবটুকু এই মাঝরাত্রে যেন এক ছায়াঢাকা স্মৃতির ধাবমানতা মাত্র। যেন বাস্তবে তা কোনওদিন ঘটেনি! এই গুচ্ছে আরো একটি কবিতা রয়েছে যার নাম ‘পরিজন’। সেই লেখাও পাঠকের সামনে নিয়ে আসি এবার:
পরিজন
বাতাস ভিক্ষুক। তার পথ
ভোরবেলা খঞ্জনীবাদক
ফুল তুলতে গিয়ে দেখি, গাছ
নিজেই মন্দির! কী অবুঝ
নিয়তি ঈশ্বর… তার গায়ে,
সমস্ত শাখায় ফুটে আছে
আমার মায়ের যত শোক!
স্নিগ্ধতা সম্পূর্ণ বজায় রেখেও কীভাবে একটি কবিতার শেষ শব্দ পর্যন্ত পাঠককে অপেক্ষা করিয়ে কবিতার মধ্যে দুঃখের আঘাত এনে দেওয়া যায়, এই কবিতাটি তার অভাবনীয় একটি দৃষ্টান্ত। কারণ ‘শোক’ কথাটি কবিতার মধ্যে আসবে আমরা তো ভাবতে পারিনি। কবিতা আরম্ভ হচ্ছে দুটি শব্দে: ‘বাতাস ভিক্ষুক’। তার পরেই পূর্ণচ্ছেদ। বাতাস কীরকম ভিক্ষুক এ কবিতায়? যে-বাতাসের পথ আসলে পথ নয়, খঞ্জনিবাদক।
কী আশ্চর্য সংকেতধর্ম নিয়ে কবিতার প্রথম দুটি বাক্য চলতে শুরু করল! বাতাস ভিক্ষুক, সে কথা ঠিক, কিন্তু এই ভিক্ষুকের কোনও হাহাকার নেই, কোনও দাবি নেই। বদলে কী আছে? আছে সঙ্গীত। পথে পথে, মফসসলে বা গ্রামে, এমন ভিক্ষুক আমি দেখেছি, যাঁরা খঞ্জনি বাজিয়ে ও গলায় গান নিয়ে, পল্লীর প্রতিটি গৃহের দ্বারে দ্বারে গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন। ভিক্ষা চাইছেন না মুখফুটে। কোনও গৃহিণী কিছু দিলেন, তো সেই দান ঝোলা এগিয়ে দিয়ে গ্রহণ করে কপালে হাত ছোঁয়ালেন, কিন্তু গান থামালেন না সেই ভিক্ষুক। এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন পরের গৃহস্থ বাড়ির দরজায়– হাতের খঞ্জনি বেজে চলেছে গানের সঙ্গে।
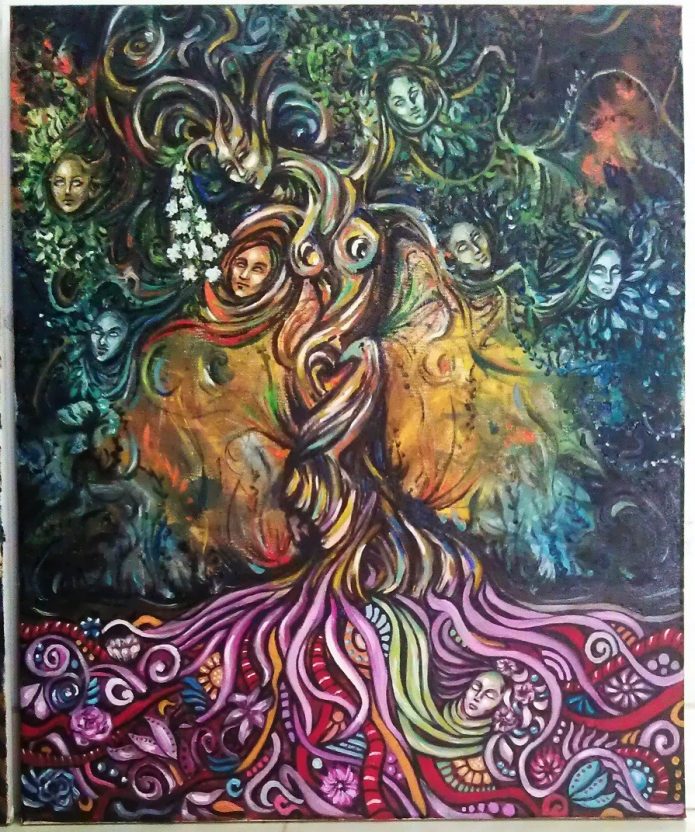
আমাদের এই নবীন কবির কাছে বাতাস যেন তেমনই এক ভিক্ষুক– যে বাতাস মাধুকরীর জন্য বেরিয়ে পড়েছে পথে, আর সেই পথই তার খঞ্জনিবাদক। এই দুটি লাইনের পরে রয়েছে একটি স্পেস বা বিরতি। তারপরে শুরু হচ্ছে দ্বিতীয় স্তবক। দ্বিতীয় স্তবকের আরম্ভে কবিকথক এগিয়ে এলেন। ফুল তুলতে গিয়ে কবির অভিজ্ঞতা দেখল গাছ নিজেই মন্দির! এও এক অপূর্ব সৌন্দর্যের কল্পনা। কবিতাটির মধ্যে, পাঠকদের প্রায় অগোচরে, একটি পূজার্চনাকে প্রবেশ করাচ্ছেন কবি। বাতাস ভিক্ষুক, কিন্তু তার পথ খঞ্জনিবাদক। খঞ্জনি কখন বাজে? নামগানের সময়। আর ফুল তুলতে গিয়ে কবি আবিষ্কার করছেন গাছ নিজেই মন্দির। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কবিতা রচনার ক্ষেত্রে পরিস্ফুট হচ্ছে। সে-বিষয়ে দু’চার কথা বলার লোভ সামলাতে পারছি না। এই কবির লেখা আগে একটি কবিতায় আমরা দেখলাম ‘তারপর ভোরবেলা, জল’– এই লাইনটি। অর্থাৎ প্রথম আট মাত্রার পরে একটি কমা দিয়ে বিরাম নেওয়ার পর ‘জল’ শব্দটি আসছে। আবারও এই কবিতায় দেখছি ‘ফুল তুলতে গিয়ে দেখি, গাছ’। তাহলে এখানেও প্রথম আট মাত্রার পরে প্রয়োজনীয় দু’মাত্রার আগে একটি কমা বসাচ্ছেন কবি। কিন্তু দুটি কমার প্রয়োগ কি একই কারণে?
না। তা নয়। ‘তারপর ভোরবেলা, জল’– এইখানে ‘জল’ শব্দটির সূত্র পরবর্তী লাইনে ঘুরে আসছে না কোনওভাবেই। ‘জল’ সেখানে একটি বিস্তার– প্রায় বাচ্যার্থ পেরিয়ে যাওয়া সংকেত এক। ঘুম ভেঙে ওঠার পর ভোরবেলা যে-শান্ত জল, তা দিঘি হতে পারে বা পুষ্করিণী, বলেছি আগে। নদীও হতে পারে। এখানে, জল এক শান্তিই যেন আসলে, যা রাত্রির অশান্তিময় ভাবনাগুলিকে সরিয়ে দিয়ে ভোরের সঙ্গে সঙ্গে জলের স্নিগ্ধতা দিচ্ছে। তাছাড়া ভোরবেলা উঠে আমরা মুখেচোখে ঠান্ডা জলের ঝাপটা দিই। তাতেও দেহমন সতেজতা পায়। কিন্তু ‘ফুল তুলতে গিয়ে দেখি, গাছ’– এই লাইনের কমা ব্যবহার সেরকম নয়। দুটি কমা ব্যবহারের উদ্দেশ্য পৃথক। যদিও দুটি ক্ষেত্রেই লাইনের প্রথম আট মাত্রার পরে কমা এসেছে, পরে দু’মাত্রা দিয়ে দশমাত্রার অক্ষরবৃত্তের ছন্দচলন অটুট রাখা হয়েছে। ‘ফুল তুলতে গিয়ে দেখি, গাছ’– এইখানে কিন্তু গাছ শব্দটির সূত্র ঘুরে আসছে পরবর্তী লাইনে। ‘তারপর ভোরবেলা, জল’ লাইনটিতে ‘জল’ শব্দ পরবর্তী লাইনে পৌঁছে তার বক্তব্য পূর্ণ করছে না। ‘গাছ’ শব্দ কিন্তু সে কাজ করছে। কারণ কবির চোখে– ‘গাছ/ নিজেই মন্দির!’
দু’জন প্রাতঃস্মরণীয় কবির রচনার অংশ এখানে পাঠকদের কাছে তুলে দেব– আমার বলার কথাটি অধিকতর স্পষ্ট করতে। ‘যাবার সময় হল বিহঙ্গের। এখনই কুলায়/ রিক্ত হবে।’ ‘প্রান্তিক’ কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাংশ সকলেরই খুব পরিচিত। কী বলতে চাইছি? বলছি, ‘যাবার সময় হল বিহঙ্গের’ তারপর পূর্ণযতি অর্থাৎ দাঁড়ি। পরক্ষণে আসছে– ‘এখনই কুলায়’। লাইন শেষ। অক্ষরবৃত্তের আঠেরো মাত্রায় ধরা লাইন। কিন্তু কথাটি ঘুরে পরের লাইনের প্রথমাংশে এসে নিজেকে সম্পূর্ণ করল: ‘রিক্ত হবে’। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স ৭৬। তিনি কি অক্ষরবৃত্তের আঠেরো মাত্রা নতুন শিখছেন যে মাত্রার মাপ নির্ভুল রাখতে ‘এখনই কুলায়’ শব্দ দুটি দিয়ে লাইনটি ছেড়ে দিলেন? তা যে নয়, সে তো বুঝতেই পারছেন আপনারা। তাহলে কেন ‘এখনই কুলায়’ কথাটিকে পূর্ণ করলেন পরের লাইনে ঘুরিয়ে এনে ‘রিক্ত হবে’ শব্দ দুটি বসিয়ে? কারণ ‘এখনই কুলায়’ কথাটি প্রথম লাইনের একদম শেষে রাখায় একটি সাসপেন্স থাকছে। ‘এখনই কুলায়’– তারপর? কিছু কি ঘটতে চলেছে? হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথ বলছেন ‘এখনই কুলায়/ রিক্ত হবে’। নিজের আসন্ন মৃত্যুর দিকে নির্দেশ করছেন রবীন্দ্রনাথ। ‘প্রান্তিক’ লেখার ঠিক আগেই একটি বড় অসুস্থতা পেরিয়ে এসেছেন তিনি। এই ‘প্রান্তিক’ কাব্যেই আমরা পাব এমন লাইন: ‘দেখিলাম অবসন্ন চেতনার গোধূলিবেলায়/ দেহ মোর ভেসে যায় কালো কালিন্দীর স্রোত বাহী/ নিয়ে অনুভূতিপুঞ্জ…’। অর্থাৎ নিজের দেহকে নিজেই দাঁড়িয়ে দেখছেন নদীজলে ভেসে যেতে। দস্তয়ভস্কির ‘দ্য ডাবল’ মনে পড়ে কি? ‘নোটস অন দ্য আন্ডারগ্রাউন্ড’ লেখাটির সঙ্গে একই মলাটের ভেতর এই ‘দ্য ডাবল’ এখন বেরিয়েছে পেঙ্গুইন থেকে। একই মলাটবন্দি অবস্থায় এখন পাওয়া যায় দস্তয়ভস্কির এই দুই যুগন্ধর রচনা।
আবার রবীন্দ্রনাথে ফিরে আসি। তাহলে ‘যাবার সময় হল বিহঙ্গের’– এই বিহঙ্গ কে? নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথ নিজেই। কোনও কোনও বাচিক শিল্পীকে আমি এ কবিতা মঞ্চে বলতে শুনেছি এইভাবে: ‘যাবার সময় হল বিহঙ্গের। এখনই কুলায় রিক্ত হবে।’ ‘কুলায়’ শব্দটির পর কোনও যতিচিহ্ন নেই, ঠিকই। কিন্তু আঠেরো মাত্রার মাপ তো ওখানে পূর্ণ হচ্ছে। তবে বাক্যাংশটি থামছে না। বাক্যাংশ থামছে পরবর্তী লাইনের প্রথমাংশে। অর্থাৎ ‘এখনই কুলায়’ শব্দটির পর একটি ‘অর্থযতি’ তৈরি করে দিচ্ছে আঠেরো মাত্রার অক্ষরবৃত্তের ছন্দের মাপ। তাই সাসপেন্স তৈরি হচ্ছে। সেইজন্যেই এই ‘অর্থযতি’ মান্য করা দরকার কবিতা পাঠ করার সময়।
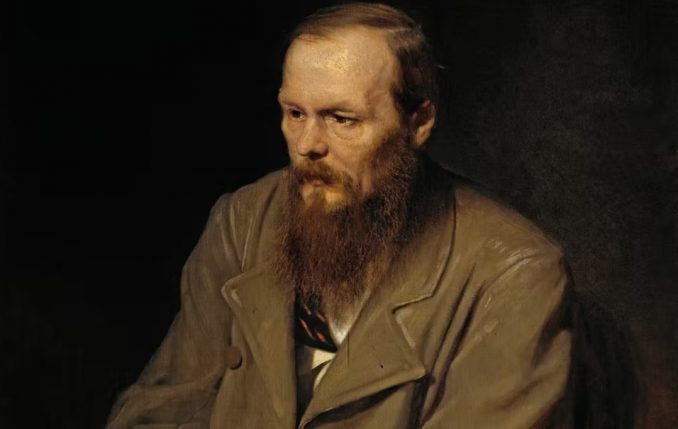
শক্তি চট্টোপাধ্যায় পরিণত বয়সে একটি কবিতা আরম্ভ করছেন এই রকম দুটি লাইন দিয়ে: ‘সন্ধ্যা হয়ে এল, তবু আমাকে ভর্ৎসনা/ কেন কর, সন্ধ্যা হল তবুও ভর্ৎসনা!’ এখানে অক্ষরবৃত্তের চোদ্দো মাত্রার চলনকে ব্যবহারে এনেছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়। ‘সন্ধ্যা হয়ে এল, তবু আমাকে ভর্ৎসনা’– এই ‘ভর্ৎসনা’ শব্দ একটি অর্থযতি তৈরি করে সাসপেন্স রাখছে। ‘ভর্ৎসনা’ কথাটির পর প্রথম লাইনে কোনও যতিচিহ্ন বসানো হয়নি। কিন্তু চোদ্দো মাত্রার মাপ ওই ‘ভর্ৎসনা’-তে এসে থামছে। তাই পরের লাইনটির প্রতি ধরে রাখছে পাঠকের কৌতূহল। সাসপেন্স। কী দেখা গেল? ‘…আমাকে ভর্ৎসনা/ কেন কর, …’। দ্বিতীয় লাইনে ‘কেন কর’ কথাটির পর একটি কমা বিদ্যমান। তারপর আবারো আসছে ‘সন্ধ্যা হল’ শব্দটি– পরক্ষণে আবারো ‘তবুও ভর্ৎসনা’ কথাটি লেখার পর দেখা যাচ্ছে একটি বিস্ময় চিহ্নকে। যাকে বলা হচ্ছে এই কথা, অনুমান হয় সে কোনও নারী– এই বলার আর্তি যেন বড় নম্রভাবে ফুটে উঠল এক করুণ জিজ্ঞাসায়। ছন্দ না জানলে অর্থযতি বিষয়ে কোনও ধারণাই তৈরি হয় না কবির এবং পাঠকের। তাই কবিতার মর্ম এবং সৌন্দর্যকে সম্পূর্ণভাবে অন্তরে ধারণ করার জন্য ছন্দশিক্ষা জরুরি। কেবল কবির পক্ষেই নয়, পাঠকের পক্ষেও জরুরি। কারণ ছন্দ কবিতার কোনও পোশাক বা অলংকার নয়। ছন্দ তৈরি হয় কবিতার বিষয়বস্তুর আত্মা থেকে। রবীন্দ্রনাথ এবং শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের যে দুটি কবিতাংশ তুলে দিলাম দুটি কবিতাই দুই কবি নিজেদের জীবনের সায়াহ্নে লিখেছেন।
তবে একেবারে নতুন যে কবির লেখা নিয়ে আজ কথা বলছি, তিনি রবীন্দ্রনাথ এবং শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের এসব কবিতা পাঠ করে অর্থযতির প্রয়োগ সুন্দরভাবে শিখে নিয়েছেন বোঝা যায়। ‘ফুল তুলতে গিয়ে দেখি, গাছ/ নিজেই মন্দির!’ প্রথম আট মাত্রার পর কমা। কিন্তু দশ মাত্রার মাপে পরের দু’মাত্রায় ‘গাছ’ শব্দটি এমনভাবে স্থাপিত হয়েছে যে পাঠকের কৌতূহল জাগ্রত থাকে। সাসপেন্স থাকে। পরবর্তী লাইনে পৌঁছে পাঠক বুঝতে পারেন, এই কবি একটি আবিষ্কার সম্ভব করেছেন এখানে। কী আবিষ্কার? ‘গাছ নিজেই মন্দির’। গাছ যে নিজেই মন্দির, তা কি আমি আগে পড়েছি কোনও কবিতায়? মনে তো পড়ছে না। ওই যে বলছিলাম, অলক্ষিতভাবে একটি পূজার্চনা এখনও পর্যন্ত বহন করছে এই কবিতা। বলা দরকার, এরপরেই পাচ্ছি আবারো ওই সাসপেন্স জাগিয়ে দেওয়া অর্থযতির ব্যবহার: ‘কী অবুঝ/ নিয়তি ঈশ্বর…।’ ‘কী অবুঝ’ শব্দটির পর কিন্তু কোনও যতিচিহ্ন বসানো হয়নি। ‘নিজেই মন্দির’ ছয় মাত্রায় এসে থেমেছে। লাইনটিকে দশ মাত্রায় নিয়ে যেতে আরো চার মাত্রা প্রয়োজন– তাই ‘কী অবুঝ’ এসে পড়ল।

পরবর্তী লাইন থেকে স্নিগ্ধমর্মসম্পন্ন এই কবিতা ঘুরতে শুরু করেছে কাঠিন্যের দিকে। কারণ, ‘কী অবুঝ’-এর পর কোন দুটি শব্দ পাচ্ছি আমরা পরবর্তী লাইনের প্রথমে? পাচ্ছি, ‘নিয়তি ঈশ্বর…’। এরপরেই আবারো ছয় মাত্রাকে দশ মাত্রার মাপে আনার জন্য প্রয়োজন হল আরো চার মাত্রার। তাই এল ‘তার গায়ে’। যদিও এখানে একটি কমা বসানো হয়েছে, তবু আমাদের মনে না হয়ে পারে না, ‘তার গায়ে’ কী? আবার কৌতূহল জাগানো, সাসপেন্স তৈরি করা। ‘তার গায়ে,/ সমস্ত শাখায় ফুটে আছে’– এই লাইনটির শেষে কোনও যতিচিহ্ন নেই। বরং লাইনটির পরেই একটি স্পেস বা বিরতি আসছে। ফলে সাসপেন্স দ্বিগুণ করা হল। বিরতির পরে কী পাব? সে উত্তরে যাওয়ার আগে দেখি এতক্ষন কী কী পেলাম কবিতাটিতে। পেলাম যে-গাছ নিজেই মন্দির বলে মনে হয়েছিল, সে-গাছই হল নিয়তি ঈশ্বর। এমন এক নিয়তি ঈশ্বর সেই গাছ, ‘যার সমস্ত শাখায় ফুটে আছে’– আবার বিরতি, এক্ষেত্রে স্পেসের প্রয়োগ দ্বারা বিরতি আসছে– এবং শেষ লাইনটিতে এসে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই গাছের, নিয়তি গাছের, সমস্ত শাখায় ফুটে আছে আমার মায়ের যত শোক। এই শেষ লাইনটি কল্পনাতীত বেদনার অভিজ্ঞতা এনে দেয়। যে গাছ মন্দির ছিল সেই গাছের সমস্ত শাখায় আমার মায়ের শোক ফুটে থাকতে দেখা গেল।
অতুলনীয় এই কবিতাগুলির লেখক তুষার বিশ্বাস। কবিতাজগতে সম্পূর্ণ অপরিচিত নাম। এঁর কোনও কবিতা পূর্বে পড়িনি তা আগেই জানিয়েছি। এই কবি যদি একাগ্র মনোনিবেশ সহকারে লিখে চলতে পারেন, তাহলে ভবিষ্যতে এঁর হাতে উৎকৃষ্ট কবিতাসম্পদ জন্ম নেবে। তবে একটি সাবধানবাণী জানিয়ে রাখি। আশা করব এই নবীন কবি আমার এই সাবধানবাণী দ্বারা কোনওভাবে আহত বা অপমানিত বোধ করবেন না। তার আগে বলে নেওয়া ভালো, এই সাবধানবাণীটি কিন্তু আমার বলা কথা নয়। কথাগুলি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের। শতাব্দীকালেরও বেশি আগে বঙ্কিমচন্দ্র নবীন লেখকদের উদ্দেশ্যে যা যা লিখেছেন তার কয়েক লাইন উদ্ধৃত করছি। আমার বয়স এই তুষার বিশ্বাসের চেয়ে অন্তত চল্লিশ বছর বেশি বলেই আমি তাঁকে উপদেশ দেওয়ার যোগ্যতা রাখি বলে মনে করি না। বঙ্কিমচন্দ্র কী বলেছিলেন সেটুকুই শুধু মনে করিয়ে দিতে চাই। বঙ্কিম লিখছেন:
‘যাহা লিখিবেন তাহা হঠাৎ ছাপাইবেন না। কিছুকাল ফেলিয়া রাখিবেন। কিছুকাল পরে উহা সংশোধন করিবেন। তাহা হইলে দেখিবেন রচনায় অনেক দোষ আছে। কাব্য, নাটক, উপন্যাস দুই-এক বৎসর ফেলিয়া রাখিয়া তারপর সংশোধন করিলে তাহা বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। যাহারা সাময়িক সাহিত্যের কার্যে ব্রতী, তাঁহাদের পক্ষে এই নিয়মরক্ষাটি ঘটিয়া উঠে না। এজন্য সাময়িক সাহিত্য লেখকের পক্ষে অবনতিকর।’
আমি, ব্যক্তিগত জীবনে, লেখাকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেছি। সে কারণে আমার লেখা সাহিত্যের পর্যায়ে উত্তীর্ণ হল না। কিন্তু এই নবীন কবির কাছে আমার অনুরোধ, লেখাকে জীবিকা করবেন না কখনও। দ্রুত বই প্রকাশ করার মোহে অনেক সময় খুব প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন কবির লেখাও নিরাশাজনক হয়ে পড়তে দেখেছি। যদিও লেখা তাঁদের জীবিকা নয়, তবু, ভিন্ন জীবিকা থাকা সত্ত্বেও অনেক কবি ও লেখককে দ্রুত লেখা প্রকাশের, বইপ্রকাশের দৌড়ে যোগ দিতে দেখেছি। শঙ্খ ঘোষের জীবনের দিকে যদি তাকাই তাহলে দেখব, শঙ্খ ঘোষ তাঁর প্রথম কবিতা ছাপা হওয়ার পর একুশ বছর সময় নিয়েছিলেন তিনটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করতে। পাশাপাশি, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম কবিতা ছাপা হয় ১৯৫০ সালে। এই কবির দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের প্রকাশকাল ১৯৬৭। অর্থাৎ লেখা প্রথম ছাপা হওয়ার পর দুটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করতে সময় নিয়েছেন ১৭ বছর। সুনীলের প্রথম কাব্যগ্রন্থ থেকে দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের সময়ের ব্যবধান দশ বছর। শঙ্খ ঘোষের প্রথম দুটি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে এগারো বছরের ব্যবধান। এঁরা আজ মহীরুহ, কিন্তু এঁদের প্রথম জীবন সাধনা এবং অনুশীলনের মধ্যে কতখানি নিয়োজিত ছিল, সেকথা বোঝা যায় তাঁদের প্রথম দিকের বইগুলির প্রকাশ তারিখের দিকে লক্ষ রাখলে। আশা করি এই নবীন কবি তুষার বিশ্বাস বঙ্কিমচন্দ্রের সাবধানবাণী স্মরণে রাখবেন।
*পরবর্তী পর্ব প্রকাশিত হবে ৫ সেপ্টেম্বর ২০২২
*ছবি সৌজন্য: Facebook, Artmajeur, Istock, Pinterest
জয় গোস্বামীর জন্ম ১৯৫৪ সালে, কলকাতায়। শৈশব কৈশোর কেটেছে রানাঘাটে। দেশ পত্রিকাতে চাকরি করেছেন বহু বছর। আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন দু'বার - ১৯৯০ সালে 'ঘুমিয়েছ ঝাউপাতা?' কাব্যগ্রন্থের জন্য। ১৯৯৮ সালে 'যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল' কাব্যোপন্যাসের জন্য। ১৯৯৭ সালে পেয়েছেন বাংলা আকাদেমি পুরস্কার। দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়িয়েছেন কবিতার সাহচর্যে। ২০১৫ সালে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক ডি.লিট পেয়েছেন।

























