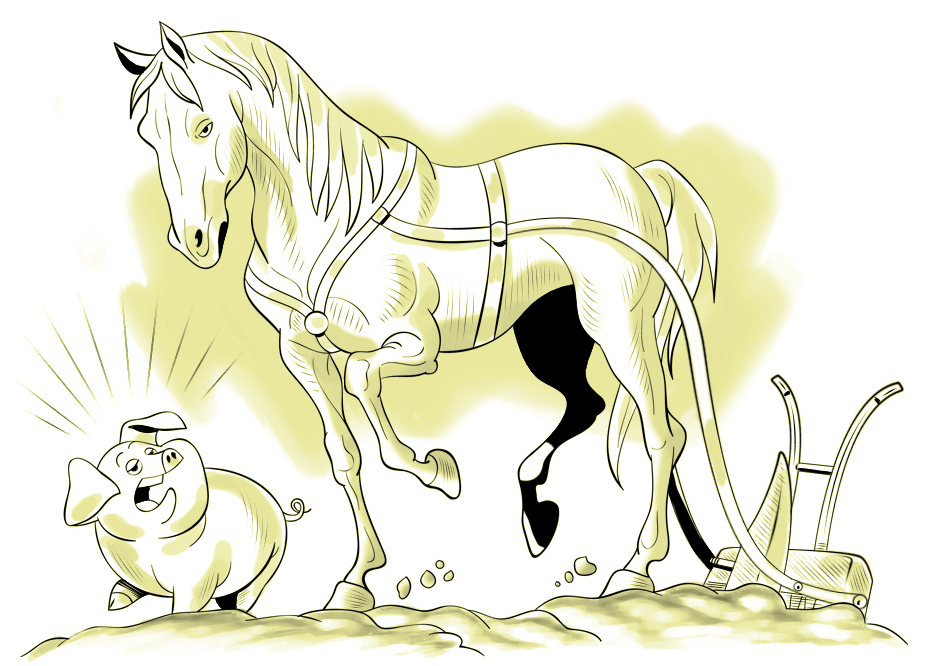শীত পড়ব পড়ব করছে, এমন সময় মলিকে নিয়ে শুরু হল মহা ঝঞ্ঝাট। সে প্রতিদিন সকালে দেরি করে কাজে আসে। কিছু বললে নানারকমের সাফাই গায়। কখনও বলে ঘুম ভাঙেনি, কখনও আবার শরীরে রহস্যময় সব ব্যথার কথা বলে। অদ্ভুত ব্যাপার, এত ব্যথা-ট্যথা সত্ত্বেও তার পেটপুজোয় কিন্তু কোনওরকম ভাটা পড়েনি। নানা অছিলায় কাজে ফাঁকি দিয়ে মলি টুক করে চলে যায় পুকুরপাড়ে, জলের কাছে। সেখানে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে বোকার মতো। তবে এসব তো কিছুই নয়, আজকাল কানাঘুষোয় মলিকে নিয়ে যেসব কথা শোনা যাচ্ছে, তা আরও সাংঘাতিক।
একদিন মলি আপনমনে খামারের উঠোনে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর তার লম্বা লেজ নাড়তে নাড়তে মহানন্দে খড় চিবুচ্ছে— এমন সময় ক্লোভার ঠিক তার পাশটিতে এসে দাঁড়াল। বলল,
– মলি, তোমার সঙ্গে খুব জরুরি কথা আছে। আজ সকালে আমি তোমাকে অ্যানিম্যাল ফার্ম আর ফক্সউডের বেড়ার ধারে দেখেছি। বেড়ার ওপারে মিস্টার পিলকিংটন-এর এক কর্মচারিও দাঁড়িয়ে ছিল। যদিও আমি অনেকটাই দূরে ছিলাম তবুও ও যে তোমার সঙ্গে কথা বলছিল সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। শুধু কথাই নয়, আমি এটাও দেখেছি যে তুমি বেড়াঝোপের ওপারে মুখ বাড়িয়ে রেখেছিলে আর লোকটা তোমার নাকে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে আদর করছিল। বলি, এসব কী হচ্ছে শুনি?
মলি সামনের দু’পা তুলে লাফাতে লাফাতে চিৎকার করে উঠল,
– না, না। মিথ্যে। সব মিথ্যে। সে কিচ্ছু বলেনি। আমিও ওসব কিছু করিনি।
ক্লোভার বলল,
– মলি, আমার দিকে তাকাও। শপথ করে বলো তো, লোকটা তোমার নাকে হাত বোলাচ্ছিল কিনা!
– মিথ্যে! সব মিথ্যে!
আরও পড়ুন: মন্দার মুখোপাধ্যায়ের তর্জমায় খলিল জিব্রানের ‘দ্য প্রফেট’
মলি ক্লোভারের চোখে চোখ রাখতে পারল না। মুহূর্তের মধ্যে উঠোন ছাড়িয়ে মাঠের দিকে ছুট লাগাল। ক্লোভারের হঠাৎ যেন কী খেয়াল হল, কাউকে কিছু না বলে সে চুপচাপ গিয়ে ঢুকল মলির আস্তাবলে। খুর দিয়ে মলির বিছানার খড় একটু উল্টে উল্টে দেখতেই একটা ছোট্ট চিনির ড্যালা পাওয়া গেল, সঙ্গে কয়েক গোছা নানারঙের রিবন।
তিনদিন পর মলি কোথায় যেন গায়েব হয়ে গেল। বেশ কয়েক হপ্তা তার আর কোনও হদিস পাওয়া গেল না। একদিন পায়রার দলে এসে জানাল তারা মলিকে উইলিংডনের অন্যপ্রান্তে একটা পানশালার বাইরে দেখেছে। লাল-কালো রঙের বেশ কেতাদুরস্ত একটা ঘোড়ার গাড়িতে জুতে দেয়া হয়েছে ওকে। চেকচেক প্যান্ট পরা মোটাসোটা চেহারার এক লালমুখো লোক— খুব সম্ভবত সেই পানশালার মালিক— মলিকে চিনি খাওয়াচ্ছিল আর নাকে হাত বুলিয়ে আদর করছিল। মলির লোম ছাঁটাই করা হয়েছে কিছুদিন হল, কপালের চুলে বাঁধা লাল টুকটুকে রিবন— সব দেখেশুনে পায়রাদের মনে হয়েছে মলি বেশ ফুর্তিতেই রয়েছে। এরপর ফার্মের কোনও জন্তু আর কখনও মলির নাম উচ্চারণ করেনি।
জানুয়ারি মাসে আবহাওয়া অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয়ে উঠল। মাটি এমন শক্ত হয়ে গেল যেন লোহার তৈরি। সে মাটিতে আর কিছুই করার জো রইল না। বড় গোলাঘরটায় দফায় দফায় সভার আয়োজন করা হল। শুয়োররাও আগামী মরসুমের কাজের পরিকল্পনা করতে লেগে পড়ল। তারা যেহেতু বাকি জন্তুদের চেয়ে বুদ্ধিমান, তাই খামারের ভালোমন্দ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া বা নীতি নির্ধারণ— এসব কাজ যে শুয়োররাই করবে, তা বাকি জন্তুরা মোটামুটি মেনেই নিয়েছে। যদিও শুয়োরদের সিদ্ধান্তগুলো সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোট পেয়ে অনুমোদিত হতে হবে।
এই ব্যবস্থাটা বেশ ভালই ছিল, যদি না স্নোবল আর নেপোলিয়নের মধ্যে বিরোধ থাকত। মতের অমিল হওয়ার সুযোগ আছে এমন প্রায় প্রতিটা ক্ষেত্রেই দু’জনের খটাখটি লাগে। এদের মধ্যে একজন যদি বেশিরভাগ জমি জুড়ে যব চাষের প্রস্তাব রাখে, তা হলে অন্যজন নিশ্চিতভাবে বলবে, না, যব নয়, তার বদলে সেখানে জই চাষ করা হোক। একজন যদি মনে করে কোনও জমি বাঁধাকপি চাষের উপযুক্ত, সঙ্গে সঙ্গে অন্যজন ঘোষণা করে, এই জমিতে মূলো ছাড়া আর কিছুই চাষ করা অসম্ভব। এদের দু’জনেরই নিজস্ব কিছু সমর্থক আছে। ফলে কখনও কখনও তর্কযুদ্ধ ভয়ঙ্কর দিকে বাঁক নেয়।
আরও পড়ুন: ল্যাটিন অ্যামেরিকার দুই কবির কবিতার অনুবাদ
স্নোবল বেশ বলিয়ে-কইয়ে। সে চমৎকার বক্তৃতা দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন আদায় করে নেয়। নেপোলিয়নও কম যায় না। সে ঠিক সময়ে প্রচার-টচার করে নিজের দল ভারী করে। বিশেষ করে ভেড়ার পালের উপর তো তার দারুণ প্রভাব। আজকাল আবার ভেড়াগুলোর মধ্যে নতুন এক হুজুগ উঠেছে। তারা যখন তখন গলা ছেড়ে ‘চারপেয়েরা ভালো, দু’পেয়েরা খারাপ’ বলে চেঁচিয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে তারা সভার মাঝেও এইভাবে হল্লা করে ব্যাঘাত ঘটায়। খেয়াল করে দেখা গেছে, স্নোবলের বক্তৃতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গাটাতেই যেন তাদের মধ্যে ‘চারপেয়েরা ভালো, দু’পেয়েরা খারাপ’ বলে চিৎকার করার হিড়িক পড়ে।
খামারবাড়ি থেকে ‘কৃষক ও পশুপালক’ পত্রিকার পুরনো কিছু সংখ্যা খুঁজে পাওয়া গেছে। স্নোবল সেগুলো খুব মন দিয়ে পড়েছে, ফলে এখন তার মগজে উদ্ভাবনী ক্ষমতা আর উন্নয়ন পরিকল্পনার একেবারে জোয়ার এসেছে। সে খুব বিজ্ঞ বিজ্ঞ বক্তৃতা দেয় জমির নিকাশি ব্যবস্থা আর খাদ্য সংরক্ষণের উপর। জমিতে সার দেওয়ার ব্যাপারে সে বিশেষ ভাবনাচিন্তা করেছে। তার নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রত্যেক পশু সরাসরি জমিতে গিয়ে এক একদিন এক একজায়গায় মলত্যাগ করবে। এতে সার বয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিশ্রম বাঁচবে। নেপোলিয়নের নিজস্ব পরিকল্পনা বলে কিছু নেই। সে গোপনে বলে বেড়াতে লাগল যে স্নোবলের এসব কায়দা-কানুনে লাভের লাভ কিস্যু হবে না। দেখে শুনে মনে হয়, সে যেন অপেক্ষা করছে কবে তার দিন আসবে। শেষমেষ একটা হাওয়া কল নিয়ে তাদের মধ্যে তিক্ততা এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছলো, যার কাছে আগের ঝামেলাগুলো প্রায় কিছুই নয়।
খামারবাড়ির খুব কাছেই বিস্তীর্ণ তৃণভূমির মাঝে একটা ছোট ঢিবি আছে। এই ঢিবিটাই খামারের সবচেয়ে উঁচু জায়গা। জমিটাকে ভালো করে জরিপ-টরিপ করে স্নোবল ঘোষণা করল, এইটেই হাওয়া কল বানাবার সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান। এই হাওয়া কল থেকে তৈরি হবে ডায়নামো আর তা থেকে ফার্মে বিজলি সরবরাহ করা হবে। বিজলি এলে অনেক সুবিধে— বাতি জ্বলবে, জন্তুদের থাকার জায়গাগুলো শীতকালেও গরম রাখা যাবে। এছাড়াও একটা গোল করাত, একটা খড় কাটার যন্ত্র, একটা বিট কাটার যন্ত্র আর একটা দুধ দোয়াবার যন্ত্র চালানো যাবে সেই বিজলি থেকে।
মতের অমিল হওয়ার সুযোগ আছে এমন প্রায় প্রতিটা ক্ষেত্রেই স্নোবল আর নেপোলিয়নের খটাখটি লাগে। এদের মধ্যে একজন যদি বেশিরভাগ জমি জুড়ে যব চাষের প্রস্তাব রাখে, তা হলে অন্যজন নিশ্চিতভাবে বলবে, না, যব নয়, তার বদলে সেখানে জই চাষ করা হোক। একজন যদি মনে করে কোনও জমি বাঁধাকপি চাষের উপযুক্ত, সঙ্গে সঙ্গে অন্যজন ঘোষণা করে, এই জমিতে মূলো ছাড়া আর কিছুই চাষ করা অসম্ভব। এদের দু’জনেরই নিজস্ব কিছু সমর্থক আছে। ফলে কখনও কখনও তর্কযুদ্ধ ভয়ঙ্কর দিকে বাঁক নেয়।
এ খামারটা বরাবরই খুব সেকেলে ধাঁচের। যন্ত্রপাতি যেটুকু যা আছে সবই একেবারে প্রস্তর যুগের। তার ফলে জানোয়াররা এই সমস্ত রকমারি যন্ত্রের কথা কস্মিনকালেও শোনেনি। স্নোবল যখন এই সব জাদুযন্ত্রের কথা বলে তখন তারা চোখ গোল্লা-গোল্লা করে শোনে। সত্যিই! কী আশ্চর্য সব যন্ত্র! তারা যখন মহানন্দে মাঠে চরে বেড়াবে, পড়াশুনো করে আর আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের মানসিক উন্নতি ঘটাবে, তখন এই যন্ত্রগুলো তাদের সব কাজ করে দেবে! কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই হাওয়া কলের একটা সম্পূর্ণ নকশা তৈরি করে ফেলল স্নোবল। যান্ত্রিক খুঁটিনাটির বেশিরভাগটাই পাওয়া গেল মিস্টার জোন্সের তিনটে বই— ‘ঘর বানবার হাজার উপায়’, ‘রাজমিস্ত্রি হতে গেলে’ আর ‘বিদ্যুতের সহজপাঠ’ থেকে। হাঁস-মুরগির ডিম ফোটানোর ঘরটাকে স্নোবল নিজের পড়ার ঘর বানাল। এই ঘরের কাঠের মেঝেটা বেশ মসৃণ। আঁকিবুকি কাটার পক্ষে বড়ই উপযুক্ত। এই ঘরে স্নোবল ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটায়। একপাশে বইগুলোকে খুলে রেখে, পাতায় পাথরের টুকরো চাপা দিয়ে স্নোবল তুলে নেয় চক। সেই চক সামনের পায়ের খুরের ফাঁকে আটকে সে ইতস্তত ঘোরাফেরা করে ঘরের মধ্যে। চক দিয়ে লাইনের পর লাইন টানে। কখনও কখনও উত্তেজনায় ঘোঁত ঘোঁত করে ওঠে।
আরও পড়ুন: তৃষ্ণা বসাকের তর্জমায় ই সন্তোষ কুমারের গল্প: আলোকবর্ষ
ধীরে ধীরে সেই মেঝের অর্ধেকের বেশি নকশায় ভরে গেল। নকশাটা বড়ই জটিল। দেখে মনে হয় যেন বিভিন্ন রকমের হাতল আর খাঁজকাটা চাকার একটা স্তূপ। নকশাটা জন্তুদের এক্কেবারে মাথার উপর দিয়ে গেল ঠিকই, তবে তারা যে বেশ মুগ্ধ হল সে কথাও অস্বীকার করা যায় না। প্রত্যেকে দিনে অন্তত একবার এসে নকশাটা দেখে যায়। এমনকি হাঁস-মুরগিরাও আসে। তবে তাদের সবসময় সাবধান থাকতে হয় যাতে নকশার উপর পা না দিয়ে ফেলে। একমাত্র ব্যতিক্রম নেপোলিয়ন। সে যেন এইসব নকশা-টকশার ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। একেবারে শুরুর দিন থেকেই সে ঘোষিতভাবে এই হাওয়া কলের বিরোধী।
হঠাৎই একদিন সকলকে অবাক করে দিয়ে সে এসে উপস্থিত হল নকশাগুলো দেখতে। ভারিক্কি চালে ছাউনির চারপাশে খানিক ঘুরল সে। তারপর খুব কাছ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নকশাটা দেখতে লাগল। নাকটাকে নকশার কাছে নিয়ে গিয়ে দু’ একবার কী যেন শুঁকল। পরমুহূর্তেই একটু দূরে সরে গিয়ে ত্যারছা চোখে নকশাটাকে দেখতে দেখতে কী সব ভাবনাচিন্তা করল। তারপর আচমকাই পা উঠিয়ে ছরছরিয়ে নকশাটার উপর খানিক পেচ্ছাপ করে দিয়ে সে চুপচাপ সেখান থেকে চলে গেল। এই হাওয়া কলকে কেন্দ্র করে পুরো অ্যানিম্যাল ফার্ম যেন দু’ভাগে ভাগ হয়ে গেল।
স্নোবল এটা অস্বীকার করছে না যে এই হাওয়া কল বানানো খুব কঠিন একটা কাজ। পাথর সংগ্রহ করে এনে দেয়াল গড়ে তুলতে হবে, তারপর বানাতে হবে পাখা, সবশেষে দরকার পড়বে ডায়নামো আর বৈদ্যুতিক তার— তবে এগুলো কীভাবে পাওয়া যাবে, সেটা অবশ্য স্নোবল ভেঙে বলল না। সে নিশ্চিত যে এক বছরের মধ্যে এই হাওয়া কল তৈরি হয়ে যাবে। সে ঘোষণা করল, এই হাওয়া কল তৈরি হয়ে গেলে পশুদের পরিশ্রম এতটাই কমে যাবে যে সারা হপ্তা আর খেটে মরতে হবে না, মাত্র তিনদিন কাজ করলেই চলবে। অন্যদিকে নেপোলিয়নের মতে এই মুহূর্তে ফসলের উৎপাদন বাড়িয়ে যাওয়াটাই সবচেয়ে জরুরি। তার বদলে যদি এই হাওয়া কল নিয়ে বেকার বেকার সময় নষ্ট করা হয়, তা হলে সবাইকে না-খেয়ে মরতে হবে।
পশুরা নিজেদের মধ্যে দুটো দল বানিয়ে ফেলল। একদলের স্লোগান, ‘স্নোবল-কে ভোট দাও, তিন দিন কাজ পাও’, অন্যদলের স্লোগান ‘নেপোলিয়ানকে ভোট দাও, ভরপেট খেতে পাও’। একমাত্র বেঞ্জামিন কোনও দলে যোগ দিল না। কারণ সে মোটেই বিশ্বাস করে না যে আরও বেশি বেশি পরিমাণে খাবার পাওয়া যাবে। আবার এটাও মনে করে না যে হাওয়া কল তৈরি হলে খাটনি বাঁচবে। তার কথায় হাওয়া কল হোক বা না-হোক, তাদের দিন যেমন বিচ্ছিরিভাবে এতদিন কেটেছে ঠিক তেমন বিচ্ছিরিভাবেই ভবিষ্যতেও কাটবে।
কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই হাওয়া কলের একটা সম্পূর্ণ নকশা তৈরি করে ফেলল স্নোবল। যান্ত্রিক খুঁটিনাটির বেশিরভাগটাই পাওয়া গেল মিস্টার জোন্সের তিনটে বই— ‘ঘর বানবার হাজার উপায়’, ‘রাজমিস্ত্রি হতে গেলে’ আর ‘বিদ্যুতের সহজপাঠ’ থেকে। হাঁস-মুরগির ডিম ফোটানোর ঘরটাকে স্নোবল নিজের পড়ার ঘর বানাল। এই ঘরের কাঠের মেঝেটা বেশ মসৃণ। আঁকিবুকি কাটার পক্ষে বড়ই উপযুক্ত। এই ঘরে স্নোবল ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটায়। একপাশে বইগুলোকে খুলে রেখে, পাতায় পাথরের টুকরো চাপা দিয়ে স্নোবল তুলে নেয় চক।
ঝামেলা শুধু যে হাওয়া কল নিয়ে হল তা নয়। খামারের প্রতিরক্ষা বিষয়েও বেশ কিছু প্রশ্ন উঠল। মানুষের দল গোয়ালঘরের যুদ্ধে গো-হারা হেরেছে বটে, তা বলে নিশ্চিন্তে বসে থাকলে তো চলবে না। কারণ একথা দিব্যি অনুমান করা যায় যে ওরা আবার ফিরে আসবে— এবার আরও দৃঢ়সংকল্প হয়ে। ওরা ফের চেষ্টা করবে এই ফার্ম দখল করে জোন্সকে পুনর্বহাল করতে। মানুষেরা এখন একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছে। তার একটা বড় কারণ হল, গোয়ালঘরের যুদ্ধে তাদের হেরে যাওয়ার খবরটা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে আশেপাশের খামারের জন্তুগুলো বড়ই অবাধ্য হয়ে উঠেছে।
বরাবরের মতোই এ-ব্যাপারেও নেপোলিয়ান আর স্নোবলের বিরোধ বাধল। নেপোলিয়নের মতে, পশুদের আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করতে হবে এবং তা চালাতে শিখতে হবে। অন্যদিকে স্নোবল মনে করে, অন্যান্য খামারগুলোতে আরও বেশি বেশি পায়রা পাঠিয়ে সেখানকার পশুদের বিদ্রোহ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। একজনের মতে, যদি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে না পারি তো হার সুনিশ্চিত। অন্যজন বলল, যদি সর্বত্রই বিপ্লবের আগুন জ্বলে ওঠে তা হলে নিজেদের রক্ষা করার কথা আর আলাদা করে ভাবতেই হবে না। জন্তুরা প্রথমে নেপোলিয়নের কথা শুনল, তারপর স্নোবলের কথা। কিন্তু কে যে ঠিক বলছে তা বুঝে উঠতে পারল না। আসলে মুশকিলটা হচ্ছে, ওরা যখন যার কথা শোনে সেই মুহূর্তে তার কথাটাই সঠিক বলে মনে হয়।
অর্ক পৈতণ্ডীর জন্ম ১৯৮৫-তে বীরভূমের সিউড়িতে। পড়াশোনা, বেড়ে ওঠা বোলপুর, শান্তিনিকেতনে। বিজ্ঞানের স্নাতক। পেশাদার শিল্পী। 'মায়াকানন' পত্রিকা ও প্রকাশনার প্রতিষ্ঠাতা ও কর্ণধার। অবসরে লেখালিখি করেন। অলঙ্করণ শুরু ষোলো বছর বয়সে শুকতারা পত্রিকায়। পরবর্তীকালে আনন্দমেলা, সন্দেশ, এবেলা, এই সময়, উনিশ-কুড়ির মতো একাধিক পত্রপত্রিকার জন্য ছবি এঁকেছেন। কমিক্স আঁকার জন্য ২০১৪ সালে নারায়ণ দেবনাথ পুরস্কার পেয়েছেন।